খুলছে গার্মেন্টস: লাখো কর্মীর নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা নিচ্ছি

চলমান কঠোর লকডাউনের আওতা থেকে বের করে দেওয়া হলো রপ্তানিমুখী শিল্পকারখানাগুলোকে। লকডাউনের পাঁচ দিন বাকি থাকতেই কারখানা খুলছে আগামীকাল। করোনা মোকাবিলায় গঠিত জাতীয় কারিগরি বিশেষজ্ঞ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এ বিষয়ে দ্য ডেইলি স্টারকে বলেছেন, 'সরকারের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেবে।'
তবু, কেন খুলতে হলো কারখানা? আমরা কি এই খাতে কর্মরত লাখো কর্মীকে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছি না? তাদের নিরাপত্তার জন্যে কী বিশেষ ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি?
বিশ্বায়নের এই যুগে পৃথিবীর এক প্রান্তের বাজার অন্য প্রান্তের উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল। আবার এর ঠিক উল্টোটাও। একপ্রান্তের বাজারের ওপর নির্ভর করেই অন্যপ্রান্তে পণ্য ও সেবার উৎপাদন হয়। বৈশ্বিক এই সরবরাহ ব্যবস্থা বা সাপ্লাই চেইনের সবচেয়ে বড় প্রবণতা হচ্ছে—যেসব দেশে সস্তায় শ্রম পাওয়া যায়, ব্যবসা ও শ্রমের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত শিথিল এবং রাষ্ট্রীয় অবস্থান শিল্পের জন্যে প্রণোদনামূলক সেসব দেশ থেকে অপেক্ষাকৃত কম দামে পণ্য তৈরি করিয়ে নেওয়া।
অধিক জনসংখ্যা, সস্তা শ্রম ও রপ্তানিমুখী ব্যবসার প্রতি রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য— এসব মিলে বাংলাদেশও বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদক ও সরবরাহকারী হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় বাংলাদেশ যে একটিমাত্র পণ্য ব্যাপকভাবে যোগান দিয়ে থাকে, সেটি হচ্ছে তৈরি পোশাক। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে আমরা বিশ্বে দ্বিতীয়। বিশ্ববাজারের ছয় শতাংশের মতো তৈরি পোশাকের যোগান দিয়ে থাকে বাংলাদেশ। এর বিনিময়ে আসে বাংলাদেশের প্রায় ৮৫ শতাংশ বৈদেশিক আয়। দেশের জিডিপিতে এই খাতের অবদান প্রায় ১২ শতাংশ।
এই খাতে কমপক্ষে ৩৫ লাখ শ্রমিক কাজ করেন। আরও লাখ-খানেক মানুষ কারখানাগুলোর ম্যানেজমেন্ট লেভেলে কাজ করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি পরিবারে যদি পাঁচ জন করে সদস্য থাকে, তাহলে শুধু গার্মেন্টস কারখানাগুলোর ওপর দেশের প্রায় ১০ শতাংশ মানুষের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা রয়েছে। এ ছাড়া, ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোয়ার্ড লিংকেজগুলোর সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ কাজ করেন। সুতরাং একক খাত হিসাবে এটা শুধু কিছু মানুষের ব্যবসা নয়। শুধু টাকার অংকে এটি বড় খাত নয়। অংশগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যায়ও এটি বড় খাত।
শ্রমিকদের আয় শুধু তিনি যেখানে থাকেন বা কাজ করেন সেখানকার স্থানীয় অর্থনীতিতে ব্যয় হয় না। বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতেও এই নিম্নবিত্ত মানুষগুলোর আয় ব্যাপক অবদান রাখে। কারণ, আয়ের কত শতাংশ টাকা গ্রামে পাঠান, এই হিসাব করলে দেখা যাবে নিম্নবিত্তরাই তাদের আয়ের একটা বড় অংশ গ্রামে পাঠান। মধ্যবিত্তরা বা উচ্চবিত্তরা তাদের আয়ের শতাংশের হিসেবে খুব কম অংশই গ্রামে পাঠিয়ে থাকেন।
গত একবছর ধরে সরকার গার্মেন্টসসহ রপ্তানিমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোকে সবধরনের লকডাউনের আওতার বাইরে রেখেছে। এখন যখন করোনা সংক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, তখন সরকার এই কারখানাগুলোকে লকডাউনের আওতায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু, শুরু থেকেই এতে রাজি নন ব্যবসায়ীরা।
তাদের যুক্তি হচ্ছে, এখন কারখানাগুলোতে প্রচুর কাজের চাপ। ইউরোপ-আমেরিকার আগামী শীতের মৌসুম ও ক্রিসমাসকে সামনে রেখে প্রচুর ওয়ার্ক অর্ডার কারখানাগুলোতে। একইসঙ্গে মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থান হওয়ার পরে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেখান থেকে যেসব অর্ডার তুলে নিয়েছে ব্রান্ডগুলো, তার কিছু অর্ডারও সম্ভবত বাংলাদেশে এসেছে। সবমিলে কারখানাগুলোর জন্যে এখন ভরা মৌসুম।
আগামী শীতের মৌসুমের আগেই ইউরোপ-আমেরিকায় করোনা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসবে— এমনটা ধারণা করা হচ্ছে। কারণ, তার আগেই সেসব দেশের নাগরিকদের বড় অংশ টিকা পেয়ে যাবেন। আসছে ক্রিসমাস সিজনে ওখানে বাজারঘাট খুলে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে পুরোদমে কাজ করা দরকার। তা না হলে সময়মতো শিপমেন্ট করা যাবে না। ফলে কাজ হারানোর ভয় আছে। এটাই ব্যবসায়ীদের যুক্তি।
তাদের দাবির মুখে চলমান কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যেই তৈরি পোশাকসহ সব রপ্তানিমুখী শিল্পকারখানা আগামীকাল থেকে লকডাউনের আওতার বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গতকাল প্রজ্ঞাপন দিয়েছে। একটিমাত্র খাতের ওপর দেশের বৈদেশিক আয়ের যে নির্ভরতা, সেটা নিশ্চয়ই সরকারের সঙ্গে দরকষাকষিতে ব্যবসায়ীদেরকে সুবিধা দিয়েছে।
চলমান বিধিনিষেধে শ্রমিকেরা, যারা ঈদের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন, তারা দূর-দূরান্ত থেকে কীভাবে কর্মস্থলে ফিরবেন, তার কোনো নির্দেশনা এই প্রজ্ঞাপনে নেই। যদিও মালিকদের সংগঠনগুলো বলছে, যেসব শ্রমিক কাছাকাছি দূরত্বে আছেন, তাদেরকে নিয়েই আপাতত উৎপাদন শুরু করা হবে।
কিন্তু, বাস্তবে দেখা যাবে, কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শ্রমিকেরা কারখানা খোলার বার্তা পেয়ে যাবেন। এতক্ষণে পেয়েও গেছেন। কারখানা খোলা অবস্থায় অনুপস্থিত থাকলে বেতন হারানো, এমনকি চাকরি হারানোর ভয়ে তার পড়িমরি করে 'নিজ দায়িত্বে' কর্মস্থলের দিকে ছুটবেন। কখনো ভাঙাপথে, কখনো পায়ে হেঁটে মানুষের যে ঢল গতবছর আমরা দেখেছিলাম, তেমন একটি দৃশ্য আজও দেখা গেছে। সেটা করোনা সংক্রমণের জন্যে আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ ভাঙাপথে পাঁচটি অংশে পাঁচটি যানবাহনে উঠলে একজন মানুষকে অন্তত পাঁচ জন মানুষের পাশে বসতে হবে। ফেরিতে গাদাগাদি করে পার হওয়ার দৃশ্য তো আমরা দেখেছি। তাই তাদের কর্মস্থলে ফেরাকে সহজ করতে বিজিএমইএ ও বিকেএমএর ব্যবস্থাপনায় আন্তঃজেলা যাতায়াতের জন্যে পরিবহনের ব্যবস্থা করা যেত।
যদিও এই পরিস্থিতি এড়িয়ে যেতে পারলেই সবচেয়ে ভালো হতো। গার্মেন্টস সেক্টরে বদলি দিন কাজ করার প্রচলন রয়েছে। সাধারণত ঈদের ছুটির সঙ্গে বাড়তি দিন যোগ করে দীর্ঘ ছুটি দেয় কারখানাগুলো। বাড়তি দিনগুলোর বদলে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কাজ করে তারা পুষিয়ে দেন। কারণ শ্রমিকরা এই দুটো ছুটি ছাড়া গ্রামে যাওয়ার সুযোগ সাধারণত পান না। অধিকাংশের পরিবার গ্রামে থাকে। এমন অনেক নারী শ্রমিক রয়েছেন যাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে গ্রামে থাকে। তাদের সঙ্গে কয়েকটা দিন বেশি কাটানোর জন্যে কয়েকটা সপ্তাহ ছুটির দিনে কাজ করতে তাদের আপত্তি থাকে না।
এই কঠোর লকডাউনের বাকি পাঁচটা দিনের জন্যে সেরকম বিকল্প ব্যবস্থা নিতে পারলে ভালো হতো। কারণ, করোনা পরিস্থিতি তো প্রতিদিন খারাপ হচ্ছে। হাসপাতালগুলো তাদের সেবা দেওয়ার ক্ষমতার প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে। রোগীরা এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতাল ঘুরছেন। জীবনের নিরাপত্তা তো সবার আগে।
কিন্তু, কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত যেহেতু চূড়ান্ত, এখন ভাবতে হবে এসব কারখানায় কর্মরতদেরকে করোনা থেকে নিরাপদ রাখতে অন্য কী করা যেতে পারে। গত একবছর ধরে কারখানাগুলো চলছে। কারখানাগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে কারখানা কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছায়, ক্রেতাদের আগ্রহ ও চাপে, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষগুলোর অংশগ্রহণে। অধিকাংশ কারখানার ভেতরে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেগুলো করোনা প্রতিরোধের জন্যে যথেষ্ট।
হাত ধোয়া, মাস্ক পরা, শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা তো আছেই। প্রতিটি কারখানায় 'সেইফটি কমিটি' রয়েছে। অধিকাংশ কারখানায় 'করোনা টাস্কফোর্স' গঠন করা হয়েছে। অনেক কারখানাতেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে; ডাক্তার, নার্স রয়েছে। করোনাকালে সেখানে যুক্ত হয়েছে আইসোলেশন সেন্টার। কোথাও কোথাও কারখানার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হাইফ্লো অক্সিজেনের ব্যবস্থাসহ করোনা চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের একটি কারখানার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটি আইসিইউ বেডেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরও আরও জায়গায় এরকম ব্যবস্থা থাকতে পারে।
কিন্তু, সমস্যা অন্য জায়গায়। এসব শ্রমিকেরা যেখানে থাকেন, সেই জায়গাগুলোতে তো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা সম্ভব না। সেখানে কোথাও কোথাও কয়েকটি পরিবার একই রান্নাঘর, একই শৌচাগার ব্যাবহার করেন। হয়তো মেস করে একই রুমে কয়েকজন থাকেন। সেখান থেকে বের হয়ে সকালে তারা কারখানার গেটে ঢোকার আগ পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি পুরোপুরি মেনে চলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং কারখানার মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মানলেও সার্বিকভাবে ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে।
শ্রমিককে ঝুঁকিতে রেখে তো দীর্ঘমেয়াদে শিল্প সচল থাকতে পারে না। সুতরাং ভাবতে হবে কীভাবে কারখানা সচল রাখার সঙ্গে সঙ্গে কর্মরতদের করোনা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি একেবারে কমিয়ে আনা যায়। ঝুঁকি কমানোর দুটো উপায়—স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও টিকা নেওয়া।
এই শিল্পকে যেহেতু লকডাউনের আওতায় আনাই যাচ্ছে না, তাহলে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে দ্রুত সময়ের মধ্যে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
কোনো কোনো ফ্যাক্টরি আগের নিয়ম অনুযায়ী ৪০ বছরের বেশি বয়সীদের টিকা দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল। তারা রেজিস্ট্রেশন করা, টিকাকেন্দ্রে কর্মীদেরকে নেওয়ার জন্যে পরিবহনের ব্যবস্থা করা—এসব দায়িত্ব পালন করেছে। গাজীপুরের একটি কারখানা কর্তৃপক্ষ সেখানকার ৪০ বছরের বেশি বয়সী সবাইকে টিকা দেওয়া নিশ্চিত করেছিল। কিন্তু, গার্মেন্টস কারখানায় ৪০ বছরের বেশি বয়সী শ্রমিকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এখন যখন টিকা নেওয়ার জন্যে ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ২৫ বছর করা হয়েছে এবং সেটাকে আরও কমিয়ে ১৮-তে আনার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে, তখন দ্রুত সময়ের মধ্যে সবাইকে টিকার আওতায় আনার ব্যবস্থা করতে হবে।
ঈদের আগে গাজীপুরে চারটি কারখানার মোট ১০ হাজার শ্রমিককে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে টিকা দেওয়া হয়েছে ফ্যাক্টরি প্রাঙ্গণে স্পট রেজিস্ট্রেশন করে। এরকম কার্যক্রমকে জোরদার করতে হবে।
করোনার টিকা প্রদানের অগ্রাধিকার তালিকায় এই সেক্টরে কর্মরতদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কারণ, তাদেরকে তো কাজে যোগ দিতেই হচ্ছে। তাদের নিরাপত্তা নিয়ে হেলাফেলা করার সুযোগ নেই।
আমাদের নাগরিকদের টিকা প্রদানের মূল দায়িত্ব অবশ্যই সরকারের। কিন্তু, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, এই সেক্টরে কাজ করা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এক্ষেত্রে যার যার জায়গা থেকে উদ্যোগ নিতে পারে। গার্মেন্টসকর্মীদেরকে টিকা দেওয়ার বিষয়ে বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা ভূমিকা রাখতে পারে, সেটা আরেকবার খতিয়ে দেখা যেতে পারে।
বাংলাদেশের তৈরি পোশাক যেসব দেশের বাজারে যায়, তার অনেকগুলোতেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত টিকার যোগান রয়েছে। কোনো কোনো দেশ তো প্রয়োজনের চেয়ে তিন-চার গুণ বেশি টিকা কেনার জন্যে অর্ডার দিয়ে রেখেছে। গার্মেন্টস পণ্যের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো যদি নিজ নিজ দেশের সরকারের সঙ্গে লবিং করে গার্মেন্টসকর্মীদের জন্যে টিকা আনার ব্যবস্থা করতে পারে, তাহলে এই দুঃসময়ে সেটা দারুণ সহায়তা হবে। একইসঙ্গে এটা ব্র্যান্ডগুলোর শ্রমিকের পাশে দাঁড়ানোর উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবে।
সেসব দেশের ঢাকাস্থ দূতাবাসগুলোর সঙ্গে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ যোগাযোগ করে দেখতে পারে যে, দ্রুত সময়ের মধ্যে টিকা পেতে তারা কী সহায়তা করতে পারে। কারণ, শ্রমিকের কর্মস্থলের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার কথা তারা প্রায়ই বলে থাকেন। এ বিষয়ে তাদের প্রতিশ্রুতির প্রমাণ দেওয়ার এর চেয়ে ভালো সময় আর কখন হতে পারে?
তাপস বড়ুয়া, বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কর্মী
(দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে লেখকের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে। প্রকাশিত লেখাটির আইনগত, মতামত বা বিশ্লেষণের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে লেখকের, দ্য ডেইলি স্টার কর্তৃপক্ষের নয়। লেখকের নিজস্ব মতামতের কোনো প্রকার দায়ভার দ্য ডেইলি স্টার নিবে না।)




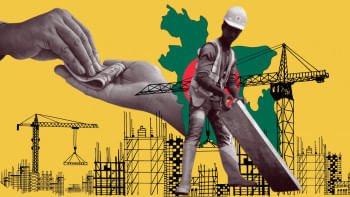
Comments