স্বাধীনতা যেমন জরুরি, পাশাপাশি মুক্তিও
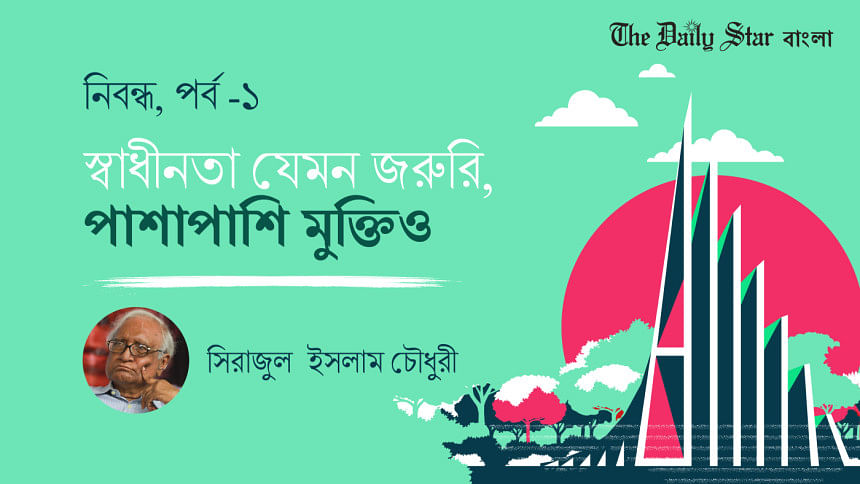
আমাদের স্বাধীনতা সবসময়েই জরুরি ছিল। কেননা আমরা পরাধীন ছিলাম। সাতচল্লিশের স্বাধীনতার পরও সেটা জরুরি হয়ে উঠেছিল একাধিক কারণে। প্রথম কারণ জাতিগত প্রশ্নের মীমাংসা। পাকিস্তান নামের এই অস্বাভাবিক রাষ্ট্রটিতে নিপীড়ন চলছিল বাঙালির জাতিসত্তার ওপরে। নিষ্ঠুর নিপীড়ন। রাষ্ট্রক্ষমতা যাদের দখলে ছিল তারা কেবল যে অবাঙালি ছিল তা নয়, ছিল তারা বাঙালি-বিদ্বেষী। শাসন ব্যবস্থার পুরোটাই ছিল এই বাঙালি-বিদ্বেষীদের হাতে। সামরিক বাহিনী, আমলাতন্ত্র, পুলিশ, আদালত, জেলখানা সবই তাদের অধীনে। ব্যবসা-বাণিজ্যসহ গোটা অর্থনীতি তারাই নিয়ন্ত্রণ করতো। প্রচার মাধ্যমে তারা ছাড়া আবার কারা? শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তারা হাতে রাখতে চাইতো।
জাতিগত নিপীড়নের এই সমস্যার সমাধান না করে অন্য প্রশ্নগুলোর মীমাংসা করা সম্ভব ছিল না। সে-জন্যই স্বাধীনতা অতি জরুরি ছিল। ওটি ছিল প্রথম পদক্ষেপ, সমষ্টিগত অগ্রযাত্রার। মূল লক্ষ্যটা কি? মূল লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় মুক্তি। জাতি বলতে শ্রেণি বুঝায় না, বিশেষ গোষ্ঠী বুঝায় না, জাতি হচ্ছে সমগ্র জনগণ। জনগণের মুক্তিই ছিল লক্ষ্য। জনগণ স্বাধীনতাকে ওই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখেছে, মনে করেছে রাষ্ট্র স্বাধীন হলে তারা মুক্ত হবে। তাদের যে ন্যূনতম চাহিদা- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার চাহিদা, সেগুলো মিটবে। তাদের জীবনে নিরাপত্তা আসবে। তারা মানুষের মতো বাঁচতে পারবে। এই স্বপ্ন নিয়েই একাত্তরের মানুষ যুদ্ধ করেছে। যে জন্য এ-যুদ্ধকে মুক্তিযুদ্ধ বলা হয়, স্বাধীনতা যুদ্ধ না বলে।
স্বাধীনতা একবার সাতচল্লিশেও এসেছিল। নতুন রাষ্ট্র, সংবিধান, রাজধানী, পতাকা, দালানকোঠা ক্ষমতায় নতুন মানুষ- সবই হলো, ভূখ-ও পাওয়া গেলো কিন্তু যে জন্য মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল সেই আশাটা মিটলো না। জনগণের মুক্তি এলো না। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে শত শত মাইলের দূরত্ব ছিল, কিন্তু ওই দূরত্বের কারণে পাকিস্তান ভাঙেনি, সামরিক বাহিনী, আমলাতন্ত্র, জুলফিকার আলী ভুট্টো ওদের তথাকথিত নির্বুদ্ধিতার কারণেও নয়, ভেঙেছে বৈষম্যের কারণে। এক অংশ সব ক্ষমতা দখল করে রেখেছিল, রেখে বেড়ে ও ফেঁপে উঠেছিল, উঠে অন্য অংশের ওপর জাতিগত নিপীড়ন ও শোষণ চালাচ্ছিল। তাদের নিপীড়ন ও শোষণে পূর্ববঙ্গ শ্মশানে পরিণত হচ্ছিল। শ্মশান হবার জন্য তো মানুষ স্বাধীনতা চায় নি, লোকে বাগান চেয়েছে, ফলের ও ফুলের; সে জন্য তারা ওই স্বাধীনতাকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যে প্রয়োজন ক্রমে ক্রমে এই ধারণা গড়ে তুললো। দাবির ব্যাপারটা প্রথমে স্পষ্ট ছিল না তাদের কাছে, ঘটনাই শিখিয়ে দিল যে পুরাতন রাষ্ট্রে তাদের মুক্তি নেই।
মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর প্রশ্ন দাঁড়াল আমাদের মুক্তি কিভাবে আসবে? আসবার একটা পথ বাংলাদেশের আদি সংবিধানে দেখানো হয়েছিল। চারটি মূলনীতি বের হয়ে এসেছিল। মুক্তিযুদ্ধের ভেতর থেকে। তারা পরিণত হয়েছিল রাষ্ট্রের মূলনীতিতে। কিন্তু পথের দিশা সংবিধানে থাকাই তো যথেষ্ট নয়, পথটা বাস্তব ক্ষেত্রে গড়ে তোলা অনিবার্য ছিল। উপযুক্ত ব্যক্তি ও সংগঠনের প্রয়োজন ছিল। আবশ্যক ছিল একটি সামাজিক বিপ্লবের।
সামাজিক বিপ্লবের কথা অনেক সময় বলা হয়, কিন্তু এর তাৎপর্য পরিষ্কার থাকে না। সামাজিক বিপ্লব বলতে সমাজের উপকাঠামোতে সংস্কার, চাঞ্চল্য বা বিস্ফোরণ বুঝায় না, বুঝায় মৌলিক পরিবর্তন। আসল কথা হচ্ছে ক্ষমতা। ক্ষমতা কাদের কাছে আছে সেটা নিয়েই সমাজের চরিত্র বুঝা যায়।
আর্য, তুর্কী-পাঠান-মুঘল, ইংরেজদের আধিপত্যের কালে সমাজে এক ধরনের বিপ্লব ঘটেছে। ক্ষমতার বিন্যাসে পরিবর্তন এসেছে। বর্ণ ও শ্রেণির উত্থান দেখা গেছে। পাকিস্তান আমলে ব্রিটিশ আমলের পুরানো সমাজই টিকে ছিল। ক্ষমতা ছিল মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে, যারা উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিক ছিল, যারা মহাজনি কারবার করতো, ব্যবসায়-বাণিজ্যে হাত দিয়েছিল, বিভিন্ন পেশায়, বিশেষ করে সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ছিল। গরিব মানুষের হাতে ক্ষমতা ছিল না। তারা শোষিত হতো। রাষ্ট্র এই ব্যবস্থাটাকে রক্ষা করতো এবং রাষ্ট্রের নিপীড়নকারী চরিত্রের পেছনে সামাজিক ব্যবস্থাটার সমর্থন ছিল। লোকে আশা করেছিল এই আয়োজনটা ভেঙে ফেলা সম্ভব হবে, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের পুরোপুরি অবসান না-ঘটুক, অবশ্যই তা হ্রাস পাবে।
এই সামাজিক বিপ্লব পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনে ঘটানো ছিল অসম্ভব। রাষ্ট্রের কাজই ছিল এর সম্ভাবনাকে নির্মূল করা। ওই রাষ্ট্রে সমাজে দুই ধরনের বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছিল। একটি সম্প্রদায়গত, আরেকটি শ্রেণিগত। খাড়াখাড়িভাবে পূর্ববঙ্গের মানুষকে ভাগ করা হয়েছিল হিন্দু ও মুসলমানে, আড়াআড়িভাবে ভাগ করা হয়েছিল ধনী ও গরিবে। আর সবাইকে এমনভাবে বেঁধে রাখা হয়েছিল শোষণের একটি নিগড়ে যে সেটা না ভেঙে সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও সুষম বণ্টনের পদক্ষেপ নেবার কথা ভাবাই সম্ভব ছিল না। প্রথম কাজ প্রথমে। প্রথম দায়িত্ব ছিল নিগড়টা ভেঙে বের হয়ে আসা, অর্থাৎ রাষ্ট্রের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু ওই স্বাধীনতাই যে চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল তা নয়, চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল মুক্তি, যেটা সম্ভব একটি সামাজিক বিপ্লব যদি ঘটানো যায় তবেই, তাকে বাদ দিয়ে নয়।
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করার ব্যাপারটা সামান্য ছিল না। প্রাণ দিতে হয়েছে, দুর্ভোগ যা সহ্য করতে হয়েছে তা অপরিমেয়। কিন্তু কাজটা হয়েছে। এক লক্ষের মতো শত্রুসৈন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়েই আত্মসমপর্ণ করেছে। আবারো সংবিধান, পতাকা, ভূখন্ড, রাজধানী, সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র ইত্যাদিতে পরিবর্তন এসেছে। ক্ষমতায় এসেছে নতুন লোক। পুরাতনরা পালিয়ে গেছে।
কিন্তু সেই সামাজিক বিপ্লবটা ঘটেনি যার জন্য স্বাধীনতা দরকার ছিল, যেটি না-ঘটলে মানুষের কাক্সিক্ষত মুক্তি ঘটাটা অসম্ভব। না, ঘটেনি। অনেক কিছুই ঘটেছে, অনেকের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু সব পরিবর্তনই জোরেশোরে একটা খবর জানাচ্ছে, সেটা হলো আসল জায়গায় পরিবর্তন আসেনি। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেনি, ক্ষমতাহীন মানুষ ক্ষমতা পায়নি, বঞ্চিতদের বঞ্চনা ঘোচেনি। অল্পকিছু মানুষ ধনী হয়েছে, অকল্পনীয়রূপে। বাকিরা গরিব হয়েছে। উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক সম্পর্ক সর্বত্র পুঁজির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লোকে এখন মুনাফা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। নিজেরটা দেখে, অন্যের দিকে তাকায় না। পাকিস্তানি হানাদাররা সশব্দে লুটপাট করেছে, বিশেষ করে নয় মাসে। তারপর থেকে স্থানীয়রা লুটপাট চালিয়েছে, তুলনামূলক কম শব্দ করে।
বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল, যেমনটা নিতো তারা পাকিস্তানি রাষ্ট্রে। তাতে বোঝা গেছে রাষ্ট্র নতুন ঠিকই, কিন্তু তার চরিত্র সেই আগেরই। সামরিক বাহিনী যখন ক্ষমতায় থাকে না তখন রাষ্ট্র চলে অসামরিক আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে। সেটাও পুরাতন ব্যবস্থা। নির্বাচন হয়েছে, নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু তাতে রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক চরিত্রে পরিবর্তন আসেনি। আর নির্বাচিত হয়েছে কারা? হয়েছে তারাই যাদের টাকা আছে। ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ, পরিচিত, স্থানীয় উন্নয়নে মনোনিবেশ সবকিছুই অর্থহীন যদি টাকার অভাব থাকে। টাকা না-থাকলে দলীয় মনোনয়নই পাওয়া যাবে না। নির্বাচিত হওয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণতার জন্য প্রসিদ্ধ, কিন্তু এখন এসেছে এক নতুন ধর্ম, সে হচ্ছে অর্থের শাসন। টাকা এখন ইহজাগতিক ঈশ্বর, তার আরাধনায় সকলেই নিমগ্ন। পুঁজিবাদে এমনটিই ঘটে। সেখানে মানুষের শ্রমে-তৈরি অর্থ মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করে। কিন্তু বাংলাদেশে ব্যাপারটা অনেক বেশি স্থূল, উলঙ্গ ও নির্লজ্জ।
কথা ছিল উল্টোটা ঘটবে। সমাজ হবে মানবিক। কর্ষণ চলবে মুনাফা-শিকারী মনোভাবের নয়, পরস্পরকে সাহায্য করার মানসিকতার। কিছু কিছু সংস্কারমূলক কাজ চলছে। সাহায্য সংস্থাগুলো করছে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয়, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এসব যে গড়া হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু তাতে সমাজের যে কাঠামো, তার ক্ষমতাবিন্যাস তাতে মৌলিক কোনো পরিবর্তন আসছে না। ফলে মানুষ স্থানীয়ভাবে সুযোগসুবিধা পেলেও ব্যাপকভাবে মুক্তি পাচ্ছে না। দরিদ্রের সংখ্যা বাড়ছে। গ্রাম থেকে মানুষ ছুটে আসছে শহরে। যেন আগুন লেগেছে। আসলে গ্রামে কর্মের সংস্থান নেই, উপার্জনের পথ নেই।
আগামী পর্বে সমাপ্ত।





Comments