ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক ফটোগ্রাফার রফিকুল ইসলাম
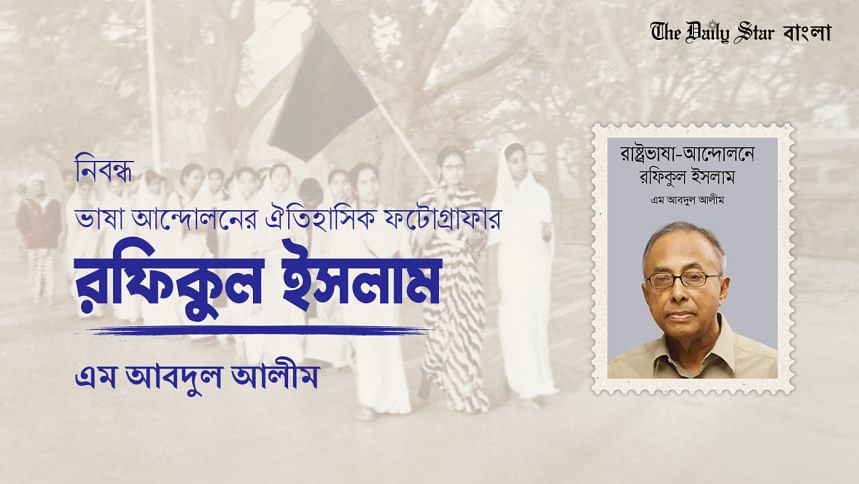
রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের অনেক ছবি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের তোলা। ঐতিহাসিকভাবে ভাষা-আন্দোলনের প্রামাণ্য দলিল ও নিদর্শনগুলোর মধ্যে রফিকুল ইসলামের তোলা ছবিগুলোর রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব।
পর্যালোচনা করে দেখা যায়, রফিকুল ইসলাম আকস্মিকভাবে ভাষা-আন্দোলনের ছবি তোলেননি। ছোটবেলা থেকেই তার শখ ছিল ছবি তোলা। সব সময়ই হাতে থাকত কোডাক সিক্স টোয়েন্টি বক্স ক্যামেরা। তার ছবি তোলার শখ ও দক্ষতা দেখে ১৯৪৯ সালের বিলেত-ফেরত এক আত্মীয় একটি জার্মান ক্যামেরা উপহার দেন। সেটি ছিল ভয়েগ ল্যান্ডার, ফোর পয়েন্ট ফাইভ ল্যান্সরিফ্লেক্ট ক্যামেরা। এটি 'রোলি ফ্ল্যাক্স' বা 'রোলি কড'-এর মতো অটোম্যাটিক না হওয়ায় অ্যাপারচার, ডিসটেন্স' ও টাইমিং হাত দিয়ে ঠিক করতে হতো। ক্যামেরাটি হাতে পেয়ে রফিকুল ইসলামের ফটোগ্রাফিতে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। এ সময় তিনি হয়ে ওঠেন এক যথার্থ ফটোগ্রাফার। পরে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী কলিম শরাফী তাকে একটি ওয়াইড ল্যান্ডের ক্যামেরা উপহার দেন, যেটি ছিল জার্মানির তৈরি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কালার স্কোপার লেন্সবিশিষ্ট। ওই ফোল্ডিং ক্যামেরায় একবারে মাত্র আটটি ছবি তোলা যেত। তারপর রোল চেঞ্জ করতে হতো। এটি অটোম্যাটিক না হওয়ায় ম্যানুয়ালি অপারেট করতে হতো। ফটোগ্রাফারের ধারণার ওপর ভিত্তি করে ডিসটেন্স, অ্যাপারচার, লাইট সবকিছু সেট করতে হতো। বাসা থেকে বের হলেই রফিকুল ইসলামের সঙ্গী হতো এই ক্যামেরাটি। একটি রোল (ফিল্ম) ক্যামেরায় ভরে রাখতেন, আরেকটি রাখতেন পকেটে।
উল্লেখ, বাবার চাকরিসূত্রে রফিকুল ইসলাম পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বাস করতেন ঢাকার রমনা এলাকার রেলওয়ে কোয়ার্টার্সে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের পেছনে)। ১৯৪৩ সাল থেকে থেকে রমনা এলাকায় বসবাস করলেও ১৯৫১ সালের জুন-জুলাই মাসে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। একদিকে রমনায় বসবাস, অন্যদিকে অধ্যয়নসূত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার আন্দোলন-সংগ্রামের ঘটনা তার প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়। হাতে থাকা শৌখিন ক্যামেরাটি দিয়ে সুযোগ পেলেই তিনি মিছিল-সমাবেশের ছবি তুলতেন।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার অধিকারের প্রশ্নে আন্দোলন শুরু হলে শখ ঐতিহাসিক দায়ে পরিণত হয়। রফিকুল ইসলাম ১৯৪৮ সালের ভাষা-আন্দোলনের মিছিল-মিটিং দেখলেও তাতে তার প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল না। কিন্তু ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে যোগ দেন। ভাষা-আন্দোলনের সংগঠক বা সামনের কাতারের নেতা নয়, একজন সচেতন ছাত্র হিসেবে তিনি ভাষা-আন্দোলনের মিছিল-মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সংস্কৃতিমনস্ক শিক্ষার্থী হিসেবে অংশ নিতেন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। সুযোগ পেলেই সেসবের ছবিও ধারণ করতেন নিজের ক্যামেরায়। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত নিজের ভায়েগ ল্যান্ডার ক্যামেরা দিয়ে অনেক ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় ছবি তুলেছেন।
রফিকুল ইসলাম বিভিন্ন সভা-সমাবেশ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ছবি তুললেও তার ভাষা-আন্দোলনের ছবিগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বেশি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানের জনসভায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রতিবাদ-মিছিল বের করে। ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১১ ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে বিশাল শোভাযাত্রা বের করা হয়। রফিকুল ইসলাম এ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন এবং ছবি তোলেন।
২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি সফল করতে ছাত্র-জনতা সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সমাবেশে আসা শুরু করে। রফিকুল ইসলাম ক্যামেরা হাতে সেখানে উপস্থিত হন। ওই সময় তার সামনে দুটি পথ খোলা ছিল, একটি দশজন দশজন করে যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করছে, তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গ্রেপ্তার হওয়া, আরেকটি ছবি তোলা। প্রথম পথে গেলে ছবি তোলা হয় না, ক্যামেরাটিও হাতছাড়া হয়, তাই তিনি দ্বিতীয় পথকেই বেছে নিলেন। কিন্তু সে পথও সহজ ছিল না। অবশেষে স্থির করলেন পুলিশের চোখ এড়িয়ে পুরাতন কলাভবনের ছাদে উঠে ছবি তুলবেন। বন্ধুদের সহায়তার উঠলেন কলাভবনের ছাদে। সেখান থেকে কয়েকটি ছবি তুলে আবার নেমে এলেন। সতর্কতার সঙ্গে ছবি তুলতে লাগলেন। এভাবে একের পর এক ১৬টি ছবি তোলেন।

২১ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩টার পর পুলিশ মেডিকেল কলেজের মোড়ে গুলিবর্ষণ শুরু করে। রফিকুল ইসলাম তখন মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ওখানে চলে আসেন। গুলিবর্ষণের পর ছাত্র-জনতা দিগ্বিদিক দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। অনেকে নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান নেয়। রফিকুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের মেইন বিল্ডিংয়ের প্রবেশপথের সামনে হাজির হন এবং দেখতে পান অ্যাম্বুলেন্সে একটি লাশ নিয়ে আসা হচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখলেন গুলির আঘাতে মাথার খুলি উড়ে গেছে। ঘিলু ছড়িয়ে পড়ছে এবং ধোঁয়া বের হচ্ছে। তখন তার পাশে ক্যামেরা হাতে আরেকজন দাঁড়িয়ে ছিলেন, নাম আমানুল হক। রফিকুল ইসলাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার কাছে ফিল্ম আছে কি না? আমানুল হক জানালে, ২-৩টা আছে। তখন কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস নামে সরকারের তথ্য দপ্তরে কর্মরত এক সাংবাদিক তাদের বললেন, 'আপনারা কি এই লাশের ছবি তুলতে চান? যে লাশটা এখন গেল!' তারপর তারা সেখানে গিয়ে দেখলেন লাশটা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে না রেখে পাশের গুদাম ঘরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সেখান থেকেই আমানুল হক তার কাছে থাকা জার্মান জাইসাকল ক্যামেরা দিয়ে লাশটির ছবি তুললেন। লাশটি ছিল ভাষা-আন্দোলনের প্রথম শহীদ, মানিকগঞ্জের পারিল গ্রামের সন্তান রফিক উদ্দিন আহমেদের। ফিল্ম নাম থাকায় রফিকুল ইসলাম ইতিহাসের সেই মাহেন্দ্রক্ষণের সাক্ষী হতে পারলেন না।
রফিকুল ইসলাম আমতলার সমাবেশ এবং শোভাযাত্রার যেসব ছবি তুলেছিলেন, এবার সেগুলোর ফিল্ম সংরক্ষণ নিয়ে শঙ্কায় পড়লেন। কারণ চারদিক পুলিশ আর গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন ছেয়ে গেছে। বাসায় নিয়ে রাখাও নিরাপদ মনে করলেন না, কারণ বাসা তল্লাশি হতে পারে। ওই অবস্থায় তাৎক্ষণিক করণীয় ঠিক করে ফিল্মগুলো সচিবালয়ের পেছনের 'যায়দিজ' নামক স্টুডিওতে নিয়ে গেলেন। স্টুডিওর মালিক ছিলেন অবাঙালি তাই তাকে কিসের ছবি তা না জানিয়ে ফিল্মগুলো দিয়ে এলেন। যা ভেবেছিলেন, তাই হলো, বাসায় ফিরেই দেখলেন গোয়েন্দা সংস্থার দুই সদস্য এসে হাজির। তারা তাকে ছবি তুলেছেন কি না জিজ্ঞাসা করে। রফিকুল ইসলাম ফিল্ম ছিল না বলে ক্যামেরা এগিয়ে দিলেন। ক্যামেরা খুলে ভেতরে কোনো ফিল্ম না পেয়ে গোয়েন্দারা চলে গেলেন। পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি। শহীদদের রক্তশপথে উত্তাল ঢাকার শহর। দিনের আলো ফুটতেই হাজার হাজার মানুষ মুসলিম লীগ সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো রাজপথে নেমে আসে। রফিকুল ইসলাম বেরিয়ে পড়েন ক্যামেরা হাতে। আগের দিন যায়দিজ স্টুডিও থেকে ফিল্ম সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। সেই ফিল্ম ক্যামেরায় ভরে হাজির হলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণের নামাজে জানাজাস্থলে। গায়েবানা জানাজা শেষে শোভাযাত্রা বের হলে তিনি সেই শোভাযাত্রার ছবি তোলেন।
১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রথম শহীদ দিবস পালনের অনেক ছবি তুলেছেন রফিকুল ইসলাম। আজিমপুর কবরস্থানে গিয়ে ভাষাশহীদ আবুল বরকত এবং ভাষাশহীদ শফিউর রহমানের কবরের ছবি তোলেন তিনি। এছাড়া তোলেন শহীদদের কবরে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর পুষ্পাঞ্জলি অর্পণের ছবিও। এরপর ১৯৫৪, ১৯৫৫ সালের শহীদ দিসব পালনের ছবি। ১৯৫৩ সালের ঢাকা কলেজের ছাত্ররা আর ইডেন কলেজের ছাত্রীরা মিলে যে শহীদ মিনার নির্মাণ করেন, সেই শহীদ মিনার নির্মাণের দৃশ্য তিনি ক্যামেরায় ধারণ করেন।
রফিকুল ইসলাম ভাষা-আন্দোলনের ঐতিহাসিক মুহূর্তের সেই গৌরবময় অধ্যায়কে ক্যামেরাবন্দী করে জাতীয় ইতিহাসে মর্যাদার আসন লাভ করলেও এ নিয়ে তার আত্মম্ভরিতা ছিল না; বরং বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন: 'এর মধ্যে কিন্তু আমার বাহাদুরির কিছু নেই। আমি ওখানে ছিলাম, আমার কাঁধে একটা ক্যামেরা ছিল, তাতে ফিল্ম ছিল এবং আমি কলা ভবনের কিছু ছবি নিচে তুলেছি, কিছু ছবি ওপর থেকে তুলেছি। পরের দিনও ২২/২৩ তারিখে কিছু কিছু ছবি আমি তুলতে পেরেছিলাম।' তার এসব ছবি ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। কালপরিক্রমায় ভাষা-আন্দোলনের দলিলপত্র অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে, কিন্তু রফিকুল ইসলামের তোলা ছবিগুলো এখনও সেই ঐতিহাসিক ঘটনার জীবন্ত সাক্ষীরূপে টিকে আছে। প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে পৃথিবীর নানা প্রান্তে যখন আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি এই অমর সংগীতের মোহনীয় সুর বেজে ওঠে তখন রফিকুল ইসলামের ছবিগুলো হাজির হয় বায়ান্নর সেই মাহেন্দ্রক্ষণের সবচেয়ে প্রামাণ্য সাক্ষ্য হিসেবে। যতদিন বাংলা ভাষা ও একুশের চেতনার ঝাণ্ডা উড়বে ততদিন রফিকুল ইসলামের নাম মর্যাদার সঙ্গে উচ্চারিত হবে।
এম আবদুল আলীম: শিক্ষক, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়





Comments