সময় বদলেছে, বদলাতে হবে শিক্ষকদেরও
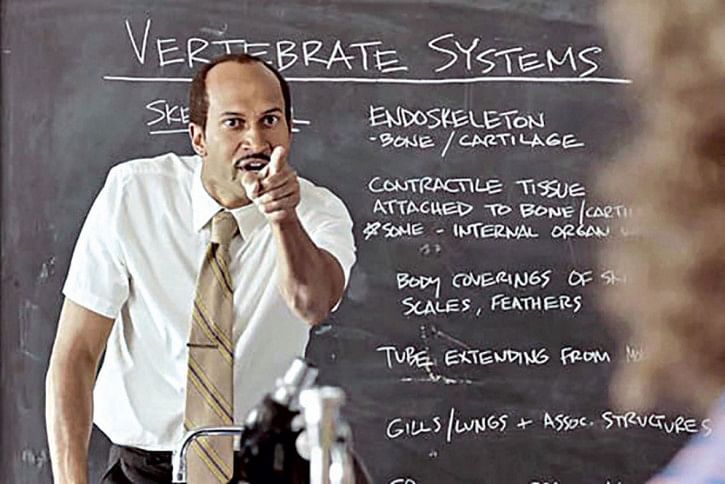
‘কোনো কিছুকে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করা এবং কারো মাঝে জ্ঞান অর্জনের আনন্দ জাগ্রত করতে পারাই একজন শিক্ষকের সবচেয়ে বড় সার্থকতা’ – আলবার্ট আইনস্টাইন
আলবার্ট আইনস্টাইনের এই পর্যবেক্ষণ কয়েক দশক পুরনো হলেও তার মূলভাব আজও শিক্ষকদের জন্য একই রকম গুরুত্ব বহন করছে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে শিক্ষকরা দেশের ভবিষ্যৎ মানবসম্পদ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। করোনা মহামারির নতুন জগতে দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষকদের এই ভূমিকাটি আরও বিস্তৃত হতে যাচ্ছে।
অনেকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস এটাই যে, বাংলাদেশে মানবসম্পদের গুণগত মান ক্রমশ কমে যাচ্ছে। চাকরি দাতারা সুযোগ পেলেই এ কথা বলেন। এই দুঃখজনক পরিস্থিতির জন্য তারা মূলত শিক্ষা খাতকেই দায়ী করেন। এই দাবির পেছনে কয়েকটি যুক্তি রয়েছে। দেশে প্রায় ৫৭টি সরকারি ও ১০৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু যখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো আন্তর্জাতিক র্যাংকিং বা স্কোরকার্ড প্রকাশিত হয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নাম সেই তালিকায় খুঁজে পেতে হলে নিচের দিক থেকে দেখা শুরু করতে হয়। কিছু কিছু র্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও সেখানে স্থান পায়নি। ‘এই র্যাংকিংগুলো বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং পক্ষপাতদুষ্ট’ দাবি করে দায় এড়ানোর চেষ্টা করে কর্তৃপক্ষ।
এটা এখন আর গোপন নয় যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের পেছনে আমাদের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলো ন্যুনতম মনোযোগটুকুও দেয় না। বিশ্বের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো আমাদের দেশের শিক্ষকদের নতুন অনুশাসন জানা কিংবা মৌলিক গবেষণা করার জন্য কোনো চাপ থাকে না। উল্টো পত্রিকার পাতায় দেখা যায় শিক্ষকদের অন্যের লেখা বা গবেষণা চুরি করে ধরা পড়ার মতো বিব্রতকর খবর। শিক্ষার্থীদেরকে তাদের শিক্ষকদের মূল্যায়ন করতে বলা হলে শিক্ষকতার সার্বিক মান নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। শিক্ষার্থীরা এ ব্যাপারটি নিয়ে কী ভাবছেন, তার দুটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল:
এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘এখানে শিক্ষার মান হাস্যকর পর্যায়ে। প্রতিষ্ঠানটি তার শিক্ষার্থী বা গবেষণার মানোন্নয়নের দিকে একেবারেই নজর দেয় না।’
আরেকজন বলেন, ‘আমি লক্ষ্য করেছি, আমার বন্ধুরা যারা দেশের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ে এসেছে, তারা অনেক বেশি শিখেছে এবং তারা সেখানে নিজেদেরকে আরও ভালোভাবে বিকশিত করতে পেরেছে। সেখানে শুধু বইয়ের প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেওয়া হয় না। বরং তাদের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে জীবন গড়ে তুলতে সহায়তা করা হয়। একবিংশ শতাব্দীতে ভালোভাবে টিকে থাকার জন্য যেসব দক্ষতা দরকার, সেগুলো শিখে নেওয়ার ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়।’
তবে কোভিড-১৯ যুগে এসে সব কিছু বদলে যাচ্ছে। ক্লাসরুমের প্রথাগত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মুখোমুখি শিক্ষাদানের পদ্ধতি বদলে গিয়ে অনলাইন শিক্ষার প্রচলন ঘটছে। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার উপযোগিতা ও উপকারিতার মান পরিমাপ করার জন্য শিক্ষার্থীদের সন্তুষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান অনেকটাই নির্ভর করে শিক্ষকের ওপর, আমরা ধরে নিতে পারি যে এ ব্যাপারটি শিক্ষার্থীদের সন্তুষ্টি এবং একই সঙ্গে শিক্ষার মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে।
মহামারির আগ পর্যন্ত শিক্ষকরা প্রথাগত ক্লাসরুমে তাদের সেরাটা না দিয়েও পার পেয়ে যেতে পারতেন। অনেক শিক্ষক তাদের শিক্ষার্থীদের পণ্য বা গ্রাহক বলে মনে করতেন। তারা ধরে নিতেন, তাদের খুশি রাখার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই। খুব কম শিক্ষকই শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সহযোগী হিসেবে বিবেচনা করতেন। মৌলিক কাজ করা বা নতুন জ্ঞান অর্জনের তাড়না না থাকার কারণে অনেকে শিক্ষক হওয়ার পর বেশ অলস ও উদাসীন হয়ে পড়েন। ভালো গ্রেড ও ডিগ্রী পেলেই অনেক সময় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়া যায়, যা ব্যাপারটিকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে গেছে।
প্রাসঙ্গিকতা বা উপযোগিতার মতো বিষয়গুলো কোর্স ডিজাইনের ক্ষেত্রে তেমন কোনো ভূমিকাই রাখে না। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পরিস্থিতি আরও খারাপ। কারণ, সেখানে জবাবদিহিতা নেই বললেই চলে। কেউ কেউ এমনও মত পোষণ করেন যে শিক্ষকরা তাদের ক্লাসে একনায়কের মতো আচরণ করে। তারা তাদের সুবিধা মতো সময়ে ক্লাস নিতে পারেন এবং চাইলে দায়সারা ভাবে নিম্নমানের লেকচার দিয়েও পার পেয়ে যেতে পারেন। এ ধরণের ক্লাস থেকে শিক্ষার্থীরা কিছুই শিখতে পারেন না। তবে অনলাইন ক্লাসের ক্ষেত্রে এ মানসিকতার পরিবর্তন আসতে বাধ্য।
একটি অনলাইন ক্লাসের কথা ভাবুন। একজন শিক্ষক প্রতিদিন নিম্নমানের লেকচার দিচ্ছেন, যা শিক্ষার্থীদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা চাইলে পরবর্তীতে আবারও ভালো করে বোঝার জন্য ক্লাসগুলো রেকর্ড করে রাখতে পারেন। আবার যারা ক্লাসটিতে উপস্থিত থাকতে পারছেন না, তাদের জন্যেও সেটি রেকর্ড করা হতে পারে। এরপর দেখা গেল কেউ না কেউ রেকর্ড করা ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করে দিলেন, যা অনেকের কাছেই উন্মুক্ত। এই নিম্নমানের লেকচারটি তখন উল্লিখিত শিক্ষকের এবং তিনি যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের ভাবমূর্তিকে কীভাবে প্রভাবিত করবে? এ ব্যাপারটিকে প্রশাসন ও নীতিনির্ধারকদের গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিৎ নয় কি? আমরা মনে করি এ ধরণের ঘটনার সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে।
একজন শিক্ষক কি চাইলেই একটি অনলাইন ক্লাসে নিজেকে দুর্বলভাবে উপস্থাপন করতে পারেন? এমনকি যে শিক্ষক অনেক অভিজ্ঞ এবং ভেবেছিলেন যে নিজেকে আর উন্নত করার প্রয়োজন নেই, ‘স্লাইড অনেক জটিল’ তাই মার্কার আর হোয়াইটবোর্ড দিয়েই ক্লাস করিয়ে যাবেন, সেই শিক্ষককেও উদ্যোগী হয়ে শিক্ষাদানের নতুন পন্থার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে হবে।
এই ডিজিটাল যুগে একজন শিক্ষক শুধু একটি নির্দিষ্ট ক্লাসরুমের উদ্দেশে লেকচার দেন না। ভার্চুয়াল জগতের কাছে সব কিছুই উন্মুক্ত। সারা দুনিয়ার মানুষ চাইলে সেই ক্লাসটি দেখতে পারেন। এই নতুন পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের ওপর একটি বাড়তি চাপ থাকে তাদের লেকচারের মান উন্নয়নের এবং দূরশিক্ষণের কৌশলগুলো আয়ত্ত করার। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম তৈরির সঙ্গে যারা জড়িত, তাদেরকেও এখন নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। কোর্সগুলোকে এমনভাবে বানাতে হচ্ছে যাতে শিক্ষার্থীরা অনলাইনে শিক্ষাগ্রহণ করেও শিক্ষক ও শিক্ষার মানের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারে।
মানুষকে শিক্ষার আলো দেওয়ার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি একটি নতুন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। যেসব শিক্ষক এই নতুন জগতের সঙ্গে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারবেন, কেবল তারাই সেরা শিক্ষক হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। অনেক শিক্ষক শিক্ষার্থীরা কী শিখছে, সেটাকে পাত্তা না দিয়েও অবকাঠামোগত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এতোদিন বহাল তবিয়তে টিকে ছিলেন। নতুন এই যুগে, এই শিক্ষকদের প্রতি তাদের শিক্ষার্থীরা দাবি জানাবে পাঠদান পদ্ধতির উন্নয়নের, অথবা আরও দক্ষ শিক্ষকদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়ার। বলাই বাহুল্য, শিক্ষার্থীদের মূল্যবান সময়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো উচিৎ। তার অপচয় করা উচিৎ না।
শিক্ষকরা দূরশিক্ষণের এই নতুন জগতে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে পড়বেন। আর তাদেরকে সেই অনুযায়ী নতুন নতুন দক্ষতা অর্জন করে নিজেদেরকে বিকশিত করতে হবে এবং সেটা করতে হবে দ্রুততার সঙ্গে। কারণ তাদের এই মহান পেশা শুধু শিক্ষার্থীদের কল্যাণের জন্যই না, বরং আমাদের জাতিকে আরও বড় সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যেও। অনেক দক্ষ মানুষের হাত ধরেই বড় সাফল্যগুলো আসবে।
মঙ্গলময় শিক্ষার আলো ও অগ্রগতির জন্য জাতি মূলত ভালো শিক্ষকদের দিকেই মুখ তুলে তাকিয়ে আছে।
সৈয়দ রাফি মোর্শেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে এমবিএ করছেন। ড. আন্দালিব পেনসিলভেনিয়া রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর ইমেরিটাস এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য। ড. আন্দালিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ অনুষদের শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় এই নিবন্ধটি তৈরি করেন এবং অপ-এডের জন্য উপস্থাপন করেন। অপ-এডগুলো লেখা হয়েছে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ওপর আলোকপাতের মাধ্যমে এবং একে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে। ‘একাডেমিক এক্সপেরিয়েন্স প্রকল্প’তে অবদান রাখতে ইচ্ছুক যে কোনো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ড. আন্দালিবের সঙ্গে [email protected] মেইলে যোগাযোগ করতে পারেন।
(দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে লেখকের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে। প্রকাশিত লেখাটির আইনগত, মতামত বা বিশ্লেষণের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে লেখকের, দ্য ডেইলি স্টার কর্তৃপক্ষের নয়। লেখকের নিজস্ব মতামতের কোনো প্রকার দায়ভার দ্য ডেইলি স্টার নেবে না।)





Comments