রবীন্দ্রনাথের ঢাকা দর্শন
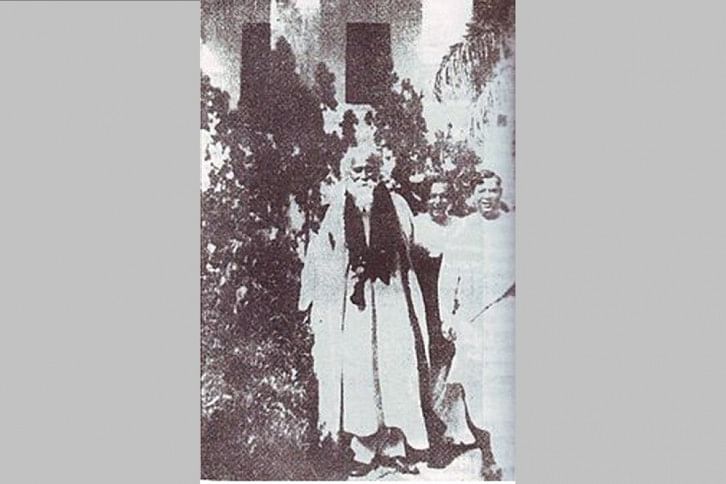
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্ববঙ্গে এসেছেন অজস্রবার। এখানকার অবারিত সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বাংলাদেশে না এলে তার প্রকৃতির অবারিত দ্বার দেখা থেকে তিনি বঞ্চিত হতেন। পূর্ববঙ্গের সৌন্দর্য, পূর্ববঙ্গের মানুষ তার সাহিত্যে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন ১৮৮৮ সালে। আর ১৮৮৯ সালের নভেম্বর মাসে তো পূর্ববঙ্গের জমিদারির দায়িত্বই নিলেন।
১৮৮৮ সাল থেকে ১৯১৫ এই সময়ে বহুবার পূর্ববঙ্গে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। থেকেছেন অগণিত দিন। নিজের জমিদারি অঞ্চল পাবনার (বর্তমানের সিরাজগঞ্জ জেলা) শাহজাদপুর, নওগাঁর পতিসর, কুষ্টিয়ার শিলাইদহ ছিল তাদের জমিদারির অঞ্চল। এই তিন কাছারিতে রবীন্দ্রনাথ এসেছেন অনেক বার। রবীন্দ্রনাথ শেষ আসেন ১৯৩৭ সালে পুণ্যাহ উৎসব উপলক্ষে। তখন তিনি জমিদার নন, বরং অতিথি হিসেবে আসেন। এই তিন জায়গাই নয়, রবীন্দ্রনাথ ঘুরেছেন পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী। চাঁদপুর দিয়ে কুমিল্লা হয়ে গিয়েছিলেন ত্রিপুরার আগরতলায়ও। সালটা ১৯০৭।
পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে বড় শহর এবং রাজধানী ঢাকা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঢাকা সফর নিয়েই আজকের আলোচনা। রবীন্দ্রনাথ তার জীবনে ঢাকায় এসেছেন দুবার। একবার ১৮৯৮ সালে, অন্যবার ১৯২৬ সালে। প্রথমবার ১৮৯৮ সালে (১৩০৫ বঙ্গাব্দ) তিনি ঢাকায় এসেছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের ১০ম অধিবেশনে যোগ দিতে। প্রথমবার তথা ১৮৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথের ঢাকা আসা নিয়ে তেমন শোরগোল হয়নি। সেবার তিনি ঢাকায় ছিলেন তিন দিন। ৩০ মে থেকে পহেলা জুন অব্দি এই তিন দিন তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এর আগে ইন্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটির সভায় রবীন্দ্রনাথসহ ঠাকুর পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্যকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছিল। সেই প্রতিনিধি দলে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দাদা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগদানকারী প্রথম ভারতীয়, লেখক সংগীতস্রষ্টা ও ভাষাবিদ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয়তাবাদী নেতা ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, প্রখ্যাত শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্মেলনে যোগ দিতে ২৯ মে ঢাকায় এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অসুস্থ শরীর নিয়েই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তিনি।
সম্মেলনের প্রথম দিন ৩০ মে সম্মেলন শুরু হয়েছিল দুপুর দুটোয় ঢাকায় ক্রাউন থিয়েটার হলে। রেভারেল্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি সম্মেলনে ইংরেজিতে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ভাষণের বাংলা উপস্থাপন করেছিলেন। প্রথমদিনের সম্মেলন শেষ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের “আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না” গানের মধ্য দিয়ে।
দ্বিতীয়দিন সম্মেলন শুরু হয়েছিল বেলা সাড়ে ১২টায়। এদিন বক্তব্য দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার বক্তব্যে তিনি কিছু প্রস্তাব রাখেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবগুলো বাংলায় উপস্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথ।
দ্বিতীয়দিন অতিথিদের জন্য ছিল বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌ বিহারের আয়োজন। রবীন্দ্রনাথ ও অতিথিরা সেই নৌ বিহারে যোগ দিয়েছিলেন।
সম্মেলনের শেষ দিন ছিল রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা। রবীন্দ্রনাথ সমাপ্তি বক্তব্য দিয়েছিলেন। শেষ দিন ১০টি প্রস্তাব উঠেছিল সম্মেলনে। পরবর্তী বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন ২৪ পরগনায় অনুষ্ঠিত হবে প্রস্তাব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সম্মেলনেই বাংলা ভাষা প্রবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সম্মেলনে একে তো প্রতিনিধির সংখ্যাও ছিল স্বল্প দ্বিতীয়ত তার প্রস্তাবের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছিলেন মাত্র তিন জন। সম্মেলন শেষে শিলাইদহ ফিরে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখান থেকে তিনি ইন্দিরা দেবীকে চিঠিতে লিখেছিলেন। চিঠির ভাষ্যটা এমন, “সমস্ত বঙ্গদেশকে এই সমিতি কতদূর একতাসুত্রে বাঁধিতে পারিতেছেন তাহাই প্রত্যেক অধিবেশনের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ কথা। অথচ এত বৎসর বাঙালির প্রাদেশিক সমিতির তর্ক বিতর্কে বাঙালির ভাষার সম্যক সমাদর লাভ করিতে পারিলো না।”
তার ক্ষোভের আরেকটি বক্তব্য পাওয়া যায় তার পরবর্তী ঢাকা সফরে করোনেশন পার্কে দেয়া স্মৃতিমূলক বক্তব্যে।
রবীন্দ্রনাথ প্রথমবারও বুড়িগঙ্গায় এসেছিলেন। সেবার সফরের দ্বিতীয় দিন বিক্রমপুরের ভাগ্যকূলের জমিদারদের সৌজন্যে বুড়িগঙ্গা নদীতে এক নৌ ভ্রমণের আয়োজন করা হয়েছিলো। সেখানে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হয়ে ভাগ্যকুলের ধনাঢ্য জমিদারদের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন।
দ্বিতীয়বার রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় আসেন ১৯২৬ সালে ৯ দিনের সফরে। দ্বিতীয়বার রবীন্দ্রনাথের ঢাকা সফর নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় গোটা শহরে। রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে ঢাকায় এসেছিলেন গোয়ালন্দ, নারায়ণগঞ্জ হয়ে।
প্রথমে কলকাতা থেকে ট্রেনে গোয়ালন্দ, তারপর স্টিমারে করে গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জ, সেখান থেকে মোটর শোভাযাত্রায় ঢাকায়। রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় এসে পৌঁছেছিলেন ৭ জানুয়ারি। রবীন্দ্রনাথের সেই সফর নিয়ে ঢাকার গণ্যমান্য সমাজে বিভক্তির দেখা দেয়। কারণ তখন তিনি প্রচণ্ড জনপ্রিয়। সবাই তার সমাদরে ব্যস্ত। স্পষ্টতই বিপাকে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। কারণ তিনি তো কোনো বিশেষ ব্যক্তির নিমন্ত্রণে আসেননি। এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের এই ঢাকা সফরের পিছনে অধ্যাপক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের অবদান ছিল অসামান্য। রবীন্দ্রনাথের প্রথমে থাকার কথা ছিলো রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে। কিন্তু সবাই তার সঙ্গ পেতে চায়। ঢাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাফ কথা, রবীন্দ্রনাথ শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রমেশচন্দ্র মজুমদারের একার অতিথি নয়, তিনি সমস্ত ঢাকাবাসীর অতিথি। সবার চায় তাদের বাড়িতেই থাকবেন রবীন্দ্রনাথ। এদিকে নবাব পরিবার এক প্রস্তাব দিয়েছিল এর আগে। তাই মোটর শোভাযাত্রা গিয়ে পৌঁছে বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে। রবীন্দ্রনাথ অবস্থান করেন বুড়িগঙ্গা নদীর ওয়াইজ ঘাটে নবাব সলিমুল্লাহ'র ছেলে খাজা হাবিবুল্লাহ'র বিলাসবহুল জলযান তুরাগ হাউস বোটে।
সফরে তুরাগ হাউস বোটে অবস্থানকালীন সময়ে প্রতিদিন সকালে রবীন্দ্রনাথ ঢাকার নবাবদের মোটর চালিত বোটে বুড়িগঙ্গায় ভ্রমণে বের হতেন। এসময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে থাকতো বই, কিছু কাগজ। প্রায় ছয় থেকে সাত মাইল ভ্রমণ করতো মোটরচালিত বোট।
রমেশচন্দ্র মজুমদারকে রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “ঢাকার জনসাধারণের পক্ষ থেকে আমাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য দূত এসেছিলেন। তাঁদের বিশেষ অনুরোধে নির্দিষ্ট সময় পূর্বে যাত্রা করতে প্রস্তুত হয়েছি। ৬ তারিখ রাত্রে রওনা হয়ে গোয়ালন্দ থেকে তাদেরই জলযানে ভেসে পড়বো। ১০ই তারিখ পর্যন্ত তাঁদের আতিথ্য ভোগ করে কর্তব্য অন্তে তোমার আশ্রমে উঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ পালন করব। নইলে আমাকে দীর্ঘকাল ঢাকা থাকতে হয়। আমার সময় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিঃস্থিত ঢাকার লোকের নিমন্ত্রণ কোনমতেই উপেক্ষা করা উচিৎ বোধ করিনে। তাই দুই নিমন্ত্রণ ক্ষেত্রে আমার সময়কে বিভক্ত করে দিলুম। যে কয়দিন তোমাদের দিবো স্থির করেছিলুম সেই কয়দিন সম্পূর্ণই রইল।”
বুদ্ধদেব বসু তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র। তিনি তার 'আমার ছেলেবেলা' গ্রন্থে স্মৃতিচারণায় লিখেছিলেন, “রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রথম দেখেছিলাম বুড়িগঙ্গার ওপর নোঙর ফেলা একটি স্টিমলঞ্চে। সেখানে নিমন্ত্রণকর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রেষারেষি করে ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিকেরা তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। উপরের ডেকে ইজি চেয়ারে বসে আছেন তিনি। ঠিক তাঁর ফটোগ্রাফগুলোর মতোই জোব্বা-পাজামা পরনে। আর কেউ কেউ উপস্থিত। রেলিং-এ হেলান দিয়ে আমি দূরে দাঁড়িয়ে আছি।”
১৯২৬ সালে ঢাকা সফরে রবীন্দ্রনাথের সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ছেলে রথীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রধান স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র সহযোগী কালীমোহন ঘোষ, ইতালির খ্যাতনামা অধ্যাপক জিয়োসেপ্নে তুচ্চি।
ঢাকায় রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা দিয়েছিল বেশ কয়েকটি সংগঠন, কবির সফরের সময় স্বল্পতা ছিল বলে অনেকে কবিকে পাওয়ার আবেদন করেও পায়নি। কবিকে প্রথম সংবর্ধনা দিয়েছিল ঢাকা পৌরসভা ও পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছিল নর্থ ব্রুক হলে। রবীন্দ্রনাথতে ঢাকার মানুষের পক্ষ থেকে মানপত্র দেয়া হয়েছিল। ঢাকা মনমোহন প্রেসে ছাপা সেই মানপত্র অনুষ্ঠানে পাঠ করেছিলেন আর কে দাস।
ঢাকা পৌরসভা ও পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতায় বলেছিলেন, “আপনারা আমাকে যে সাদর অভিবাদন করলেন আমি তার যথাযোগ্য প্রত্যাভিবাদন করতে পারি এমন শক্তির আমার অভাব ঘটেছে। আপনারা বোধ হয় শুনে থাকবেন আমি ভীষণ দুর্বল ও ক্লান্ত। সে কথা সহসা আপনারা সকলে হয়তো গ্রাহ্য না করতে পারেন। সে জন্য আমিই দায়ী, কারণ, আজ আমার এখানে উপস্থিতিই শারীরিক অপটুতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। যখন আপনাদের নিমন্ত্রণ আমার কাছে পৌঁছল, দুর্বল শরীর বললে, নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারব না। কিন্তু মনেরও যেঁ দুর্বলতা আছে তাই আপনাদের ডাক এড়াবার সাধ্য রইল না। মন তখন বলে, হ্যাঁ। শেষে মনেরই জিত হলো। ডাক্তারের উপদেশ লঙ্ঘন করেই এসেছি, এখন আর অসুস্থ শরীরের দোহাই দিয়েই কি হবে? অতএব আমাকে কিছু বলতেই হবে, কেবল আমার আবেদন এইটুকু যেঁ আমার কাছে বেশি বলা দাবী করবেন না।”
বক্তৃতার আগে রবীন্দ্রনাথকে যে মানপত্র প্রদান করা হয়েছিল সেখানে লেখা ছিল,
“বাণীর বরপুত্র তুমি। শ্বেত- সরোজবাসিনী বীণাপাণি তাঁর শ্রীকর ধৃত বীলা তোমারই করকমলে অর্পণ করিয়াছেন। তাহার ত্রিতন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলিয়া অমর গীতধারায় তুমি বিশ্বজগত প্লাবিত করিয়াছ। প্রাচীন - ইতিহাস -বিশ্রুত, হিন্দু - মোসলেমের শতকীর্তি বিভূষিত, শিল্পকলা- প্রশিদ্ধ- ঢাকা নগরীর অধিবাসী আমরা, তোমাকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি।”
সেবার ঢাকা পৌরসভা ও পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ছাড়াও রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা দেয় জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলজিয়েট স্কুল, ডাকসু, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ, রেটপেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজ, দীপালি সংঘ, হিন্দু মোসলেম সেবা সংঘসহ বেশ কয়েকটি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান। আবার অন্যদিকে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ঢাকা সাহিত্য পরিষদ, ইডেন গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, লালেগ্রা ক্লাব। তবে এসব অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ হাজির থাকতে পারেননি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জর্জ হ্যারি ল্যাংলির দেয়া নৈশভোজেও রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকতে পারেননি।
৮ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ নবাব পরিবারের আহসান মঞ্জিলে আয়োজিত চা চক্রে অতিথি হিসেবে যোগ দেন।
সেদিন সন্ধ্যায় পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে অনুষ্ঠিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথকে মানপত্র প্রদান করে দীপালি সংঘ। ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকার বিশিষ্ট মহিলারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে তাকে অভ্যর্থনা জানান। তার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন ঢাকার বিপ্লবীদের কয়েকজন সদস্য। একই দিন বুড়িগঙ্গায় তুরাগ বোটে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুখরঞ্জন রায়।
তিনি স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন, 'কবি থাকতেন বজরায়। বুড়িগঙ্গার বক্ষে বজরার ওপর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। ডা. মজুমদার, ডা. ঘোষ, ব্যারিস্টার আর কে দাশ প্রভৃতি ঢাকার গণ্যমান্যদের অনেকে উপস্থিত ছিলেন সেখানে। কবির বয়স সম্বন্ধে আলাপ হচ্ছিল। তাঁর বয়স তখন বোধ হয় চৌষট্টি ছিল। ডা. মজুমদার আমার পরিচয় করে দেন।'
তৃতীয় দিন তথা ৯ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা দেয় বিশ্বভারতীর সম্মিলনী ঢাকা শাখা। তারপর তাকে জগন্নাথ কলেজে সংবর্ধনা দেয়া হয়। সেদিন সন্ধ্যায় ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে এক বক্তৃতা দেন রবীন্দ্রনাথ। বক্তৃতার বিষয় ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার স্বরূপ।
চতুর্থ দিন রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে বক্তৃতা দেন। সেদিন দুপুরে কবিকে সংবর্ধনা দেয় ঢাকা কলজিয়েট স্কুলের ছাত্ররা। ওই দিন বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ (ডাকসু) কবিকে সংবর্ধনা দিয়েছিল কার্জন হলে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জর্জ হ্যারি ল্যাংলি। সেদিন মুসলিম হল ছাত্র ইউনিয়নও রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা দিয়েছিল।
পরের দুই দিন তথা ১১ ফেব্রুয়ারি এবং ১২ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ অসুস্থতার কারণে কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দেননি।
১৩ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ "দ্যা রুল অব দ্যা জায়ান্ট" শিরোনামে কার্জন হলে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।
১৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ইডেন কলেজের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক কবির সঙ্গে দেখা করতে তুরাগ হাউস বোটে যান। এদিন বিকেলে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল অপূর্ব কুমার চন্দের (পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব) বাড়িতে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে যোগ দেন রবীন্দ্রনাথ। ওই অনুষ্ঠানে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর গান গেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন।
১৫ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ থাকার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্রদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যেতে পারেননি, তবে তিনি আগের দিন রাতে একটি গান লিখেছিলেন হলের বার্ষিকী সাহিত্য সাময়িকীর জন্য। এদিন ছিল একইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় বিদায়ী দিন। ১৫ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।
বুড়িগঙ্গায় বোটে রবীন্দ্রনাথ জগন্নাথ হলের বার্ষিক সাময়িকীর জন্য লিখেছিলেন,
“ভারী কাজের বোঝাই তরী কালের পারাবারে
পাড়ি দিতে গিয়ে কখন ডোবে আপন ভারে।
তার চেয়ে মোর এই ক-খানা হালকা কথার গান
হয়তো ভেসে বইবে স্রোতে তাই করে যাই দান।”
তথ্যসূত্র -
আমার ছেলেবেলা/ বুদ্ধদেব বসু
ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ/ গোপাল চন্দ্র রায়
বাংলাদেশে রবীন্দ্র সংবর্ধনা/ ভূঁইয়া ইকবাল
রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ/ ভূঁইয়া ইকবাল
রবি জীবনী ৪র্থ খণ্ড/ প্রশান্ত কুমার পাল
আহমাদ ইশতিয়াক [email protected]
আরও পড়ুন:





Comments