জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের মুক্তি কেন জরুরি ছিল

আজ থেকে ১৭ বছর আগে বাগদাদের রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছিলেন কয়েকজন, কথা বলছিলেন নিজেদের মধ্যে। হঠাৎ একটা মার্কিন হেলিকপ্টার থেকে তাদের ওপর ব্রাশফায়ার করা হয়। ২০০৭ সালের ১২ জুলাইয়ের ওই হামলায় অন্তত ৮ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হন, যাদের মধ্যে রয়টার্সের দুজন সাংবাদিকও ছিলেন।
এই হত্যাকাণ্ডের পর রয়টার্সের পক্ষ থেকে একাধিকবার আইনী উপায়ে হেলিকপ্টারে রেকর্ড করা ভিডিও চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু মার্কিন প্রশাসন সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে।
মার্কিন প্রশাসনের দাবি ছিল, হামলাটি প্রতিরক্ষামূলক, বিধিসম্মত। এক পর্যায়ে এই হামলার কথা মানুষ ভুলেও যায়।
তবে এর তিন বছর পর ২০১০ সালের এপ্রিলে 'কোলাটেরাল মার্ডার' শিরোনামে ইন্টারনেটে একটি সাদা-কালো ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। বাগদাদে সেই আমেরিকান হেলিকপ্টার থেকে রেকর্ড করা ভিডিওতে দেখা গেছে, কোনো কারণ ছাড়াই আমেরিকান সৈন্যরা হাসতে হাসতে একদল নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলে। এমনকি এক দফা হামলা করার পর আরেক দফা হামলা করার জন্যও তারা বারবার অনুমতি চেয়েছে এবং দ্বিতীয়বারের মতো হামলা চালিয়েছে।
এই এক ভিডিওতে গোটা বিশ্বের মানুষ প্রথমবারের মতো আমেরিকার জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রকৃত রূপ দেখতে পায়-যা ছিল সরাসরি ঠাণ্ডা মাথার নির্মম হত্যাকাণ্ড ও যুদ্ধাপরাধ।
ভিডিওটি প্রকাশ করা হয়েছিল 'উইকিলিকস' নামে একটি ওয়েবসাইট থেকে। যার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন এক অস্ট্রেলিয়ান, নাম তার জুলিয়ান অ্যাস্যাঞ্জ। উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠা ২০০৬ সালে হলেও সংস্থাটি তুমুল আলোচনায় আসে ২০১০ সালে ওই ভিডিওটি প্রকাশের পর।
এখন পর্যন্ত দশ মিলিয়নের বেশি সরকারি গোপন নথি প্রকাশ করেছে উইকিলিকস। আর এর মাধ্যমেই রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন অ্যাস্যাঞ্জ ও তার সঙ্গীরা।
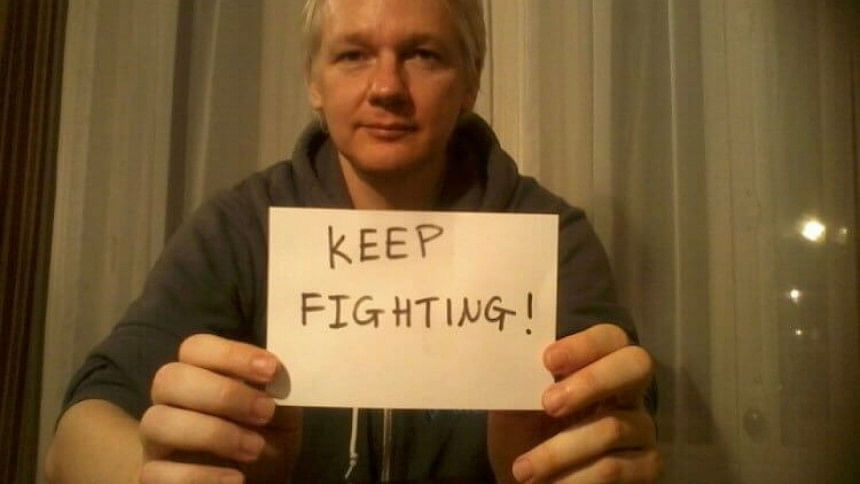
সাইফারপাংক, উইকিলিকস ও অ্যাসাঞ্জ
তথ্য অধিকারকর্মী ও 'সাইফারপাংক' অ্যাস্যাঞ্জের জন্ম ১৯৭১ সালে। কিশোর বয়সেই তিনি হ্যাকিংয়ে আগ্রহী হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে যুক্ত হন নিজেদের সাইফারপাংক (cypherpunk) হিসেবে পরিচয় দেওয়া একদল প্রযুক্তিবিদের সঙ্গে।
উইকিলিকসে অ্যাস্যাঞ্জের কাজ বুঝতে গেলে সাইফারপাংকদের সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা আর সরকারের স্বচ্ছতার ব্যাপারে অ্যাসাঞ্জের চিন্তাধারা শুরু এই সাইফারপাংকদের মাধ্যম্যেই।
সাইফারপাংক মূলত একদল প্রযুক্তিবিদ, যারা ক্রিপ্টোগ্রাফি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য কাজ করতেন। এই আন্দোলনের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারি কেন্দ্রীয় নজরদারির বাইরে মানুষের প্রাইভেসি নিশ্চিত করে এমন বিকেন্দ্রীক নিরাপদ ডিজিটাল ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত 'দি ক্রিপ্টো অ্যানার্কিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে এমনটাই বলা হয়েছে।
সাইফারপাংকরা সেসময় নিজেদের মেইলিং লিস্টের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করত। ১৯৯৩ এর শেষ দিকে অ্যাস্যাঞ্জও সেই মেইলিং লিস্টে যুক্ত হন। সেই মেইলিং লিস্টের সদস্যরা এখনও নিজ নিজ অবস্থানে মানুষের ডিজিটাল অধিকারের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন।
এভাবেই অ্যাস্যাঞ্জের হ্যাকিংয়ের প্রতি আগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হয় রাজনৈতিক চিন্তা। বিশ্বের ক্ষমতা-কাঠামোগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় তথ্যই ক্ষমতা। আর সেই তথ্যের নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন কর্তৃত্ববাদী সংগঠন। সরকার আর প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো মানুষের ওপরে নজরদারি চালায়। কে কোথায় কী করছে, কার সঙ্গে দেখা করছে, কার সঙ্গে সখ্যতা, কার সঙ্গে মনোমালিন্য–একজন মানুষের পুরো জীবন এই নজরদারির আওতাধীন।
কিন্তু অন্যদিকে সরকারের ব্যাপারে মানুষ কী জানে? সরকারের সম্মতির বাইরে কিছুই জানে না। সরকারগুলো কী সিদ্ধান্ত নেয়, কী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে-তার সবই রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তায় মানুষের জানাশোনার আড়ালে থাকে। অ্যাস্যাঞ্জ মূলত মানুষকে রাষ্ট্রের এসব কর্মকাণ্ড জানানোর এই কাজটিই করেছেন, যার রাজনীতি হলো কর্তৃত্ববাদ-বিরোধিতা।
অ্যাস্যাঞ্জের মতে, যুদ্ধ যদি মিথ্যা দিয়ে শুরু হয়, তবে তা বন্ধ হবে সত্যের মাধ্যমেই। উইকিলিকসের মতাদর্শও তাই। উইকিলিকসের ম্যানিফেস্টো হিসেবে ধরা হয় অ্যাস্যাঞ্জের রচনা 'কনস্পিরেসি অ্যাজ গভার্ন্যান্স'কে।
যার শুরুতেই তিনি লিখেছেন, রাষ্ট্রগুলো নিজেদের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করতে চায় না, যদি তা পরিবর্তন করতে হয় তাহলে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে।
উইকিলিকস শক্তিশালী এনক্রিপশন প্রযুক্তির মাধ্যমে হুইসেলব্লোয়ারদের (প্রাতিষ্ঠানিক গোপন তথ্য ফাঁসকারী) একটি নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম দেয়–যেখানে হুইসেলব্লোয়াররা নিজেদের পরিচয় প্রকাশ ছাড়াই গোপন নথি পাঠাতে পারে।
উইকিলিকস ও অ্যাস্যাঞ্জের লক্ষ্য একটি মুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা হলো প্রধান উপাদান।
অ্যাস্যাঞ্জের মতে, রাষ্ট্রীয় এসব গোপনীয়তা মূলত জনগণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রগুলোর ষড়যন্ত্র। এসব 'ষড়যন্ত্র'ই কর্তৃত্ববাদী নিপীড়নকে জনগণের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। তারা জনগণকে সত্য জানতে দেয় না। কিন্তু যখনই মানুষ এই সত্যগুলো সম্পর্কে জেনে যাবে, তখনই পরিবর্তন শুরু হবে মুক্তির পথে।
অ্যাসাঞ্জের বিরুদ্ধে অভিযোগ, মামলা, শাস্তি
২০১৯ সালে ট্রাম্প প্রশাসন আনুষ্ঠানিকভাবে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি আইনে ১৮টি অপরাধে বিচার শুরু করে। প্রাথমিকভাবে অভিযোগ করা হয় যে, হুইসেলব্লোয়ার চেলসি ম্যানিংয়ের সহযোগিতায় অ্যাসাঞ্জ মার্কিন জাতীয় প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত গোপন নথিগুলো বেআইনিভাবে সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন।

উইকিলিকসে প্রকাশিত এই নথিগুলোর মধ্যে আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ, গুয়ানতানামো বে'র বন্দিদের নির্যাতন এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের গোপন বার্তা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে দোষী সাব্যস্ত হলে অ্যাস্যাঞ্জকে ১৭৫ বছর কারাবাসের সাজা পেতে হতো।
এই মামলায় গুপ্তচরবৃত্তির কথা বলা হলেও অ্যাস্যাঞ্জের 'অপরাধ' মূলত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও সত্য প্রকাশের আওতায় পড়ে। অভিযোগগুলো মোটা দাগে এই যে–২০১০ থেকে ১১ সালের মধ্যে অ্যাস্যাঞ্জ ও চেলসি ম্যানিং একধরনের ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিলেন; চেলসি ম্যানিং যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় প্রতিরক্ষা বিষয়ক নথিপত্র অবৈধভাবে অ্যাস্যাঞ্জকে দিয়েছেন। আর অ্যাস্যাঞ্জ সেই তথ্যগুলো প্রকাশ করেছেন।
এই পুরো প্রক্রিয়াটি সাংবাদিকতার বাইরে অন্য কিছু নয়। কেননা একজন সাংবাদিক কোনো গোপন নথি সংগ্রহ করা ছাড়া তা প্রকাশ করতে পারেন না। আর এসব গুরুত্বপূর্ণ নথি প্রকাশ না করা গেলে সাংবাদিকতা পেশাটিও গুরুত্ব হারায়।
প্রথাগত সাংবাদিকদের অনেকে অ্যাস্যাঞ্জের নথি প্রকাশের সময় কিছু র্যাডিকেল নীতিমালার কারণে তাকে অনুসন্ধানী সাংবাদিক হিসেবে স্বীকার করতে চাননি।
কিন্তু অ্যাস্যাঞ্জের বিরুদ্ধে এই মামলা শুধু অ্যাস্যাঞ্জের জন্যই নয়–যুক্তরাষ্ট্র ও সারা বিশ্বের সাংবাদিকদের জন্যও বিপজ্জনক। এই মামলায় তাকে সাজা দেওয়া সম্ভব হলে এই আইনের মাধ্যমে পরবর্তীতে অন্যান্য বড় বড় সংবাদ প্রতিষ্ঠানকেও তাদের পেশাদারি কাজের জন্য শাস্তি পেতে হবে এবং যখনই কেউ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য প্রকাশ করতে যাবে, তাকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।
অবশেষে গত ২৬ জুন ১৮টি অভিযোগের মধ্যে একটি অভিযোগ স্বীকার করে নেওয়ার শর্তে জুলিয়ান অ্যাস্যাঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রের মামলা থেকে রেহাই পান।
আইনি ভাষায় এটি স্বীকারোক্তি হলেও, অ্যাস্যাঞ্জ আদালতে নিজের অবস্থান থেকে সরেননি।
তিনি আদালতে বলেছেন, 'একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি আমার সোর্সকে গোপন তথ্য প্রদান করতে উৎসাহ দিয়েছি, যেন আমি সেই তথ্য প্রকাশ করতে পারি। আমি বিশ্বাস করি যে ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট এই কাজকে সুরক্ষা দেয়। আমি মনে করি ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট এবং গুপ্তচরবৃত্তি আইন একে অপরের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কিন্তু আমি মেনে নিয়েছি যে, এসব পরিস্থিতি বিবেচনায় এমন একটি মামলায় জয়ী হওয়া কঠিন হবে।'
অর্থাৎ, আদালতে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে দোষ স্বীকার করতে গিয়েও অ্যাস্যাঞ্জ জানিয়ে দিলেন–তিনি আসলে সাংবাদিকতাই করেছেন।
আজকের সময়ে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কর্তৃত্ববাদী শাসনের নতুন জাগরণ ঘটছে, তখন অ্যাস্যাঞ্জের মুক্তি আশা জোগায়। আস্যাঞ্জের মুক্তি প্রাতিষ্ঠানিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে বড় অনুপ্রেরণা।









Comments