‘একুশ’ নিয়ে বিশ্বমানের চলচ্চিত্র নির্মিত হোক
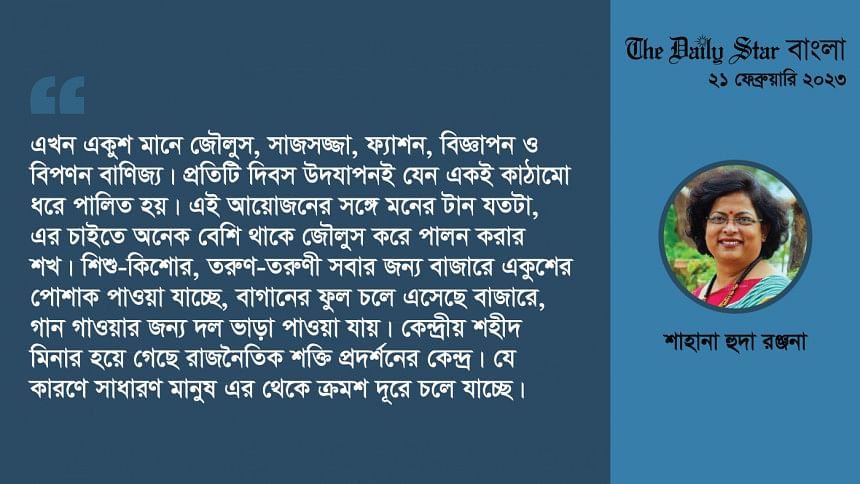
আসাদগেট নিউকলোনিতে একটি ছোট শহীদ মিনার ছিল। প্রায় ৪৫ বছর পরেও চোখ বন্ধ করলে আমি সেই শহীদ মিনারকেই দেখি। কলোনির বিভিন্ন গাছ থেকে ফুল চুরি করে এই বেদিতে অর্পণ করতাম। বাগানের মালিকরা জানতেন, কিন্তু কখনো বাধা দেননি। ছোট শহীদ মিনারটিতে অনুষ্ঠান হতো, আমরা গান গাইতাম, কবিতা আবৃত্তি করতাম। সেখানে কলোনি ছাড়াও লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর থেকে দর্শক, শ্রোতারাও আসতেন, ফুল দিতেন।
আবার কখনো কখনো ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ১৫ থেকে ২০ জন শিশু-কিশোর গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে, গামছায় ঢোল বেঁধে, সাদা কাপড় পরে, ফুল হাতে নিয়ে খালি পায়ে চলে যেতাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে—আসাদগেট থেকে আজিমপুর। কণ্ঠে ধ্বনিত হতো 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'। সেটাই ছিল আমাদের প্রভাতফেরির মিছিল।
শিশু-কিশোরের দলটি কীভাবে যে গান গাইতে গাইতে, পরাণভরা ভালোবাসা নিয়ে, পায়ে হেঁটে প্রভাতফেরির মিছিলে অংশ নিতো, তা এখন আর ভাবতে পারি না। বিত্ত-বৈভব, নতুন পোশাক, স্টাইল কিচ্ছু ছিল না আমাদের, শুধু ছিল অদেখা বীরদের জন্য আবেগ আর ভালোবাসা। আমরা জানতাম আমাদের এই দেশ, ভাষা, পরিচয় সবকিছু সেই বীরদের দান। কাজেই তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য আমাদের শহীদ স্বপ্নের কাছাকাছি পৌঁছাতেই হবে।
খেলাঘরের বড় ভাইবোনেরা প্রতিবছর একুশের গল্প শোনাতেন, ছবি দেখাতেন, ছবি আঁকতে দিতেন, দেয়াল পত্রিকা বের করাতেন আমাদের দিয়ে। সেই বয়সেই শুনেছি রফিক, জব্বার, বরকত, সালামের গল্প। শুনেছি শহীদ আলতাফ মাহমুদ ও আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর কথা। পাড়ার শিশু সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকার সুবাদে, বইয়ে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পড়ার আগেই, ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত মানুষগুলোর প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।
একুশে ফেব্রুয়ারির প্রতি সেই যে ভালোবাসা-শ্রদ্ধা মনে গেঁথে গিয়েছিল, আজ পর্যন্ত তা অম্লান হয়ে আছে। আমরা আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে যেমন শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছি, তেমনি গিয়েছি পরিবারের সঙ্গে, আব্বা-আম্মার হাত ধরে।
এখন একুশ মানে জৌলুস, সাজসজ্জা, ফ্যাশন, বিজ্ঞাপন ও বিপণন বাণিজ্য। প্রতিটি দিবস উদযাপনই যেন একই কাঠামো ধরে পালিত হয়। এই আয়োজনের সঙ্গে মনের টান যতটা, এর চাইতে অনেক বেশি থাকে জৌলুস করে পালন করার শখ। শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী সবার জন্য বাজারে একুশের পোশাক পাওয়া যাচ্ছে, বাগানের ফুল চলে এসেছে বাজারে, গান গাওয়ার জন্য দল ভাড়া পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হয়ে গেছে রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের কেন্দ্র। যে কারণে সাধারণ মানুষ এর থেকে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে।
একটা সময় একুশে ফেব্রুয়ারি আর বইমেলা ছিল ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণী ও যুবাদের প্রাণের পরিচয়। একুশ মানে আমরা জানতাম কবিতা উৎসব, স্বৈরাচার-বিরোধী কবিতা পাঠের আসর, গানের আসর, আলোচনা, মিটিং, মিছিল। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, টিএসসি চত্বর, বইমেলা জমজমাট। নবীন-প্রবীণ লেখক, কবি, অভিনেতা, রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, আঁকিয়ে, সাংবাদিক, আবৃত্তিকার, গায়ক, ছাত্র-ছাত্রী, শিল্পীদের পদচারণায় চারিদিক ছিল সরগরম। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারকে গদিচ্যুত করার সব আয়োজন যেন এই ফেব্রুয়ারিকে ঘিরেই করা হয়েছিল।
একুশের বইমেলা আমাদের কাছে শুধু মেলা ছিল না, ছিল প্রাণ। বইমেলা আজ তার প্রকৃত জৌলুস হারিয়েছে। হয়তো বেড়েছে আয়তন, শান-শওকত, রাজনীতি, লেখক বিভাজন, নিয়ম-কানুন, স্টলের সংখ্যা ও সৌন্দর্য। কিন্তু কমেছে ভালো বইয়ের কদর, কমেছে পড়ুয়ার সংখ্যাও। স্বাধীনতার পরের কয়েকটি প্রজন্মের শিশু-কিশোর ও তরুণরা যেভাবে একুশকে দেখেছে, ২০০০ সাল পরবর্তী প্রজন্ম সেভাবে দেখেনি, বরং অনেকটাই উপেক্ষা করা হয়েছে এই অর্জনকে।
শহীদ স্বপ্নের কাছাকাছি যেতে যেতে লক্ষ্য করছি সময় বদলে গেছে, আমরা বদলে গেছি, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাও বদলে গেছে। একদিন লক্ষ্য করলাম শহীদ বেদি থেকে অনেকটাই দূরে সরে এসেছি। একুশ উপলক্ষে তৈরি করা বিভিন্ন ব্যানারে যখন দেখি ভাষা শহীদদের ছবির পরিবর্তে বীরশ্রেষ্ঠদের ছবি ব্যবহৃত হচ্ছে, তখন আর অবাক হই না। আমাদের শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিধি এতটাই দুর্বল হয়ে গিয়েছে যে দেশের ইতিহাস নিয়ে অনেক কিছুই জানি না বা যতটুকু জানি, তাও খুবই দুর্বল ও খণ্ডিত। এমনকি অনেকে জানতেও চাইছি না।
যেহেতু এখন শিশু সংগঠন নেই, বাবা-মায়েদের হাতে সময় নেই, শিশুরা বই পড়তে অনাগ্রহী, সিনেমার প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে, শিশু-কিশোররা প্রযুক্তি-নির্ভর হয়ে উঠেছে, তাই আমাদের উচিত প্রযুক্তির পথেই শিশু-কিশোরদের হাতে একুশ নিয়ে সঠিক ও আগ্রহ জাগানো তথ্য পৌঁছে দেওয়া।
স্বাধীনতার ৫১ বছর ও ভাষা আন্দোলনের ৭১ বছর পার হলো। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি, মুক্তি সংগ্রাম, উনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থান এমনকি এরশাদ-বিরোধী আন্দোলন নিয়েও ভালো কোনো চলচিত্র হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যাও কয়েকটি হয়েছে, কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে নয়। একুশে ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে কি আমরা একটি আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্র তৈরি করতে পারি না? দিবস উদযাপন করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানান আয়োজন থাকে, থাকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা। কিন্তু ইতিহাস-নির্ভর কোনো নাটক বা চলচ্চিত্র না থাকলে একদিন এসব দিবসের প্রকৃত চিত্র হারিয়ে যাবে, সব অর্জন বৃথা হয়ে যাবে।
সেদিন একটি লেখা পড়ে অনেক নতুন কিছু জানতে পারলাম। এই বিষয়গুলো আমরা অনেকেই জানি না এবং এখন সেইভাবে জানার আগ্রহও নেই। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে প্রথম মত প্রকাশ করেছিলেন একজন ব্রিটিশ লেখক ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড, এ কথা আমরা অনেকেই জানি না।
তিনি ব্রিটিশ কোম্পানি সরকারের পক্ষে বাঙালিদের ইংরেজি শেখাবার জন্য একটি বই প্রকাশ করেন ১৭৭৮ সালে। এটিকে বলা হয় 'হ্যালহেডের ব্যাকরণ'। তখন উপমহাদেশের রাষ্ট্রভাষা ছিল ফার্সি। হ্যালহেড তার ব্যাকরণের ভূমিকায় ফার্সির পরিবর্তে বাংলাকে সরকারি কাজকর্মে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলেছিলেন।
ভাষা আন্দোলনের গল্প শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন নাগরিক ও বুদ্ধিজীবীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের জাতীয় ভাষা হিসেবে উর্দুকে গ্রহণ করার ষড়ষন্ত্রমূলক অপচেষ্টার বিরুদ্ধে লেখালেখি শুরু করেছিলেন।
উপমহাদেশে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রথম প্রস্তাবক ছিলেন নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী। ১৯২১ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রথম লিখিত প্রস্তাব পেশ করেন তিনি। এ প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারকে বলেছিলেন: 'ভারতের রাষ্ট্রভাষা যাই হোক, বাংলার রাষ্ট্রভাষা করতে হবে বাংলা ভাষাকে।'
বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি ওঠে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক সংঘের পক্ষ থেকে। ১৯৪৭ সালে সংঘের পক্ষ থেকে এ দাবি জানান আবুল কালাম শামসুদ্দীন, কাজী জহিরুল হক, বঙ্কিমচন্দ্র সাহা, জ্যোতিদাশ গুপ্ত, আবু জাফর শামসুদ্দীন প্রমুখ। একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে রশিদ বিল্ডিংয়ে প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়েছিল।
একই সময়ে 'তমদ্দুন মজলিস'র পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের কাছে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে প্রথম স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এতে দেশের বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদসহ শতাধিক লোকের সই ছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন: মওলানা আকরাম খাঁ (বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির সভাপতি), মওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী (মেম্বার অব লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি), অধ্যাপক আবুল কাসেম (তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক), অধ্যাপিকা শামসুন্নাহার মাহমুদ, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ (মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান), শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন, অধ্যাপক ড. কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যাপক ড. মোয়াজ্জেম হোসেন, (এসএম হলের প্রভোস্ট), আবুল মনসুর আহমদ (দৈনিক ইত্তেহাদ সম্পাদক), আবু জাফর শামসুদ্দীন, জহুর হোসেন চৌধুরী প্রমুখ। (সূত্র: এম আর মাহবুবের 'একুশের অনালোচিত অজানা কিছু কথা, কিছু ঘটনা')
সেই চলচ্চিত্রে থাকবে একুশকে ঘিরে আরও অনেক জানা-অজানা ইতিহাস। বাংলা ভাষার ওপর প্রথম আঘাত, ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রতিবাদ, ৫২ এর একুশে ফেব্রুয়ারির মিছিলের প্রস্তুতি, ছাত্র আন্দোলন, দেশব্যাপী মিছিল, রফিক, জাব্বার, বরকত, সালামের শহীদ হওয়া, মেয়েদের প্রতিরোধ, ইটের মিনার গড়ার কথা, আজিমপুর কবরস্থানে শহীদদের সমাধিক্ষেত্র, আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো গানের কথা ও সুর নিয়ে তথ্য, রাতের প্রভাতফেরিসহ রাজনৈতিক দল ও নেতাদের অবদান সব ঘটনা ও কাহিনী তুলে ধরতে হবে।
শুধু কোনোভাবে খেটে-খুটে এই ইস্যুগুলো তুলে এনে একটি অসাধারণ সিনেমা যদি নির্মাণ করা যায়, তাহলে সেই সিনেমাই হারিয়ে যাওয়া একুশকে ফিরিয়ে আনবে দেশে ও বিদেশে। বিশ্বের কোনো দেশ ভাষার জন্য আন্দোলন করেনি, প্রাণও দেয়নি, শুধু বাঙালিরা করেছে। কাজেই আমাদেরই দায়িত্ব একুশ নিয়ে একটি বিশ্বমানের সিনেমা বানানো। চিত্রনাট্যটা হয়তো শুরু হতে পারে আসাদগেট নিউকলোনির সেই ছোট শহীদ মিনারটি দিয়েই।
শাহানা হুদা রঞ্জনা, সিনিয়র কোঅর্ডিনেটর, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
(দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে লেখকের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে। প্রকাশিত লেখাটির আইনগত, মতামত বা বিশ্লেষণের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে লেখকের, দ্য ডেইলি স্টার কর্তৃপক্ষের নয়। লেখকের নিজস্ব মতামতের কোনো প্রকার দায়ভার দ্য ডেইলি স্টার নেবে না।)








Comments