আগুন লাগে, নাকি লাগানো হয়?
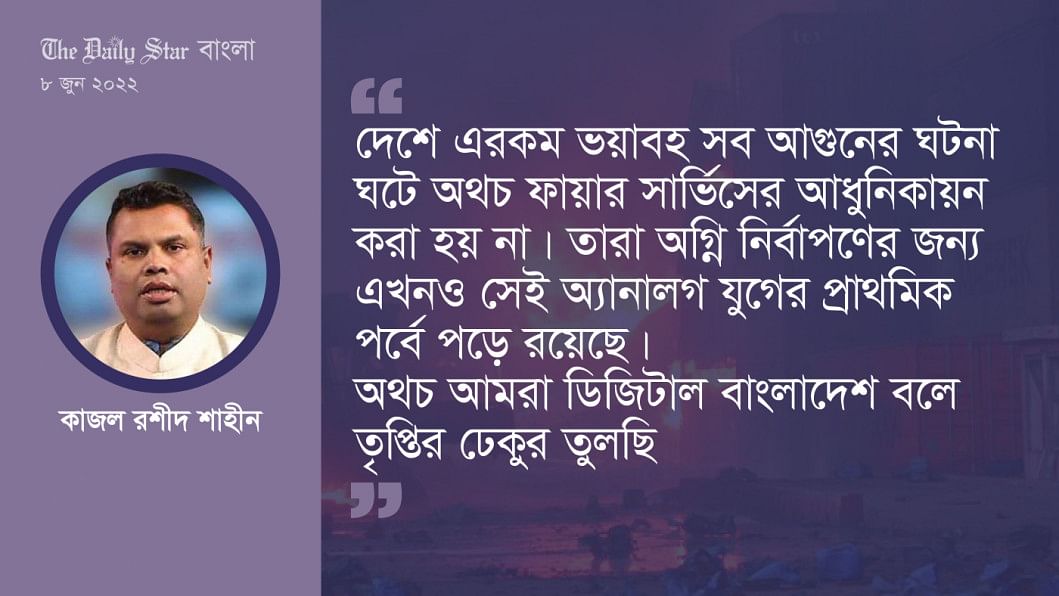
আগুনে পুড়ে মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত, কেননা ঘটনাটা প্রায়ই ঘটছে। বেদনা ও লজ্জার কথা হলো, হৃদয়বিদারক-বেদনাবিধুর ও ভয়াবহ এ বিষয়টাকে আর দশটি স্বাভাবিক ব্যাপার কিংবা প্রকৃতি প্রদত্ত বলে মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, বিশেষ করে রাষ্ট্রের যেসব প্রতিষ্ঠানের এ ব্যাপারে দায় ও জবাবদিহি অবশ্যম্ভাবী।
অথচ দায় স্বীকার ও জবাবদিহির কোনো বালাই নেই। উল্টো চেপে বসেছে অচলায়তনের জগদ্দল পাথর। ফলে, পুরান ঢাকার নিমতলীতেই আগুনে পুড়ে মানুষের মৃত্যুর ঘটনার ইতি ঘটছে না। ছড়িয়ে পড়ছে অন্যত্র। সর্বশেষ যা, সীতাকুণ্ডকে বানিয়েছে ভয়-কান্না ও শোকের এক জনপদে। আগুন লাগার এই সব ঘটনার আগপাশতলা দেখে একটা প্রশ্ন ওঠে জোরালোভাবেই, এসব স্থানে আগুন লাগে, নাকি আগুন যাতে নিশ্চিত লাগে তার আয়োজন করা হয়।
এতো অনিয়ম-অন্যায়-অরাজকতা-অব্যবস্থাপনার সঙ্গে মানিয়ে নিতে মানুষ চিড়েচ্যাপ্টা হয়েও সহ্য করে যায়। কিন্তু কেমিক্যাল, দাহ্য পদার্থ কি চিড়েচ্যাপ্টা হতে জানে? নিশ্চই না। ফলে, নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই সে তার ধর্মমতো বিস্ফোরণ ঘটায়। যাতে শুধু মালের ক্ষতি হয় না, প্রাণেরও বিনাশ হয়। সীতাকুণ্ডেও এরকমই ঘটেছে। ৪৯ জন, মতান্তরে ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুইশর মতো মানুষ পুড়ে চট্টগ্রাম ও ঢাকার হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তাদের কয়েকজন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।
আগুন লাগে নিমতলীতে, চুড়িহাট্টায়, বনানীতে, নারায়ণগঞ্জে। আগুন লাগে সীতাকুণ্ডে। এর বাইরেও আগুন লাগে আরও অনেক অনেক জায়গায়। মারা যায় অনেক-অনেক মানুষ। আহত হয় আরও অনেকে। কিন্তু আগুন বন্ধ হয় না। আগুনে পুড়ে মৃত্যু এবং আগুনে দগ্ধ হওয়া যে কী রকম বিভীষিকা ও যন্ত্রণার ব্যাপার তা কল্পনা করা অসম্ভব।
এই লেখকও আগুনে পুড়তে-পুড়তে বেঁচে গেছেন কোনোরকমে এবং চোখের সামনে মানুষকে পুড়ে মরে যেতে দেখেছেন। পৃথিবীতে এরকম অসহায় মৃত্যু কারোরই যেন না হয়। তারপরও এদেশে আগুনের ঘটনা ঘটে-মানুষের পুড়ে মৃত্যু ও দগ্ধ হওয়ার অচলায়তনই যেন এখানকার বাস্তবতা। এই অচলায়তন ফ্রাংকেনস্টাইনের দানবের মতো বড় হতে হতে অতি দানবীয় শক্তির অধিকারী হয়ে উঠেছে। এ কারণে আমরা যে বলি, 'আগুন লাগে।' কথাটা আসলে ঠিক নয় মোটেই। আগুন লাগে না, আগুন লাগানো হয়। আগুনের কী শক্তি যে সে নিজে নিজেই লেগে যাবে?
আবিস্কারের শুরুতেও আগুন তো নিজে-নিজেই লাগেনি কখনো। ঘষা লেগে কিংবা ঘষা লাগিয়েই জ্বলে উঠেছে আগুন। সুতরাং, সত্যের খাতিরে-বাস্তবতাদৃষ্টে একথা বলাইতো যুক্তিযুক্ত-সুবিবেচনাপ্রসূত ও সঙ্গত যে, নিমতলী থেকে সীতাকুণ্ড সর্বত্র আগুন লাগানো হয়েছে। প্রত্যেকটি জায়গায় আগুন লাগার মতো সকল উপকরণ-উপাদান ছিল। আগুন যাতে লাগতে পারে তার সকল আয়োজন সম্পন্ন করা ছিল। অথচ হওয়ার কথা ছিল উল্টো। একেবারেই বিপরীত কিছু। আগুন যাতে না লাগে, কোনোভাবেই যেন আগুনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা রাখা জরুরি ছিল। কোনো কারণে যদি আগুন লাগেও সেটা কতো দ্রুত নেভানো যায়, কোনোভাবেই যেন মানুষের মৃত্যুর ঘটনা না ঘটে তার জন্য সব প্রস্তুতি সম্পন্ন রাখার বিকল্প ছিল না। কিন্তু না বিদ্যমান অচলায়তন সেসবের কিছুই করেনি। করার দায়বোধও মনে করে না দিনের পর দিন ধরে। যদি দায়বোধ থাকত তাহলে কিছুদিন পরপরই আগুন লাগার ঘটনা এবং আগুনে পুড়ে মৃত্যুর ভয়াবহ বাস্তবতা হতভাগ্য এই দেশবাসীকে দেখতে হতো না।
আগুন যেমন লাগে না, তেমনি পুড়ে মৃত্যু হয় না। পুড়িয়ে মারা হয়। মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়। পুড়ে মৃত্যু বলা মানে তো হলো স্বেচ্ছামৃত্যু। এসব মৃত্যুর কোনোটাই যে স্বেচ্ছামৃত্যু নয়, তা আমরা সকলেই জানি। ফাঁদপাতা অচলায়তনই এই মৃত্যুর জন্য দায়ী। আর দায়ী দায়হীনতার সংস্কৃতি। প্রশাসনিক জবাবদিহির অভাব দায়হীনতার সংস্কৃতিকে বিষবৃক্ষে পরিণত করেছে। যা একের পর এক আগুনের ঘটনা ঘটাচ্ছে আর মানুষের সকরুণ মৃত্যুকে নিশ্চিত করে তোলা হচ্ছে। তাদের ব্যর্থতার ফল হিসেবে আগুন লাগানো হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, যার সর্বশেষ উদাহরণ হলো সীতাকুণ্ডের ঘটনা।
দায়হীনতার সংস্কৃতি ও প্রশাসনিক জবাবদিহির অভাব কীভাবে এবং কেন এই ঘটনার জন্য পুরোপুরি দায়ী, তা বুঝতে আমাদের কয়েকটা বিষয়ে নজর দেওয়া জরুরি।
প্রথমে একটু অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনার দিকে নজর দেওয়া যাক।
১. পুরান ঢাকায় রয়েছে দেড়হাজারেরও বেশি কেমিকেলের গুদাম ও কারখানা। বলা হয়, কেমিকেলের ওপর ভাসছে পুরান ঢাকা। যার নজির হলো নিমতলী ও চুড়িহাট্টা ট্রাজেডি। নিমতলীর ঘটনার পরপরই তদন্ত কমিটির কয়েকটা সুপারিশের মধ্যে অন্যতম ছিল পুরান ঢাকা থেকে কেমিকেলের গুদাম সরিয়ে ফেলা। এ লক্ষ্যে উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু শেষাবধি কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অবস্থা আগের তিমিরেই রয়ে গেছে।
২. নিমতলী ও চুড়িহাট্টার ঘটনায় কে বা কারা দায়ী, তা আজও জানা যায়নি। তাদেরকে বিচারের আওতায়ও আনা হয়নি।
৩. আগুনে পুড়ে মৃত্যুর ঘটনায় কারও সর্বোচ্চ শাস্তি হওয়া তো দূরের কথা, কোনো প্রকার শাস্তি হয়নি, গ্রেপ্তার করা যায়নি, লোকদেখানো গ্রেপ্তার হলেও কিছুদিন পরই জামিনে বেরিয়ে এসেছে।
আগুনে পুড়ে মৃত্যুর ঘটনায় এবং এতবড় অন্যায় ও অপরাধের পরও যদি দণ্ডের নামে এই প্রহসন করা হয়, তাহলে তো আগুনের ঘটনা বাড়াটাই স্বাভাবিক। যেখানে শাস্তি দিয়েও অপরাধ বন্ধ করতে বেগ পেতে হয়, সেখানে আগুনে পুড়ে মৃত্যুর ঘটনায় যদি কোনো শাস্তিই নিশ্চিত করা না যায়, তাহলে আগুনতো লাগবেই, আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটবেই।
সীতাকুণ্ডের ঘটনায় স্পষ্ট হলো কেমিক্যালের বিধ্বংসী ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার পরও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ এ ব্যাপারে কতোটা উদাসীন।
বিস্ফোরক অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ এ সংক্রান্ত অন্যান্য দপ্তরগুলো ভালো করেই জানে যে, ২০১০ সালের ৩ জুন নিমতলীতে ১২৪ জন মারা গিয়েছিল রাসায়নিক দ্রব্যের গুদামে আগুন লেগে। তারপরও তাদের যে প্রাতিষ্ঠানিক দায় কিংবা মানুষের প্রতি যে মমত্ববোধ সেই জায়গা থেকে কোনোপ্রকার দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন বোধ করেনি।
আগুন লাগার পর জানা যায়, ভবনের যথাযথ অনুমোদন নেওয়া হয়নি, নকশা জাল ইত্যাদি-ইত্যাদি। কোনো প্রতিষ্ঠানের যদি জনগণের প্রতি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা থাকে তাহলে কোনোভাবেই ঘটনা ঘটার পর একথা বলতে পারে না। এটা যে, তাদের জন্য লজ্জা ও ব্যর্থতার চূড়ান্ত উদাহরণ সেটাও তারা উপলব্ধি করে বলে মনে হয় না।
সীতাকুণ্ডের কন্টেইনার ডিপোতে আগুন লাগা এবং মানুষের মৃত্যুর পর সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর জানতই না যে, ওখানে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের মতো পদার্থ রয়েছে। তাহলে তাদের কাজটা কী? তাদের রুটিনওয়ার্কের মধ্যে কি পড়ে না এ বিষয়গুলো দেখভাল করা। যদি প্রচলিত বিধি ব্যবস্থায় সেটা না পড়ে, তাহলে সেটা পাল্টানোর চেষ্টা কেন করা হচ্ছে না, বাধাটা কোথায়, নাকি নিজেরাই নিজেদের বাধা?
আগুন লাগার পর দুই ধরনের বক্তব্য বেরিয়ে এসেছে। ফায়ার সার্ভিস বলছে তারা মালিকপক্ষের কাউকে পাচ্ছেন না প্রথম থেকেই, পেলে ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশেই কমানো যেত। অন্যদিকে আমরা গণমাধ্যমে মালিকপক্ষের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি ভালোভাবেই। তাহলে এ ব্যাপারে সমস্যাটা কোথায়?
মালিকপক্ষের একজন ক্ষমতাসীন দলের চট্টগ্রামের প্রভাবশালী নেতা নন শুধু, স্থানীয় একটা পত্রিকার সম্পাদক। যদিও তিনি পেশাদার সাংবাদিক নন। কিন্তু ক্ষমতা ও অর্থ থাকলে এ দেশে কি না হওয়া যায়? এই কি না হওয়া যায়, সংস্কৃতির কারণেই কি প্রশাসন হাত গুটিয়ে রাখে নিজেদের দায় ও দায়িত্ব থেকে?
দেশে এরকম ভয়াবহ সব আগুনের ঘটনা ঘটে অথচ ফায়ার সার্ভিসের আধুনিকায়ন করা হয় না। তারা অগ্নি নির্বাপণের ক্ষেত্রে এখনও সেই অ্যানালগ যুগের প্রাথমিক পর্বে পড়ে রয়েছে। অথচ আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বলে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছি। কবে তাদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে?
প্রশাসনিক জবাবদিহি যতদিন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যাসে পরিণত না হবে, ততদিন সীতাকুণ্ডের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবেই। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা যদি দায়হীনতার সংস্কৃতিতে গা ভাসায় এবং সেটাকেই মূলধারা জ্ঞান করে তাহলে নিমতলী থেকে সীতাকুণ্ডের ঘটনার মতো ঘটনা দেখতে হবে আরও। যেটা বনানী-নারায়ণগঞ্জের পর কন্টেইনার ডিপোতে দেখতে হলো।
এই অব্যবস্থাপনা-এই অচলায়তনই যে, আগুন যাতে লাগে-মানুষের মৃত্যু যাতে ঘটে সেই সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ করে চলেছে, সেই প্রশ্ন জারি রাখতে আমরা যেন ভুলে না যায়।
কাজল রশীদ শাহীন: সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও গবেষক।
(দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে লেখকের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে। প্রকাশিত লেখাটির আইনগত, মতামত বা বিশ্লেষণের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে লেখকের, দ্য ডেইলি স্টার কর্তৃপক্ষের নয়। লেখকের নিজস্ব মতামতের কোনো প্রকার দায়ভার দ্য ডেইলি স্টার নিবে না।)





Comments