আইয়ুব খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শত্রুপক্ষ মনে করতো
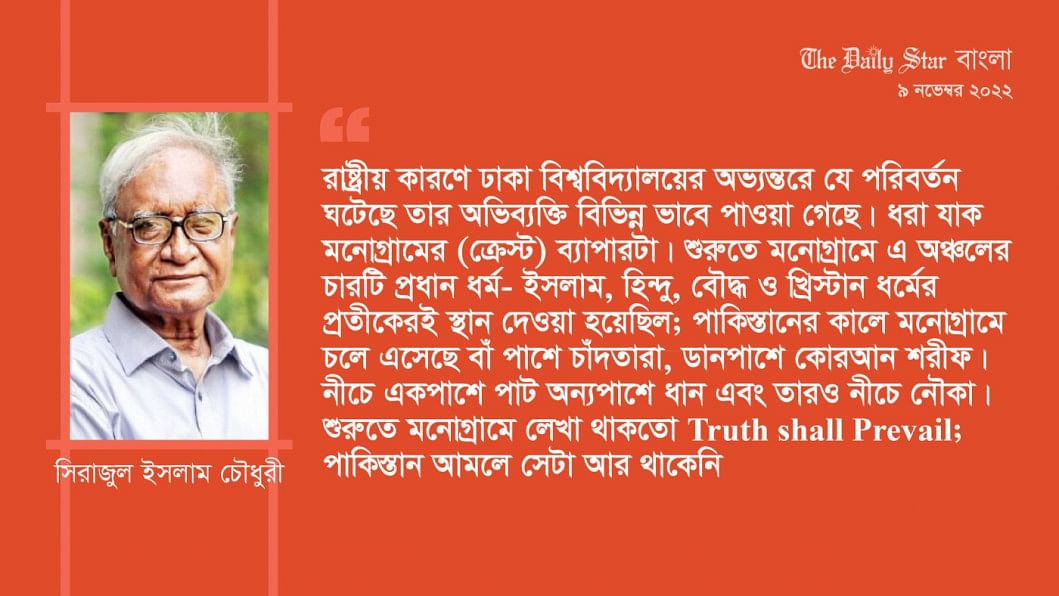
শিক্ষাবিদ, লেখক ও গবেষক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষার্থী ছিলেন তিনি। বহু আগে শ্রেণিকক্ষ থেকে অবসর নিলেও বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র করে তোলার জন্য তার ভাবনা ও কর্মে কখনো ছেদ পড়েনি। একাধিকবার উপাচার্য হওয়ার প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। মনোযোগী হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি প্রকৃত জ্ঞান উৎপাদন ও চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য।
সমাজ-রূপান্তর অধ্যায়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ৭ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাফফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তনে অধ্যাপক আহমদ কবির প্রথম স্মারক বক্তৃতা দেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ: বিচারের দুই নিরিখে'।
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর এই স্মারক বক্তৃতার কথাগুলো ৭ পর্বে প্রকাশিত হচ্ছে দ্য ডেইলি স্টার বাংলায়। আজ প্রকাশিত হলো চতুর্থ পর্ব।
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানগুলোর একটি হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। বাইরে যখন প্রবল সাম্প্রদায়িক হানাহানি চলছে, এবং দেশ এগিয়ে যাচ্ছে ভাগ হওয়ার দিকে, এই বিশ্ববিদ্যালয় তখন কেবল যে সাম্প্রদায়িক হতে অস্বীকার করেছে তাই নয়, হয়ে উঠেছে ধর্মনিরপেক্ষই। ধর্মনিরপেক্ষতার যে দু'টি গুণ- ইহজাগতিকতা ও রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের বিচ্ছিন্নতা- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেই দু'টিকে লালন করেছে। শিক্ষকরা ছিলেন অসাম্প্রদায়িক; আর রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে বাড়িয়ে দেওয়ার আগ্রহ থাকলেও, বিশ্ববিদ্যালয় ওই পথে এগোয়নি।
শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষাদান ও জ্ঞানসৃষ্টির কাজটা তো চলছিলই, আরও যা ঘটছিল তা হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি। প্রথম সমাবর্তনে লর্ড লিটন যে বিশ্ববিদ্যালয়টি ইসলামী শিক্ষা চর্চার কেন্দ্র হবে বলে যে আশা প্রকাশ করেছিলেন সে আশা মোটেই পূরণ হয় নি। তবে ধর্মনিরপেক্ষতার সংস্কৃতি গড়ে ওঠার আসল কারণ হচ্ছে ধর্মপরিচয় নির্বিশেষে শিক্ষক এবং ছাত্রদের ভেতর সম্প্রীতি এবং ইহজাগতিক জ্ঞানের চর্চা। হ্যাঁ, মুসলিম ছাত্ররা ইসলামী বিদ্যা ও আরবী বিভাগেই বেশী সংখ্যায় গেছে বটে, তবে সেটা শুরুতে যতোটা সত্য ছিল পরবর্তীতে ততোটা থাকেনি। নতুন যে 'ঢাকার মানুষ' (Dacca Man) তৈরী হবে বলে লর্ড লিটন আশা করেছিলেন সেই ব্যক্তি যদি গড়ে উঠে থাকে তবে তার পরিচয় মোটেই সাম্প্রদায়িক ছিল না, ছিল ধর্মনিরপেক্ষ।
ঢাকা শহর তখন নানা ধরনের সংক্রামক রোগের জন্য খ্যাতি অর্জন করছিল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও কম ঘটে নি, সহিংসতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরেও আছড়ে পড়েছে বৈকি; তবে সাময়িক বিচ্যুতি সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ গৌরবের দাবী এর মূল ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে তো বটেই এমনকি পূজা দেখতেও মুসলমান ছাত্ররা যেত, ঠিক একইভাবে মুসলিম হলের অনুষ্ঠানেও হিন্দু শিক্ষক ও ছাত্ররা নিমন্ত্রিত হতেন, এবং যোগদান করতেন। রবীন্দ্রনাথ যখন ঢাকায় আসেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল ঠিক সেরকমটাই ঘটেছিল মুসলিম হলে তাঁর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও। নজরুল এসেছিলেন ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের আমন্ত্রণে, কিন্তু তাঁকে আপনজন হিসেবে গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী।
সাতচল্লিশে নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি হলো, বলা হলো এ রাষ্ট্র স্বাধীন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কী স্বাধীনতা পেল? না, পেল না। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আমরা লক্ষ্য করেছি ব্রিটিশ আমলে একের পর এক প্রাদেশিক গভর্নরদেরকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে; একই রকমের ঘটনা কিন্তু ঘটেছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও। ১৯৪৯ সালে খাজা নাজিমুদ্দিনকে ওই সম্মাননা দেওয়া হয়, কারণ তখন তিনি পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী (যদিও তিনি বাঙালীর স্বার্থ দেখতেন না, দেখতেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ)। ১৯৫৬-তে ডক্টরেট দেওয়া হয় ইস্কান্দার মির্জাকে, যিনি তখন গভর্নর জেনারেল, এবং এর আগেই যিনি গভর্নর হয়ে এসেছিলেন যুক্তফ্রন্টের বিজয়কে নাকচ করে দেবার অভিসন্ধির অংশীদার হিসেবে। ইনিও ছিলেন বেশ ভালো রকমের বাঙালী-বিদ্বেষী। ১৯৬০ সালে ডক্টরেট পান জেনারেল আইয়ুব খান, তখন তিনি রাষ্ট্রপ্রধান। আর ঠিক পরের বছরেই তিনি একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে ব্রিটিশ আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে স্বায়ত্তশাসনটুকু দেওয়া হয়েছিল সেটুকু পুরোপুরি হরণ করে নেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল ন্যাথান কমিটি যে বলেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান তার চেয়েও অধিক অন্ধকারে নিয়ে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি আগাপাশতলা সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার। আইয়ুব খানের ওই অর্ডিন্যান্সকে কালা কানুন বলে অভিহিত করা হতো, এবং ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় উত্থাপিত ছাত্রদের ১১ দফার ১ নম্বর দফাতেই ওটিকে বাতিল করার দাবী অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বাতিলের ওই দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তদানীন্তন ইতিহাসের প্রথম বারের মতো রাজপথে মিছিল পর্যন্ত করেছেন; এবং বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে ওই কালা কানুন যে আরও কিছুকাল বলবৎ থাকতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
আইয়ুব খান ও তাঁর সামরিক আমলাতন্ত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শত্রুপক্ষ বলেই মনে করতো; শহর থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে একে রাজনীতিমুক্ত করা যায় কি না সে চিন্তা তাদের ছিল। সামরিক শাসন জারির পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে আসেন বিচারপতি হামুদুর রহমান, তিনি তাঁর প্রথম সমাবর্তন বক্তৃতাতে কথাটা আনুষ্ঠানিক ভাবেই উত্থাপন করেন : We have been driven to the conclusion that perhaps it would be better to shift the university to more congenial circumstances in the outskirts of the city [...] (Dhaka University Convocation Speeches, vol II, op.cit, p 20)
এই বক্তব্যে তিনি রাষ্ট্রীয় চিন্তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। কাজটি সম্পন্ন করতে তাঁরা পারেন নি, কারণ এমনকি সরকার-সমর্থক শিক্ষকরাও এতে সম্মত হন নি, এবং স্থানান্তরকরণের জন্য যে বিপুল অর্থ বরাদ্দ দরকার ছিল সরকার তা দিতে সম্মতও ছিল না। তবে পরে যখন চট্টগ্রামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবশ্যকতা দেখা দিল তখন সেটিকে শহরে না রেখে শহর থেকে অনেক দূরে প্রায়-দুর্গম একটি এলাকাতে স্থাপন করা হয়। ওদিকে আইয়ুব শাসনামলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাত ঘটানো চলছিলই। গভর্নর মোনায়েম খান তো ছাত্রদের একটি বাহিনীই তৈরী করেছিলেন যার সদস্যরা বহুবিধ দুষ্কর্মের উদ্যোক্তা ও নায়ক ছিল। তারা অর্থনীতি বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক আবু মাহমুদকে ক্যাম্পাসের ভেতরেই এমন ভাবে আক্রমণ করেছিল যে তাঁর প্রাণ সংশয় দেখা দিয়েছিল। এর কারণ সরকার-অনুগত উপাচার্যের একটি অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন, শরণাপন্ন হয়েছিলেন হাইকোর্টের, এবং হাইকোর্টের রায় তাঁর পক্ষে গিয়েছিল। স্বৈরশাসনের প্রবলতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামরিক শাসনবিরোধী প্রবল ক্ষোভ গড়ে ওঠে, যার বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৬৪ সালের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে। ছাত্রবিক্ষোভের দরুন সেটি পণ্ড হয়ে যায়। এরপরে শুরু হয় দমনপীড়ন। আইয়ুব শাসনামলে থেকে থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হতো, রাষ্ট্রীয় অসুবিধার কারণে। আইয়ুবের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তার সূত্রপাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই ঘটায়, এবং ঊনসত্তর সালের যে গণঅভ্যুত্থানে ওই শাসনের পতন ঘটে তাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা তো সর্বজনবিদিত।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চরম আঘাতটাও আসে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বেই। আইয়ুবের লোকেরা চেয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থানান্তরিত করবে, আইয়ুবের পরবর্তী সামরিক শাসক, তারই বশংবদ ও সকল তুলনাতেই নিকৃষ্টতর ইয়াহিয়া খানের নিয়োজিত সৈন্যরা ঠিক করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়কে পারলে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, নইলে অন্তত একটি কঙ্কালে পরিণত করে ছাড়বে। ঔপনিবেশিক শাসকেরা যেটিকে স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিল, ছদ্ম-ঔপনিবেশিক শাসকরা তাকে সহ্য করতে পারে নি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রশাসনের কাছে নত হতে সম্মত হয়নি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা তাঁদের নিজেদের ও বাঙালী জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার পক্ষে এবং শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। একাত্তরে যুদ্ধটা প্রকৃত অর্থে ছিল একটি গণহত্যা; এবং এই গণহত্যার শুরু করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। পঁচিশে মার্চের রাত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী- যাকে হাতের কাছে পেয়েছে হানাদারেরা তাকেই নির্বিচারে হত্যা করেছে। আবার যখন সময় এসেছে তাদের আত্মসমর্পণের তখন তারা বেছে বেছে প্রগতিশীল ও মেধাবী শিক্ষকদের কয়েকজনকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। ইয়াহিয়ার শাসনে-উৎফুল্ল জামায়াতে ইসলামী ও তাদের অনুচরদের নিয়ে গঠিত আলবদর বাহিনীর লোকেরা চেয়েছিল গণহত্যার সুযোগকে ব্যবহার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি তথাকথিত ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করতে। লর্ড লিটনের চাইতেও বড় লর্ড ছিল এই পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা।
নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রথম সমাবর্তনে 'জাতির পিতা' কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যে বক্তৃতাটি দেন তাতেই বোঝা গিয়েছিল নতুন শাসকেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কিভাবে দেখতে চান। গভর্নর জেনারেল হিসেবে সেটাই তাঁর প্রথম ও শেষ ঢাকা সফর। রেসকোর্স ময়দানের গণসংবর্ধনাতে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে উর্দু এবং কেবল মাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা। দু'দিন পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে তিনি ওই একই ঘোষণা দ্বিতীয়বার দিলেন। উর্দুর পক্ষে তার যুক্তি ছিল উর্দু ভাষা has been nurtured by a hundred million Muslims এবং এই ভাষা 'embodies the best that is in Islamic culture and Muslim tradition'। (H, p 13)
উর্দু তাঁর নিজের মাতৃভাষা নয়, বস্তুত উর্দু পশ্চিম পাকিস্তানের শতকরা ৫ জনেরও মাতৃভাষা ছিল না; কিন্তু তবু উর্দুকে তিনি যে কেমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন তার কারণটা মোটেই অস্পষ্ট ছিল না। পাকিস্তান ছিল একটি অস্বাভাবিক ও অবাস্তবিক রাষ্ট্র; এর দুই অংশ ছিল শত্রুভাবাপন্ন ভারতের ১২০০ মাইল ভূমির দ্বারা বিচ্ছিন্ন; এবং দুই অংশের ভেতর সাংস্কৃতিক মিল ছিল না বললেই চলে। দুই পাকিস্তানকে তিনি ঐক্যবদ্ধ রাখবেন কি ভাবে? ধর্ম দিয়ে যে কুলাবে না সেটা তিনি জানতেন; আচার-আচরণে, এমনকি বিশ্বাসেও নিজে তিনি ধর্মনিরপেক্ষই ছিলেন; ধর্মকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন রাজনৈতিক কারণে এবং রাজনৈতিকভাবে। ভারতে বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে তিনি রেখে এসেছেন, এবং শরণার্থী হিসেবে যে মুসলমানরা পাকিস্তানে এসেছে, এবং যে অমুসলিমরা পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে যাচ্ছে তাদের দুর্দশা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন এবং মর্মাহত যে হন নি তাও নয়। ধর্ম দিয়ে পাকিস্তানকে এক রাখার অন্তরায়ও ছিল। প্রথমত পাকিস্তানী অমুসলিম মানুষের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না; দ্বিতীয়ত ধর্মাচারের ব্যাপারে এমনকি পাকিস্তানের দুই অংশের মুসলমানদের মধ্যেও বিস্তর পার্থক্য ছিল। তৃতীয়ত পাকিস্তানে ছিল অন্তত পাঁচটি ভাষার মানুষের বসবাস। তিনি তাই মনে করেছিলেন যে একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু করে 'ঐক্য' ধরে রাখতে হবে। কেবল ঐক্য ধরে রাখা নয়, তিনি আশা করছিলেন যে পাকিস্তানে নতুন একটা জাতিই তৈরী হবে, এবং সেই জাতিগঠনের জন্য উর্দুই উপযোগী।
বলা বাহুল্য জিন্নাহর ওই ঘোষণাই পাকিস্তানের জন্য পতনের সূচনাটি সরবরাহ করলো। পাকিস্তানে বাঙালীর সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৬ জন; পাকিস্তান যে এসেছে সেটাও বাঙালী মুসলমানদের ভোটের কারণেই; অথচ রাষ্ট্রেরপ্রধান রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে যে ধারণা দিলেন তার তাৎপর্য হলো এই যে, পাকিস্তানে বাঙালীদেরকে চিরকাল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে বসবাস করতে হবে। রেসকোর্সের ঘোষণার সময়েও মৃদু প্রতিবাদ উঠেছিল, তবে সেটা জনসমুদ্রে হারিয়েই যায়; কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে সীমিত সংখ্যক শ্রোতাদের মধ্য থেকে যে প্রতিবাদটি উঠলো সেটি প্রবল না হলেও অকর্ণগোচর থাকে নি। ছাত্রদের একাংশ ধ্বনি তুলেছিল no no বলে।
উর্দুভাষী উপাচার্য মাহমুদ হাসান জিন্নাহকে কায়েদে আজম তো বটেই আমীর-ই-পাকিস্তান বলে সম্বোধন করেছিলেন, এবং পাকিস্তান যে একটি truly Islamic state হবে এই বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করতে ভোলেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার যে ধর্মনিরপেক্ষ ধারাটি গড়ে তুলেছিল সেটিকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়ে তিনি বললেন শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হবে ইসলামের মূলনীতি। তাঁর ভাষায়:
Basing our educational system on the fundamental principles of Islam will be beneficial to Muslims and non-Muslims alike, and there will be many conmon grounds between the different communities.
কী কারণে সেটা ঘটবে? ঘটবে তা এই কারণে যে, 'The truly Islamic state allows the fullest development of all peoples and communities; for Islam is extensive and espansive like the sun..." (H, p 26)
উপাচার্য মহোদয় ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক; তাঁর ভাষাতে প্রবল ইসলামী উদ্দীপনার সঙ্গে কাব্যিকতার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। জিন্নাহ অবশ্য ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন না, তাঁর লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানকে একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা। সে জন্য শিক্ষার্থীদেরকে তিনি সতর্ক করে দিলেন দেশের অর্থাৎ রাষ্ট্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে। রেসকোর্সের বক্তৃতায় কমিউনিস্টদেরকে শত্রু হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় তিনি পঞ্চম বাহিনীর (ফিফথ কলমিস্ট) তৎপরতার দিকে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনি বললেন ছাত্রদেরকে রাষ্ট্রের 'honest, unselfish servants' হতে হবে।
অলিখিত ওই বক্তৃতার শেষাংশে তিনি বলেছিলেন পাকিস্তান মানুষের জন্য সৌভাগ্যের দরজা খুলে দিয়েছে। দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন করাচীর এক যুবকের। এই যুবক এক সময়ে ২০০ টাকা মাসিক বেতনে কাজ করতো, এখন এক ব্যাংকের ম্যানেজার হতে পারায় তার বেতন হয়েছে ১,৫০০ টাকা। শিক্ষার্থীদের জন্য জিন্নাহ সাহেবের পরামর্শটা ছিল কেবল সরকারী চাকরীর ওপর নির্ভর না করে বাণিজ্য ও শিল্পউদ্যোগের দিকে মনোযোগ দেওয়া চাই।
You will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry and will thus be helping not only yourselves but also your state. (H, p 41)
পরামর্শটা ইসলামী হবার নয়, ছিল পুঁজিবাদী উন্নতির রাস্তা ধরবার। তাঁর এই পরামর্শকে অবশ্য তখন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ওই বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোনো no no ধ্বনি ওঠেনি। জিন্নাহ চাইছিলেন পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র নয় একটি বুর্জোয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হোক। তিনি পুঁজিবাদেই বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ওই পথপ্রদর্শনই পাকিস্তান রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে।
রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের কথাটা ছিল আবরণ মাত্র, ভেতরের আকাকঙ্ক্ষা ছিল ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত মুনাফা লাভের। পাকিস্তান রাষ্ট্র ওই পথেই এগিয়েছে। ওই রাষ্ট্র পূর্ববঙ্গকে একটি উপনিবেশ হিসেবে ধরে রাখতে চাইছিল, ধর্মের আচ্ছাদনটা বিছানো হয়েছিল পুঁজিবাদী উন্নয়নের স্বার্থেই। অথচ সাধারণ মানুষ এবং তখনকার শিক্ষার্থীরাও চাইছিল একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গবাসী যে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মুক্তি চেয়েছে সেই জাতীয়তাবাদ কেবল যে ধর্মনিরপেক্ষ ছিল তাই নয়, ছিল গণতান্ত্রিকও। এবং গণতন্ত্রের মূল কথাটাই হলো নাগরিকদের ভেতর অধিকার ও সুযোগের সাম্য। তবে ইসলামী শিক্ষার কথাটা কিন্তু প্রবল বেগেই বলা হচ্ছিল।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বক্তৃতাগুলো পড়লে দেখা যায় শিক্ষার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রটিকে খারিজ করে দেবার ব্যাপারে পাকিস্তানী রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের উৎসাহের কোনো অভাব ছিল না। এর মূল কারণ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে, এবং জিন্নাহ যেভাবে বুর্জোয়া (অর্থাৎ পুঁজিবাদী) রাষ্ট্রের কথা ভেবেছেন সেই চিন্তাটা শিক্ষাবিদদের মধ্যে সবেগে প্রবাহিত হয়নি। অধ্যাপক মাহমুদ হাসানের পরে উপাচার্য হন বাঙালী অধ্যাপক সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন; সমাবর্তন বক্তৃতায় তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধেই বলেছেন। বক্তৃতায় তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে একটি সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন। সিদ্ধান্তটি ছিল এই যে, রাষ্ট্রের ইসলামী ভাবাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলে ধর্মশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে, তবে 'similar facilities should also be granted to other communities in respect of their religion should they so desire'। (H, p 157)
উল্লেখ্য যে, এই শিক্ষা সম্মেলনেই কিন্তু এই প্রস্তাবও গৃহীত হয় যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।
শিক্ষাক্ষেত্রে উপাচার্যদের কথিত পাকিস্তানপন্থী চিন্তাধারা বেশ শক্তিশালী ছিল, এবং তা যে ঘটেছে বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যের কারণে, সেটাও বোঝা যায়। পাকিস্তানী দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস লেখার চেষ্টা হয়েছে, এবং তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও যুক্ত হয়েছেন। রাষ্ট্রীয় সংহতির জন্য প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত বাদ দেবো, এমন উক্তি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একজনের কাছ থেকেই এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সমর্থক যে ছিলেন না, এমন নয়। তবে উদারনীতিকরাও ছিলেন; তাঁরা মাঝে মধ্যে নিজেদের বক্তব্য দিতে চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। কারণ রাষ্ট্রের কর্তারা ছিল বিপক্ষে।
১৯৫৭ সালে উপাচার্যের দায়িত্বে ছিলেন বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম। তিনি তাঁর সমাবর্তন বক্তৃতায় সুনাগরিক হবার শিক্ষা এবং যথার্থ অর্থে মানবিক হওয়ার শিক্ষার ভেতর একটা পার্থক্যের কথা বলেন। তাঁর মতে নাগরিক হবার শিক্ষা একজন ব্যক্তির পক্ষে পরিপূর্ণ শিক্ষা হতে পারে না। তিনি বলেন, 'The citizen is only a particular type of individual and his horizon of life is circumscribed and limited by his political affiliation and loyalty to the existing order of things or an order imposed by the most powerful political party in the state.'
তার ভাষ্য ছিলো, শিক্ষা যদি এই রকমের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে জ্ঞানের বিকাশ অবশ্যই বাধাগ্রস্ত হবে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন, 'If Christ had been born loyal to the order of his day, perhaps there would have been no Christianity. Similarly if Prophet Mohammed had not rebelled against the existing order there would have been no Islam.' (H, p 205)
এই উক্তিটি ছিল ১৯৫৭ সালের; পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের পরে এবং আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির আগে। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক তখন পূর্ববঙ্গে গভর্নর, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার। ওই সমাবর্তনে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতায় তিনি কিন্তু individual-এর সঙ্গে citizen-এর এই পার্থক্যকে অস্বীকার করেন। শেরে বাংলা বলেন, 'the real, definite and decisive reason why I do not accept the distinction is the all-important fact that this runs counter to the principle of Islam. (H, vol. I, p 131)
পদার্থবিজ্ঞানের ইংরেজ অধ্যাপক ডব্লু এ জেনকিনস্ দুইবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রথমবার ১৯৩১ সালে, অর্থৎ ব্রিটিশ শাসনামলে; দ্বিতীয়বার ১৯৫৪-৫৫-তে, পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ শাসনের পতন এবং পূর্ববঙ্গবাসীর নির্বাচনী রায়কে বানচাল করবার কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টার সময়ে। ১৯৩১ সালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আবহাওয়া বেশ তপ্ত ছিল। গান্ধী কারামুক্ত হয়েছেন, তবে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যাচ্ছেন; অন্যদিকে চট্টগ্রামে যুব বিদ্রোহ ঘটেছে, পাঞ্জাবে বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর ফাঁসি হয়েছে; সেই সময়ে সনদপ্রার্থী গ্রাজুয়েটদেরকে উদ্দেশ্য করে জেনকিনস্ বলছেন, তারা যেন সাহস না হারায়। বলছেন, সাহসী হও, 'Leave cynicism and pessimism to the disillusionment of old age.'। বলছেন, 'One of the tragedies of modern life is the movement inculcating cynicism and unbelief amongst the youth of today,' (H, vol. II, p 143)
১৯৫৫-তে, অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের সময়ে অধ্যাপক জেনকিনস্ তাঁর সমাবর্তন বক্তৃতায় যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন সেটা হলো 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা'। তিনি বলেছেন, 'I have chosen this topic because it is one of those problems of what the finding of the correct solution is fundamental to the future useful development of the Universities and of the country.'। (H, vol. I, p 260)
অধ্যাপক জেনকিনস্ কিন্তু দেশের কথাই বলেছেন, জাতির কথা নয়, দেশ বলতে তিনি হয়তো পূর্ববঙ্গের কথাই ভেবেছেন, জাতির প্রসঙ্গ আনলে 'পাকিস্তান' এসে যেত।
১৯৫৫ সালের ওই সমাবর্তনের চ্যান্সেলার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি আমিরউদ্দিন আহমদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা উপাচার্য-উপস্থাপিত মতের সঙ্গে তিনি মোটেই ঐকমত্য প্রকাশ করেন নি। তাঁর মতে স্বাধীনতা নয়, প্রয়োজন হচ্ছে 'সত্যের অন্বেষণ'। সমাজে অমঙ্গল দেখা দিয়েছে 'প্রতিযোগিতা'র কারণে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন ভয়ঙ্কর একটি সত্য; সেটা হলো,
The manual labourer of yesterday has become the leader of today. The levelling down of class distinction has created new and serious social and moral problems and it is in the right solution of these problems and the proper guidance of various relations that the Universities of today can be of the greatest help and service...' (H, vol. I, p 305)
সন্দেহ করবার তাই কোনো কারণ নেই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল চিন্তা যেমন শক্তিশালী হয়ে উঠছিল, তেমনি প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাও কার্যকর ছিল, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় 'আদর্শবাদিতা' ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণে। জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে যুক্ত হয়ে একাত্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকরা যেমন প্রাণ দিয়েছেন, তেমনি ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী ছাত্রসংঘের সদস্যরাও ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেও ক্ষুদ্র যদিও তবু একাংশ ছিল যারা পাকিস্তানী হানাদারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে লড়াই করেই প্রগতিকে এগুতে হয়েছে; তবে প্রতিক্রিয়ার শক্তি ছিল বেশ বিস্তৃত।
একাত্তরের শেষে এসে দেশ স্বাধীন হলো। ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি অধ্যাদেশ পেল, যেটি তাকে পরিপূর্ণ না হলেও অনেকটা স্বায়ত্তশাসনই দিলো, বলা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কের বিশেষ একটি এলাকা হলো অর্থায়ন, এটি যাতে সরাসরি না ঘটে তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নামে একটি প্রতিষ্ঠানও তৈরী করা হলো। আশা ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্বাধীনতা' ও গণতান্ত্রিকতার অনুশীলন দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের তো বটেই, শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যেও সম্পর্কটা আগের মতো সামন্ততান্ত্রিক না থেকে গণতান্ত্রিক হয়ে উঠবে।
শেষ পর্যন্ত তেমনটা কিন্তু ঘটে নি। বোঝা গেছে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের ঘাটতি ঘটলে বিশ্ববিদ্যালয়ও তার বাইরে থাকতে পারে না। দেখা গেল রাষ্ট্রের শাসকরা চাইছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর প্রভাব, সম্ভব হলে কর্তৃত্বই, বহাল থাকুক; আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেও কিছুসংখ্যক শিক্ষক শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠলেন, কিছুটা মতাদর্শিক কারণে, অনেকটাই বৈষয়িক উন্নতির আশায়। ফলে অন্য পেশাতে যেমন শিক্ষকদের মধ্যেও তেমনি দলীয় বিভাজনের ভেতর দিয়ে এক ধরনের রাজনৈতিক বিভাজন চলে এলো। পরবর্তীতে সেটা বেড়েছে বৈকি, কমে নি। অভিযোগ আছে যে নিয়োগে ও পদোন্নতিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্যের বিবেচনা মেধাগত বিবেচনাকে ছাপিয়ে যায়।
রাষ্ট্রীয় কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার অভিব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে পাওয়া গেছে। ধরা যাক মনোগ্রামের (ক্রেস্ট) ব্যাপারটা। শুরুতে মনোগ্রামে এ অঞ্চলের চারটি প্রধান ধর্ম- ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের প্রতীকেরই স্থান দেওয়া হয়েছিল; পাকিস্তানের কালে মনোগ্রামে চলে এসেছে বাঁ পাশে চাঁদতারা, ডানপাশে কোরআন শরীফ। নীচে একপাশে পাট অন্যপাশে ধান এবং তারও নীচে নৌকা। শুরুতে মনোগ্রামে লেখা থাকতো Truth shall Prevail; পাকিস্তান আমলে সেটা আর থাকেনি। মনোগ্রামের এই পাকিস্তানীকরণটি কিন্তু ঘটেছে ১৯৫২ সালে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যখন প্রবল হয়ে উঠেছে তখন।



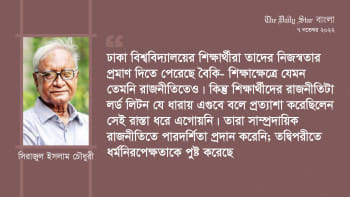
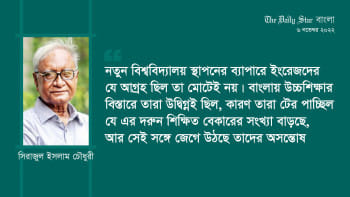







Comments