বাংলা ভাষার প্রথম বিদ্রোহী মধুসূদন
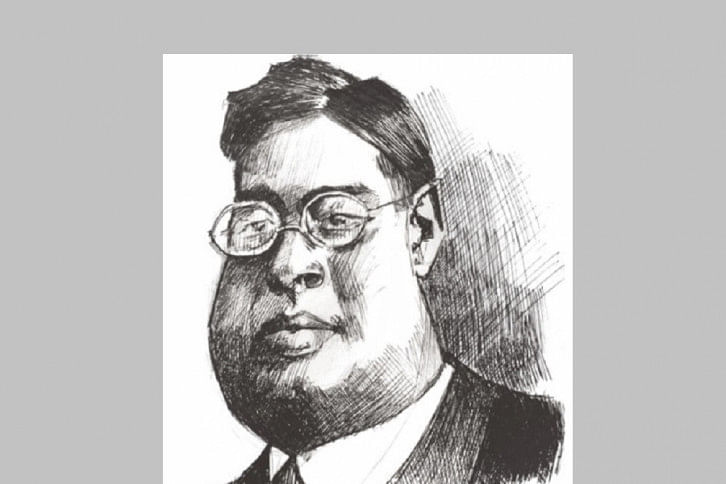
যখন পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ জাতি নানাভাবে সমাজ সময়কে পরিবর্তন করতে তথা ধর্মীয় গোঁড়ামি ভেঙে চেতনার উন্মেষ ঘটাতে মানবিক মূল্যবোধের সমাজ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে (কলকাতায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উত্থান পতন। বলা যায় পুরাতনের বিদায় ও নতুনের আগমন) ঠিক সে সময় আবির্ভাব মধুসূদনের। অতি সাধারণ ঘটনা তবুও এ সময়ে কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু সমাজে জাগরণ শুরু হয়েছিল। অগ্রগামী খ্যাত ইউরোপীয় রেনাসাঁসের সঙ্গে চিন্তার ফারাক থাকলেও ঐতিহাসিকরা নাম দিয়েছেন ‘বঙ্গীয় রেনাসাঁস’। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগরের মতো চিন্তাশীলরা সরাসরি সমাজে নব চেতনার আলোয় কুসংস্কারের ভেড়াকজাল ভেঙে নতুন পথের, নতুন মতের সৃষ্টিতে মগ্ন হলেও মধুসূদন সে পথে পা রাখেননি।
মধুসূদন জন্মেছিলেন শহর থেকে দূরে। অজ পাড়াগাঁয়ে নগরের ব্যস্ততা বর্জিত শান্ত সবুজ তটে। মূল্যবোধ মধ্যযুগের, যুগের ঘুমে কাতর সাগরদাঁড়িতে। কিন্তু বাবার যাতায়াত ছিল কলকাতায়, বয়ে নিয়ে আনতেন নগরীর জানা অজানা খবরের ডালী। এসবে অনুপ্রাণিত হয়ে একান্নবর্তী পরিবারে থেকে সাহিত্যের গতানুগতিক ধারা উপধারার বিরুদ্ধে হাঁটার সংকল্প করেন। বিদ্রোহ করেন সাহিত্যকাশের তারা নক্ষত্র নিয়ে আলাপ আলোচনার। পুরনো আদর্শের বিপরীতে অবস্থান রীতিমত বিস্ময়কর। তার অসামান্যবোধ ও চিন্তাশক্তি এবং সমকালীন পাণ্ডিত্য পাঠ্যভ্যাস অগ্রসর মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল বাংলা ও বাঙালির সাহিত্য সংস্কৃতি মানসে।
আলোচনার পূর্বে মধুসূদনের জীবন পূর্বগুলো প্রচলিত ধারায় আলাদা করে ধারণা দেওয়া যাক। সাগরদাঁড়ি থেকে কলকাতায় নতুন অধ্যায়ের শুরু হয়েছিল। তার আগের জীবনের সাথে নতুন জীবন যোগসূত্র ছিল মা বাবা, পরিবার ও নিজ আত্মদুনিয়া। আর যখনি ধর্মান্তরিত হন, তখনি চিত্র বদলে গেল। একেবারে ভিন্ন পৃথিবী। মাদ্রাজে গিয়ে শুরু করেন নতুন জীবন, আগের চেয়ে পোশাকি ঢংসহ যোগ হয়েছে বেশ কিছু। মাদ্রাজে যখন কলকাতায় ফিরেন, তখন সেখানের সকল সম্পর্ক ভুলে, চলেছেন নতুন খেলায়। বলা যায় জাহাজ থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় পঞ্চম জীবনে ঢুকে পড়েন। কলকাতা ছেড়ে ব্যারিস্টারি পড়তে যখন বিলেতে যাত্রা করেন—সে জীবনের স্বাদ রঙ গন্ধ পেয়েছিলেন দেখা দুনিয়া থেকে আলাদা। তৃতীয়বারের মতো যখন কলকাতায় ফিরেন আগের জীবনের সঙ্গে সামান্য মিল থাকলেও মধুসূদন- মাইকেল হয়ে পাল্টে দিলেন চেনা জগত। এইভাবে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন কাটিয়েছেন বলে জীবনীকারদের ভাষ্য।
খ.
ভালো ছাত্র ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মায়ের কাছ থেকে রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী শুনে পুরাণ প্রীতি অর্জন। পিতার সংস্পর্শে কাব্যের অনুপ্রেরণা। গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষক হরলাল রায়ের কাছে বাংলা ও অংক, পাশের গ্রামের মৌলভি খন্দকার মখমল আহমদের কাছে শিখছেন ফারসি। এসবে মধুসূদনের মানস গঠনে ভূমিকা রাখে।
এছাড়াও ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে একটা মানসিক ক্ষমতাও ছিল তার। ফলে কলকাতায় স্কুলে যাবার পর ইংরেজি জানা সহপাঠীদের সহজে ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু প্রথম দিকে পরিবেশগত দিক থেকে খাপ-খাওয়াতে পারেন নাই বলে বেশ পীড়া দিয়েছে। যশোরের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলা, আচরণে গ্রাম্যতা কাটিয়ে উঠতে সময় লেগেছিল।
জীবনীকার গোলাম মুরশিদ বলেন, এ সময় যদি ইংরেজ কবি শেলির মতো পাঠশালায় সবার অজ্ঞাতে চোখ মুছে থাকেন, লেখার খাতায় ফেলে আসা গ্রামের ছবি এঁকে থাকেন, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অন্যদিকে শৈশবের স্মৃতি ও চিরায়ত বাংলার নৈসর্গ মধুসূদনের জীবনে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে। দীর্ঘস্থায়ী রেখাপাত করেছে কাল থেকে কালান্তরের ভেলায়। সেটার প্রমাণ মিলে তার বিভিন্ন রচনায়। যখন ‘দ্য ক্যাপটিভ লেডি’ যখন মাদ্রাসে প্রকাশ করেন, তখন সে জন্মভূমি থেকে অনেক দূরে। তা সত্ত্বেও রচনায় ছায়া ফেলেছে শৈশবের নিসর্গ দৃশ্যপট। ভার্সাইতে সনেটগুচ্ছের উপরেও সাগরদাঁড়ির স্মৃতি জীবন্ত হয়ে উঠছে।
নানা আচরণে প্রচলিত রীতির বিরোধিতা করেছেন। পরিবার থেকে এর প্রশ্রয় পেয়েছেন বলে ধারণা করা যায়। তার বন্ধু গৌরদাসের স্মৃতি থেকে বলা যাক। বেশ ভাব হবার পর বাড়িতে আসা যাওয়া করতেন। একদিন আরেক বন্ধুসহ মধুসূদনের বাড়িতে যেতে সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে যান। দেখেন রাজনারায়ণ দত্ত (মধুসূদনের বাবা) আলবোলা টানছেন। তার টানা শেষ হবার পর নলটা এগিয়ে দিলেন মধুর দিকে। তার মধুও তৃপ্তির সঙ্গে তামাকের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। ১৮৪০ সালে এমন দৃশ্য কল্পনাও করা যায় না। পরে গৌরদাস বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে মধু উত্তর দেন, তার পিতা অন্যদের মতো এসব তুচ্ছ আচার-অনুষ্ঠানের ধার ধারেন না।
এইভাবে গতানুগতিক পথের বাইরে চলছেন। চলার উৎসাহ পেয়ে বোধের দেয়াল টপকে আলো ফেলেছেন। এ আলো ছড়িয়ে গেছে কাল থেকে কালান্তর। যেমন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্মৃতিচারণ জানা যায়, ১৮৫৯ সালে শর্মিষ্ঠা অভিনয়ের মহড়া চলছিল। এর মাঝে আলাপের এক পর্যায়ে কবি বলেন, যত দিন না বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচলিত হচ্ছে, ততদিন বাংলা নাটকের উন্নতি আশা করা যায় না। তার উত্তরে যতীন্দ্রমোহন বলেন যে, বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ বোধ হয় রচনা সম্ভব না। উত্তরে কবি বলেন, তেমন চেষ্টা করলে বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ লেখাও সম্ভব। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। একসময় ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন বলে প্যারোডি করেন। এক পর্যায়ে মধুসূদন চটে গিয়ে বলেন, ‘বুড়ো ঈশ্বরগুপ্ত পারেননি বলে, আর কেউ বাংলায় অমিত্রাক্ষর লিখতে পারবে না, এটা আমি বিশ্বাস করি না। তর্কের শেষে কবি জানিয়ে দেন আমি ভুল এই ভাঙিয়ে দেবো। প্রমাণ করে দেবো বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর লেখার যথেষ্ট উপকরণ আছে। কয়েকদিন পরেই লিখে তাদের দেখান। জানান দেন অজানা অধ্যায়!
সামালোচক বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, ‘মাইকেলের যতি স্থাপনের বৈচিত্র্যই বাংলা-ছন্দের ভূত-ঝাড়ানো জাদুমন্ত্র। কী অসহ্য ছিল ‘পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল’ একঘেয়েমি, আর তার পাশে কী আশ্চর্য মাইকেলের যথেচ্ছ-যতির উর্মিলতা। যতিপাতের এ বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গেই যে ছন্দের প্রবহমানতা এসে অন্তহীন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিল।’
ছন্দমুক্তি সম্পর্কে তার দৃঢ়তা ও প্রত্যয় ধরা পড়ে ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে’র উৎসর্গপত্র মঙ্গলাচরণে। নতুন এ ছন্দ ব্যবহারের কৈফিয়ৎ হিসেবে তিনি লেখেন ‘আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হতেছে যে, এমন কোনো সময় অবশ্যই উপস্থিত হবে, যখন এ দেশের সর্বসাধারণ জনগণ, ভগবতী বাগদেবীর চরণ হতে, মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখে চরিতার্থ হবেন।’
গ.
ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ১৮৬২ সালে ইংল্যান্ড এসেছিলেন। পরিবার ছিল কলকাতায়, ‘গ্রেজ ইন’-এ যোগ দিয়েছিলেন। এক বছরও পূর্ণ হয়নি, ১৮৬৩ সালে স্ত্রী সন্তানসহ ইংল্যান্ড চলে আসেন। কারণ, যাদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে ইংল্যান্ডের পড়া ও পারিবারিক খরচ দেওয়ার ব্যবস্থা করে এসেছিলেন, তারা সবাই কবিকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। কোনোরকম ভাড়াটা জোগাড় করে সন্তানসহ হেনরিয়েটা ইউরোপ পৌঁছান। অর্থাভাবে চরম বিপদে পড়লেন। পরে বহু চিঠিপত্র বন্ধুবান্ধবকে লিখেও কোনো সাড়া পাননি। ইংল্যান্ডে চেয়ে ফ্রান্সের ভার্সাইয়ে বসবাসে অর্থ খরচ কম পড়বে ধারণায় ১৮৬৩ সালের মধ্যভাগে সপরিবারে ভার্সাই চলে আসেন ।
তবে ভার্সাই শহরের কেটেছে চরম দুঃখের দিনগুলো। অচেনা পরিবেশে কোনো চাকরি জোগাড় করতে পারেননি। সামান্য টাকাপয়সা তখনো হাতে যা ছিল, তা দিয়ে যাতে সবচেয়ে বেশি সময় টিকে থাকা যায়, তার জন্য তিনি অথবা হেনরিয়েটা চেষ্টার কোনো কসুর করেননি। জীবিকা নির্বাহের জন্য স্ত্রীর অলংকার, গৃহসজ্জার উপকরণ ও পুস্তকাদি বন্ধক বা বিক্রি করে চলতে হয়েছিল। এ সময় আশপাশের মানুষের কাছে প্রচুর ঋণও জমে গিয়েছিল।
ঋণের দায়ে একবার জেলে পর্যন্ত যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এ সময় তার গুণগ্রাহী এক ফরাসিনী জেলে যাওয়ার হাত থেকে তাকে বাঁচান। চাতক পাখির মতো প্রতিদিন ডাকের অপেক্ষা করতেন কলকাতা থেকে কখন তার প্রাপ্য টাকা এসে পৌঁছাবে। অথবা দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর কখন তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে অর্থ পাঠাবেন, তার অপেক্ষায় থাকতেন বুকভরা আশা নিয়ে।
অন্যদিকে বাংলাকে উপেক্ষা করে ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চার যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন, তা যে পরবর্তীকালে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে সে কথা সবাই জানেন। স্বপ্নের দেশ ইংল্যান্ডের কাছাকাছি পৌঁছে যাবার অনুভূতির কথা জানতে পারি বন্ধু গৌরদাসকে লেখা চিঠি থেকে। ‘হে আমার প্রিয় ও পুরনো বন্ধু। আমি সীলোন নামক একটা জাহাজে চলেছি। এখন তোমাকে কয়েক ছত্র লিখব বুঝলে বৎস!...
এ মুহূর্তে আমি ভেসে যাচ্ছি বিখ্যাত সেই ভূমধ্যসাগরের মাঝ দিয়ে, এখান থেকে উত্তর আফ্রিকার পর্বতাকীর্ণ উপকূল দেখা যায়। গতকাল ছিলাম মলটায়, গত রোববারে আলেকজান্দ্রিয়ায়। আর মাত্র কয়েকদিনের ভেতরেই ইংল্যান্ডে পৌঁছে যাব আশা করি। আজ থেকে বাইশ দিন আগে আমি কলকাতায় ছিলাম। বেশ দ্রুতগতিতেই আমরা চলেছি কী বল? কিন্তু এ ভ্রমণের একটা দুঃখজনক বিষয়ও রয়েছে। সব জানতে পারবে, ধৈর্য ধারণ কর ধৈর্য, বন্ধু।’
মাদ্রাজে যখন ছিল, তখন সাদা-কালো, ইউরোপীয়-নেটিভদের যে বৈষম্য তার শিকার হন মধুসূদন। ধর্মীয় খোলসের আবরণে বিশপস কলেজেও দেখেছেন বর্ণবাদী দৃশ্য, প্রতিবাদ করেছেন চির বিদ্রোহী কবি। কখনো কখনো বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। ধর্ম পরিবর্তন করার পর তিনি নিজেই বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেও ধর্মযাজকদের সকল কাজ সমর্থন করেননি। তিনি দেখেছেন গরিব অসহায়, অশিক্ষিত, নিম্নবর্গের মানুষদের ধর্মান্তরিত করে চলছেন। কেবল তাই নয়- মাদ্রাসে হিন্দুদের অবজ্ঞাভরে ‘হিদেন’ বলে তাচ্ছিল্য করত।
সংবাদপত্র সম্পর্কে সে সময়ে সমাজের ধারণা, কর্মকাণ্ড জানিয়েছেন। বিস্ময়ের সঙ্গে তার কথা উল্লেখ করেন। ‘সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতি কতখানি উচ্চকণ্ঠ, কতখানি স্পষ্টবাদী। শাসকগোষ্ঠীকে স্বৈরাচার বলতেও দ্বিধা করেননি। সরকারকে আহ্বান করেছেন অস্ত্রের ক্ষমতা নয়, তিনি জ্ঞানের ক্ষমতা, শক্তি বা বলকে হরণ না করার জন্য শাসকশ্রেণীর প্রতি আহ্বান করেন। সেই সাথে যারা তাঁবেদারি করে তাদের প্রতিও বিরক্ত হয়েছেন।’ (খসরু পারভেজ : মধুসূদন বিচিত্র অনুসঙ্গ)
বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমানের তীর্থভূমি ভারতের উদার সম্পাদক মধুসূদন লিখেছেন মুসলমান নিয়েও। হিন্দু জাগরণের যুগে এমন স্পর্ধা ভাবা যায় না। তিনি রিজিয়া, লিখে মুসলমানদের বীরত্বেও কথা বলেছেন তার কিছুদিন আগেও। স্মরণ করিয়ে দেন কারবালার করুণ কাহিনী নিয়ে মহাকাব্য রচনার। নাটক লিখতে চেয়েছেন মুসলমান নিয়ে। মধুসূদন অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে হিন্দু ক্রনিকালে লিখেন, ভারতে মুসলমান শাসনামলে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। যে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে তা ভারতেই রক্ষিত আছে. পাচার হয়নি। তিনি সমালোচনা করলেন তাঁদের রামমোহন রায়, দ্বারকানাথের মত মহারথীদের, যারা ভারতবন্ধু বলে দাবি করেন, তাঁরাই ব্রিটিশ শাসনের গুণগান গেয়ে মধ্যযুগে ভারতের গলায় পরাধীনতা, ধর্মান্ধতা, স্বৈরাচারের কণ্টমালা পরিয়ে দিয়েছেন। Mussalmans in India নিবন্ধে মুসলমান শাসনামলের সমালোচনার পাশাপাশি লীডেন হলের শাসন ভারতের দুরবস্থার কথা বললেন। স্যার চার্লস যে সত্যকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছেন, সেটিও উন্মোচন করলেন।
মধুসূদনের মাদ্রাজে প্রথম কিছু সময় জীবিকার তাগাদে নষ্ট হলেও, পরে আর তা হতে দেননি। পাঠচর্চা রীতিমত বিস্ময়কর। ১৮৪৯ সালে ১৮ আগস্ট বন্ধু গৌরদাসকে জানান, হয়তো তুমি জানো না যে, প্রত্যহ আমি কয়েক ঘণ্টা তামিল চর্চায় কাটাই। একজন স্কুল ছাত্রের চেয়ে আমার জীবন অনেক ব্যস্ততায় কাটে। আমার রুটিন ৬টা থেকে ৮টা হিব্রু, ৮টা থেকে ১২টা স্কুল, ১২টা থেকে ২টা গ্রিক, ২টা থেকে ৫টা তেলেগু ও সংস্কৃত, ৫টা থেকে ৭টা ল্যাটিন, ৭টা থেকে ১০টা ইংরেজি। আমি কি আমার মাতৃভাষাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছি নে।
‘ভারতের গণ্ডি পেরিয়ে সারা পৃথিবীর শিল্পভুবনে নিজেকে হাজির করা এবং খ্যাতি অর্জনের নেশা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল নাট্যকার কবি মধুসূদন দত্তকে। তিনি গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু, সংস্কৃত, তেলেগু, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয় ভাষাও শিখেছিলেন এবং পাশ্চাত্য চিরায়ত সাহিত্য অধ্যয়ন করেছিলেন। মধুসূদনের যখন জন্ম, তখন ভারতে সরকারি কাজকর্মের ভাষা ছিল ফারসি। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আদালত এবং সরকারি কাজকর্মের ভাষা হিসেবে চালু হয় ইংরেজি। তখন স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজি শেখার চাহিদা বাড়তে লাগল! এই সহজ সত্যটি, মধুসূদনের সাহিত্যপাঠের সময়, আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন।’ বাংলা সাহিত্যের যুগ প্রবর্তক এই কবির শেষ জীবন চরম দুঃখ ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ছিল। ঋণের দায়, অর্থাভাব, চিকিৎসাহীনতা ইত্যাদি কারণে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। (মাতৃভাষা ও মধুসূদন : ফজলুল হক সৈকত)
তবে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি এমনিভাবে লিখতে ও পড়তে পারতেন। পরধন লোভে মত্ত মাদ্রাসে বসে স্বদেশের ছবি এঁকেছেন। কেবল সাহিত্যরুচি নয়, সামগ্রিক চিন্তায় রুচিবোধ ছিল অসামান্য। ভাষার জন্য, মাতৃভাষার প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উন্নয়নের বিষয় ভেবেছেন। বলা যায় বিশ্বের কাছে বাংলা ভাষাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার অবদান অসামান্য। উজ্জ্বল অগ্রদূতের ভূমিকা রেখেন মধুসূদন। কী মেঘনাদবধ কাব্যে কী বৈপরীত্য বৈচিত্র্য রচনায়। সব জায়গায় বিদ্রোহের, নিজস্বতায় মায়া কানন!
তথ্যসূত্র ও উদ্ধৃতি কৃতজ্ঞতা :
১.মাইকেল মধুসূদন দত্ত : জীবন ও সাহিত্য। সুরেশচন্দ্র মৈত্র
২. আশার ছলনে ভুলি : গোলাম মুরশিদ
৩. মধুসূদন বিচিত্র অনুষঙ্গ : খসরু পারভেজ
৪. পার্থ প্রতিম মজুমদার, ড.ফজলুল হক সৈকত ও বীরেন মুখার্জীর প্রকাশিত প্রবন্ধ।
ইমরান মাহফুজ : কবি গবেষক





Comments