একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির সন্ধানে
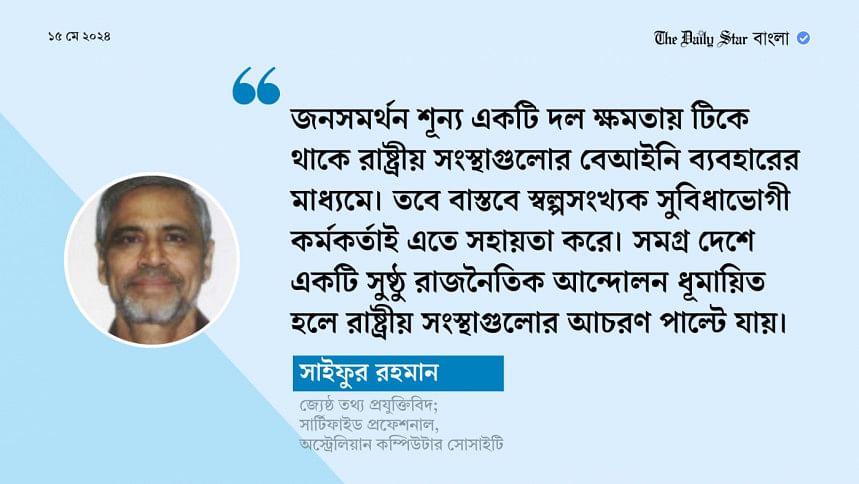
একটি দেশের সফলতার প্রধান মাপকাঠি হলো 'সে দেশের মানুষ কতটা ভালো আছে'। এর একটি পরিমাপক জাতিসংঘের 'ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইনডেক্স ২০২৪' অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান পাকিস্তানেরও নিচে।
মানুষ হিসেবে আমরা কতটা স্বাধীন তার একটি সূচক আটলান্টিক কাউন্সিলের 'ফ্রিডম অ্যান্ড প্রসপারিটি ইনডেক্স'। ২০২৪ সালের রিপোর্টে দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের অবস্থান আফগানিস্তান ছাড়া বাকি সব দেশের নিচে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা তুলনামূলক ভালো, যদিও স্ট্যাটাস এখনো 'বেশির ভাগই অসচ্ছল' অবস্থায় রয়ে গেছে।
বিগত কয়েক দশকে স্বাধীনতার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমান্বয়ে নিচে নেমেছে, কিন্তু আর্থিক সচ্ছলতায় এগিয়েছে। এই বৈপরীত্য অনেককে অবাক করলেও এর অন্তর্নিহিত কারণটি সহজ। দেশে সুশাসন নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সংস্থার এবং তারা এ কাজে ব্যর্থ হয়েছে। অর্থনৈতিক সচ্ছলতার পিছনে রয়েছেন রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ এবং তারা সফল হয়েছেন।
প্রবাসীরা নিয়মিত-অনিয়মিত উপায়ে দেশে ৪৫ বিলিয়ন ডলার পাঠান। টাকার মাল্টিপ্লায়ার অ্যাফেক্টে তা ১৩৫ বিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রূপান্তরিত হয়, যা জিডিপির প্রায় ৩০ শতাংশ। এ অর্থই গ্রামাঞ্চলে আধুনিক কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, ব্যবসা ও সেবাখাতের প্রয়োজনীয় পুঁজির যোগান দিয়ে সচ্ছলতা এনেছে। গার্মেন্টস শ্রমিক, রেমিট্যান্স প্রেরণকারী এবং কৃষকের হাড়ভাঙা পরিশ্রমই বাংলাদেশের আর্থিক উন্নয়নের মূল কারণ। তা না হলে আমরা এখনো 'তলাবিহীন ঝুড়ি'ই থেকে যেতাম।
ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড, উর্বর মাটি, মিষ্টি পানি, পর্যাপ্ত সূর্যলোক ও বিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকূলের মতো অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর বাংলাদেশ। ভাষা ও সংস্কৃতিতে প্রায় বৈষম্যহীন একটি জাতি। কেবলমাত্র সুশাসন নিশ্চিত করা গেলেই দেশটি হতে পারত পৃথিবীর অন্যতম সুখী, মুক্ত ও সমৃদ্ধশীল একটি রাষ্ট্র। কিন্তু সর্বস্তরের দুর্নীতি এবং সুশাসন ও ব্যবসাবান্ধবতার অভাব এতটাই প্রকট যে একজন সাধারণ মানুষও মনে করেন, রাষ্ট্র উন্নয়নের সহায়ক নয়, বরং বাধা।
রাষ্ট্র যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে তার জন্য মূলত দায়ী সমাজের নেতৃত্ব—রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, আমলা, পেশাজীবী, গণমাধ্যম ও ব্যবসায়ী শ্রেণি। সাধারণ মানুষ সহজ ও সরল প্রকৃতির। তাই দেশের দুরবস্থার জন্য তারা মোটেও দায়ী নয়—এমন একটি ধারণা সমাজে রয়েছে। তবে একটি কথা প্রচলিত আছে, যার মর্মার্থ হলো, 'যে দেশের জনগণ যেমন, রাষ্ট্র ঠিক তেমনই হয়ে থাকে।' দেশের সম্পদ লুটের জন্য একজন দুর্বৃত্ত নেতা যেমন দায়ী, অজ্ঞতাবশত অথবা সামান্য টাকার লোভে ওই মানুষটিকে যে ভোট দিয়েছে সেও দায়ী।
রাজনৈতিক দার্শনিক হান্না আরেন্ডটের মতে রাজনীতির অন্যতম প্রধান কাজ মানুষকে সক্রিয় নাগরিকে রূপান্তর করা। তাদের রাজনীতি সচেতন এবং নাগরিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করা। একজন দুর্বৃত্তও যখন সমাজ সচেতন হয়ে উঠে, তখন সে বুঝতে পারে যে ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে সমাজের স্বার্থ রক্ষাই দীর্ঘ মেয়াদে তার ও তার সন্তানদের অধিক লাভবান করবে। তখন সে-ও সমাজের পক্ষে কাজ করে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূল দায়িত্বই হলো জনগণের মাঝে সেরকম চিন্তার বিকাশ ঘটানো।
ঔপনিবেশিক ভারতে জমিদার নামক একটি দালাল শ্রেণি ও প্রভুসুলভ আমলাতন্ত্র তৈরি করা হয়েছিল দেশের সম্পদ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে। ১৮৬১ সালে ভারতীয় কংগ্রেসের গোড়াপত্তন হয়, যার পুরোধায় ছিল জমিদার, ব্যবসায়িক ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণি। শোষণমূলক রাষ্ট্রীয় কাঠামো, আইন ও প্রশাসন যন্ত্র যেহেতু ওই শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য ছিল অত্যন্ত উপযোগী, তাই তারা স্বাধীনতার পরও এর পরিবর্তন করেনি।
পাকিস্তান এবং পরবর্তী সময় বাংলাদেশের সামরিক ও বেসামরিক প্রতিটি সরকার একই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে। দক্ষিণ এশিয়ার পশ্চাৎপদতার এটিই প্রধান কারণ।
অসাধু ব্যবসায়ী, ভণ্ড রাজনীতিবিদ ও দুর্নীতিগ্রস্থ আমলার যে নেক্সাস আজ জনগণের ওপর দৈত্যের মতো চেপে বসেছে, রাষ্ট্রীয় সংস্কার ছাড়া এর থেকে মুক্তি নেই। গতানুগতিক ধারার রাজনৈতিক দলগুলো সংস্কারের আশ্বাস দেয়, কিন্তু দুটি কারণে তারা শক্তিহীন।
১. নেক্সাস এতটাই ক্ষমতাবান যে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া গণবিচ্ছিন্ন কোনো দলের পক্ষেই ক্ষমতায় আরোহণ ও টিকে থাকা সম্ভব নয়।
২. রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের পরিবর্তনে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আইনশৃঙ্খলার সাময়িক অবনতির যে ঝুঁকি, তা সরকারের পক্ষে বহন করা অত্যন্ত কঠিন।
সত্যিকারের মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে জনগণের ক্ষমতায়ন। আর এটা হতে হবে এমন এক রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে, যারা জনগণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত; যে দলে এলিট বা পরিবারতন্ত্র নেই, গণতান্ত্রিক উপায়ে যোগ্যতা ও সেবার ভিত্তিতে দলের প্রতিটি স্তরে নেতা নির্বাচিত হয়; দলে নীতিগত দিক নির্দেশনা ছাড়া অন্য সব বিষয় কেন্দ্র থেকে সরিয়ে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের শাখায় ন্যস্ত; সদস্য গ্রহণ, প্রশিক্ষণ, নেতা নির্বাচন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও স্থানীয় ইস্যুর ভিত্তিতে আন্দোলন সংগঠিত করার ব্যাপারে দলের তৃণমূলের শাখাগুলো স্বাধীন।
সক্রিয় নাগরিক তৈরি জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগে হতে পারে। যেমন—
১. তৃণমূলে সামাজিক ও রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যাপক কর্মসূচি
২. সর্বস্তরে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি
৩. স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতি, সুশাসন ও অন্যান্য ইস্যুতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা ইত্যাদি।
স্বল্প সময়ে ক্ষমতায় আরোহণের কোনো কৌশল এটি নয়। দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন মুক্তির আরেকটি সংগ্রাম, যার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও প্রয়োগযোগ্য কর্মসূচি। ভৌগলিক স্বাধীনতার প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন হয়েছিল ১৮ বছরের (১৯৫২-১৯৭০) রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধরন হলো 'পেট্রোন-ক্লাইন্ট' সম্পর্ক। যেখানে অন্ধভাবে দলনেতাকে অনুসরণ করা হয়। যোগ্য নেতৃত্ব বিকাশের জন্য চিরচারিত এ নিয়মের পরিবর্তন ঘটিয়ে সার্ভেন্ট-লিডারশিপ মডেল প্রয়োগ হতে পারে। কেবলমাত্র যোগ্যতা ও সেবার ভিত্তিতেই প্রত্যেক স্তরে নেতা নির্বাচিত হতে হবে।
সাংগঠনিক বিশেষজ্ঞ রোবার্ট গ্রিনলিফ ১৯৭০ সালে এই মডেলের স্বপক্ষে সুপারিশ করেছন। তারও বহু পূর্বে শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক বলেছিলেন, 'তিনিই নেতা হওয়ার যোগ্য, যিনি সর্বোৎকৃষ্ট সেবা প্রদান করেন।'
জনগণকে শিক্ষিত ও সচেতন করার একটি প্রধান উপায় হলো সামাজিক আন্দোলন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যার পল কলিয়ার বলেছেন, মানুষ সাধারণত নিজস্ব স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত। সে তখনই একটি সামাজিক প্রতিবাদে অংশ নেয়, যখন মনে করে এতে ঝুঁকির চেয়ে লাভের সম্ভাবনা বেশি।
আরেকটি শ্রেণি হলো যারা দুঃশাসনের কারণে নির্যাতিত, তাই এর প্রতিকার চান। অনেকেই খাঁটি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েও আন্দোলনে যোগ দেন। আন্দোলনের সংগঠকদের এসব বিষয় বিবেচনা করতে হবে। প্রতিবাদের বিষয়বস্তু এমন হওয়া উচিত, যাতে এলাকার মানুষ উপদলীয় বিভেদের ঊর্ধ্বে একটি 'সাধারণ কারণ' খুঁজে পায়।
রাজনীতি এক প্রকার রক্তপাতহীন যুদ্ধ। সমরবিদ্যার নির্দেশিকা 'আর্ট অব ওয়ার' এ বর্ণিত যুদ্ধজয়ের কৌশলের একটি হলো—লক্ষ্যবস্তু এমন হতে হবে, যেখানে শত্রুর বাধার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। সাফল্যের জন্য প্রাথমিক পর্যায় রাজনৈতিক আন্দোলন সীমিত রাখা উচিত স্থানীয় পর্যায়ের এমন বিষয়বস্তুতে, যা রাষ্ট্রের মূল প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ করবে না এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের দ্রুত লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
ক্ষুদ্র পরিসরের স্থানীয় প্রতিবাদ ক্রমান্বয়ে দেশের বৃহৎ সমস্যা নিয়ে অন্যান্য অঞ্চল ও কেন্দ্রীয় স্থানে ছড়িয়ে পড়তে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন নেই—বিশেষত বর্তমানের তথ্য-প্রযুক্তির যুগে।
কৌশলগত কারণে প্রাথমিক পর্যায় আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। উদাহরণস্বরূপ উপজেলা পরিষদের একজন চিকিৎসক সরকারি হাসপাতালে সময় না দিয়ে প্রাইভেট ক্লিনিক পরিচালনা করছে—তার বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীদের প্রতিবাদ। প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা প্রয়োগের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হলে পরবর্তী ধাপ হতে পারে সামাজিক বয়কট, অর্থাৎ ওই ডাক্তারের ক্লিনিকে কোনো রোগী যাবে না, এলাকার কোনো ব্যবসায়ী কোনো পণ্য বা সার্ভিস তার কাছে বিক্রি করবে না ইত্যাদি।
যেহেতু সবাই সমাজের ওপর নির্ভরশীল, তাই এ কৌশলের মাধ্যমে যেকোনো কর্তা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জনগণের সামনে আত্মসমর্পণ করানো সম্ভব।
জনসমর্থন শূন্য একটি দল ক্ষমতায় টিকে থাকে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর বেআইনি ব্যবহারের মাধ্যমে। তবে বাস্তবে স্বল্পসংখ্যক সুবিধাভোগী কর্মকর্তাই এতে সহায়তা করে। সমগ্র দেশে একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক আন্দোলন ধূমায়িত হলে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর আচরণ পাল্টে যায়। কারণ, বাহিনীর অধিকাংশ সদস্যই সুবিধাভোগী বৃত্তের বাইরে অবস্থান করে এবং তারা বৃহত্তর জনগণেরই একটি অংশ। একপর্যায়ে যখন তারা উপলব্ধি করে যে গণআন্দোলনের সাফল্য তাদের স্বার্থও রক্ষা করবে, তখন তারা জনগণের বিরুদ্ধে বেআইনি আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জানায়।
যেকোনো রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য প্রয়োজন অর্থের। যেহেতু মানুষই একটি গণমুখী কর্মসূচির প্রধান সুবিধাভোগী, তাই এ অর্থ তাদের কাছ থেকেই আসতে হবে। বাংলাদেশের দেড় কোটি মানুষ বিদেশে কর্মরত। বাইরে অবস্থানকালে দেশের জন্য ভালবাসা অনেক বৃদ্ধি পায়। এলাকার যেকোনো কল্যাণমূলক কাজে তারা অংশগ্রহণ করবে এটাই স্বাভাবিক।
সাইফুর রহমান: জ্যেষ্ঠ তথ্য প্রযুক্তিবিদ ও সার্টিফাইড প্রফেশনাল অস্ট্রেলিয়ান কম্পিউটার সোসাইটি








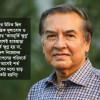

Comments