আমি যত না বাবার সন্তান, তার চেয়ে বেশি মায়ের
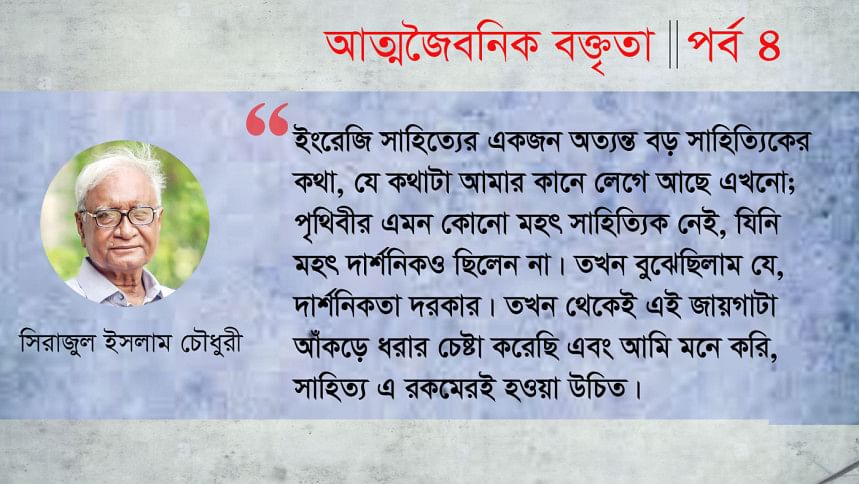
লেখক, গবেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তার ৮৭তম জন্মদিন উপলক্ষে গত ২৩ জুন বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে একক আত্মজৈবনিক বক্তৃতা দেন। ওই বক্তৃতায় উঠে আসে তার মা-বাবার স্মৃতি, শৈশব কৈশোরের দিনগুলোর বর্ণনা, শিক্ষা ও সাহিত্য জীবন এবং মুক্তিযুদ্ধের আগে-পরের সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতির নানা অনুষঙ্গ। সবমিলিয়ে তার এই বক্তৃতা যেন ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসেরই অংশ।
এই শিক্ষাবিদের দেওয়া আত্মজৈবনিক বক্তৃতার কথাগুলো ৭ পর্বে প্রকাশিত হচ্ছে দ্য ডেইলি স্টার বাংলায়। দীর্ঘ বক্তৃতাটি অনুলিখন করেছেন ইমরান মাহফুজ, খালিদ সাইফুল্লাহ ও মোহাম্মদ আবু সাঈদ। আজ এর চতুর্থ পর্ব প্রকাশিত হচ্ছে।
ব্যক্তিগত জীবনে আমি উপলব্ধি করেছি, আমি যত না আমার পিতার সন্তান, তার চেয়ে বেশি মাতার সন্তান। পিতাও আমার অভিভাবক ছিলেন, আমার মঙ্গল করেছেন। কিন্তু, আমার মাতার যে চরিত্র, যে অবস্থান- সেইটা ভিন্ন। আমি দেখতাম মাতা এবং পিতার কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে।
আমার পিতা খুব আশাবাদী ছিলেন। সেইটা আমার মধ্যেও আছে। তিনি আশা করতেন যেহেতু আমরা ঢাকার লোক, বুড়িগঙ্গার ওপরে ব্রিজ হবে। টেমস নদীর ওপরে কতগুলো ব্রিজ আছে তিনি জানেন। হাওড়ার ব্রিজ দেখেছেন। বুড়িগঙ্গায় ব্রিজ হবে, গ্রাম থেকে তিনি আসা-যাওয়া করবেন। কিন্তু, বাস্তবতা হলো যে, ব্রিজ হলো না।
উন্নয়ন চলল উত্তর দিকে। যেখানে ক্যান্টনমেন্ট আছে, বিমানবন্দর আছে। দক্ষিণ দিকে নদীর ওইপাড়ে কোনো উন্নয়ন হলো না। তো আমার বাবা সেইখানে খুব হতাশ হলেন। বাইরে থেকে যারা শরণার্থী আসছেন, তারা তখন জায়গা-জমি কিনছেন। কিন্তু, আমার বাবা ভাবছেন, আমরা তো এখানকার লোক, আমাদের জায়গা-জমির কী দরকার!
আমার মা বাস্তববাদী ছিলেন। এই বাস্তববাদী মা তাকে তাড়া দিলেন। তখন আমার বাবা জমি খুঁজতে বের হলেন এবং দেখলেন যে, ভালো জায়গা সব চলে গেছে। তিনি নবাবগঞ্জে ছোট্ট একটা জায়গা পেলেন, সেখানে একটা ঘর তুললেন। আমার মেজো ভাই ততদিনে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন। সে ওই বাড়ির নাম দিলো 'শেল্টার'।
এবার অন্য একটা বিষয় বলি। আমি প্রথমে খুব সমালোচনা লিখতাম। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদরা 'কণ্ঠস্বর' বের করেন, হাংরি জেনারেশন নিয়ে কাজ করেন, বলা যায় অনুকরণ, এরা সব নকল। সে সময় একটা কলাম লিখতাম প্রতি মাসে পত্রিকায়। এতে তাদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতাম। কিন্তু, ব্যক্তিগত আক্রমণ না। কাজ নিয়ে কথা বলতাম।
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদরা একটা আড্ডা করতেন সপ্তাহে। এতে তারা আমার লেখা নিয়ে তুমুল আলোচনা করতেন। বলতেন, আমাকে নিয়ে তাদের অনেক আশা ছিল। কিন্তু, আমি তাদের হতাশ করেছি।
আর একবার আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে বলেছিলাম 'পালের গোদা'। সেটা তিনি এখনো ভুলতে পারেন না, প্রায় এটা নিয়ে বলেন। তার একটা বই আমাকে উৎসর্গ করে লিখলেন, 'পালের গোদা'র উপহার আপনার জন্য।
দ্বিতীয় ধাপের কথা বলি। আমার একটা স্কলারশিপ হবার কথা, প্রস্তুতি নিচ্ছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাই সাহেব ও মুনির চৌধুরীর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। এর মধ্যে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শেকসপিয়ারের ৪০০তম জন্ম অনুষ্ঠান চলছে, সে সময় আমি গবেষণার বিষয় ঠিক করেছিলাম 'শেকসপিয়ার ইন বেঙ্গল'।
আমি ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটিতে গেলাম, পিএইচডি করলাম তিনজন ঔপন্যাসিকের ওপরে, তারা কিন্তু আমার পাঠ্যসূচিতে ছিলেন না। এটা অসম্ভব মনে হয় আমার কাছে, তাদের সমস্ত লেখা, সমালোচনা, চিঠিপত্র, বিতর্ক সবকিছু নতুন করে পড়ে আমাকে লিখতে হয়েছে। তখন আমাদের জায়গাটা এত সংকীর্ণ ছিল না।
আমি মফস্বল থেকে গিয়েছিলাম ব্রিস্টল শহরে, তিনজন ঔপন্যাসিকের ওপরে আমি কেন পিএইচডি করতে গেলাম? তিনজন ঔপন্যাসিকের তিনটি ধারা আমি দেখাতে পেরেছিলাম। থিসিসটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে পরে।
এখন সাহিত্য সম্পর্কে আমার ধারণার কথাটা বলতে হবে। আমরা সাহিত্য পাঠ করেছি নন্দনতাত্ত্বিকভাবে। বাংলাতেও যা পড়া হতো, ইংরেজিতেও তাই পড়া হতো। আমাদেরকে প্রথম বাইরের জগতের সাথে পরিচয় করালেন সৈয়দ আলী আশরাফ। ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস যাকে বলে সাহিত্যের, আমাদেরকে তা পড়ালেন। আমি আশরাফ সাহেবের কাছে সেটা শিখলাম। কিন্তু, তা পর্যাপ্ত মনে হলো না আমাদের কাছে। পরে যেটা বুঝলাম, সাহিত্যের পেছনে তো ইতিহাস আছে।
এটা শেখার কারণ হলো, আমি যখন লিপসে যাই, তখন সেখানে দুজন বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। একজন হুইলসন নাইট, অনেক বড় একজন স্কলার। কিন্তু, তিনি হচ্ছেন নন্দনতাত্ত্বিক লাইনের; আরেকজন ক্যাটাল, তিনি ছিলেন মার্কসবাদী, তিনি উপন্যাসকে ব্যাখ্যা করেন বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের আলোকে, যেখানে শ্রেণি আছে ইতিহাস আছে শ্রেণিদ্বন্দ্ব আছে—আমার কাছে মনে হল এটাই তো পাওয়া উচিত।
এই ধারাতেই আমি সাহিত্য সমালোচনা করেছি এবং পড়ানোর চেষ্টা করেছি। আমি যখন ছাত্র অবস্থায় ছিলাম তখন একজন সমালোচকের কথা আমার খুব কানে বাজল। তিনি খুব কটাক্ষের স্বরে বলেছিলেন, মার্ক্সসিস্টরা আসলে নিজেরাই মার্ক্সকে ধারণ করেন না। এটা আমার মনে ছিল। আমি লিপসে গিয়ে জেন অস্টিনের নায়কদের ব্যাপারে বিস্তারিত দেখাতে চেষ্টা করলাম যে, তারা সবাই মরালিস্ট কিন্তু তাদের এই মরালের ভিত্তিতে আছে প্রপার্টি। প্রপার্টি না থাকলে তারা আসলে মরালিস্ট হতে পারত না।
এই দৃষ্টিভঙ্গিটা আমি আমার সাহিত্য সমালোচনায় নিয়ে এসেছি। একটা উদাহরণ দেই, যেমন আমি রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসটার ওপর লিখেছিলাম- কুমুদ সে আবদ্ধ, তার ভাই তাকে আশ্রয় দিতে পারছে না, সামন্তবাদ ভেঙে পড়ছে, তাকে তুলে নিচ্ছে উঠতি এক সামন্তকারী বুর্জোয়া, কলোনিয়াল বুর্জোয়া, কুমুদ এর মাঝখানে পড়ে বৌদ্ধ হয়ে গেছে। তো এই ধরনের সাহিত্য সমালোচনা আমি করেছি।
পাকিস্তান আমলে আমার প্রথম বই—নাম ছিল 'অন্বেষণ'। বাংলাদেশে আমার প্রথম বই বের হয়—'নিরাশ্রয়ীর তীর'। আমি দেখলাম, মানুষ আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না, নিরাশ্রয়ী হয়ে পড়ছে, প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে সেটা লিখলাম।
'ঢাকায় থাকি' লিখতাম, রূপালি পত্রিকাতে। 'ঢাকায় থাকি'র ইতিহাস হচ্ছে শনিবারের চিঠি বুদ্ধদেব বসুদের খুব ধোলাই করত, সেখানে লিখেছে সজনীকান্ত- 'যদিও সে, ছোট কিসে, ঢাকায় থাকে!' আমি তখন 'ঢাকায় থাকি' 'নাগরিক' নামে লিখতাম। আমার ওপর প্রভাব পড়েছিল তিনজন লেখকের। একজন বুদ্ধদেব বসু, একজন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আরেকজনের শিবরাম চক্রবর্তী।
সুধীন্দ্রনাথ তো খুবই মার্জিত, সুন্দর সুন্দর কথা বলেন, কিন্তু তিনি তো সহে না সহে না প্রাণে জনতার জঘন্য মিতালি—যেটা আমি পরবর্তীতে পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করেছি। বুদ্ধদেব বসু আনন্দে সাহিত্য করেন। তিনি বলেন, সাহিত্যে চলাটাই প্রধান, গন্তব্য বলে কিছু নেই।
শিবরাম চক্রবর্তী কৌতুক করেন, তিনি আবার মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি লিখেছেন। মস্কোর পক্ষে এবং পণ্ডিতের বিপক্ষে। কিন্তু, তিনি আবার বলছেন, ভারতীয় যে সাম্যবাদ তা কিন্তু মস্কোর চাইতে ভালো। এই প্রভাবগুলো আমার ওপর পড়েছে।
বুদ্ধদেব বসুর এক সহপাঠী আমাদের ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন। তখন বুদ্ধদেব বসুর যে উক্তি—চলতে থাকা, গন্তব্য নেই—তা শিখছি। ইংরেজি সাহিত্যের একজন অত্যন্ত বড় সাহিত্যিকের কথা, যে কথাটা আমার কানে লেগে আছে এখনো—পৃথিবীর এমন কোনো মহৎ সাহিত্যিক নেই, যিনি মহৎ দার্শনিকও ছিলেন না। তখন বুঝেছিলাম যে, দার্শনিকতা দরকার। তখন থেকেই এই জায়গাটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছি এবং আমি মনে করি, সাহিত্য এরকমেরই হওয়া উচিত।


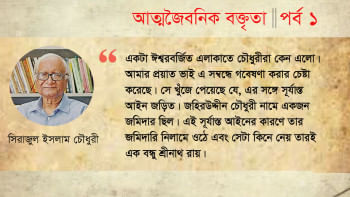

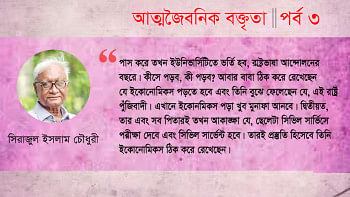








Comments