উচ্চতাভীতি কেন হয়, কাটিয়ে উঠবেন কীভাবে

উচ্চতাভীতির কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন না অনেকে। আবার এই উচ্চতাভীতির কারণে উঁচু ভবনে অফিস করা দুঃসাধ্য ব্যাপার অনেকের কাছে।
কেন এই উচ্চতাভীতি, সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন ইউএস বাংলা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এবং স্কয়ার হসপিটালস লিমিটেডের সাইকিয়াট্রি বিভাগের সিনিয়র কনসালট্যান্ট ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) অধ্যাপক ডা. মো. আজিজুল ইসলাম।
উচ্চতাভীতি কী ও কেন হয়
অধ্যাপক আজিজুল ইসলাম বলেন, উচ্চতাভীতিকে অ্যাক্রোফোবিয়া বলা হয়। অ্যাক্রাফোবিয়া মানে উচ্চতার প্রতি অস্বাভাবিক, মাত্রাতিরিক্ত এবং অযৌক্তিক এক ধরনের ভয়। উচ্চতায় উঠতে হবে, উঁচু কোনো স্থানে যেতে হবে এটা নিয়ে ভয়। সবসময় এই ভয়টা হয়, ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে এবং মাত্রাতিরিক্ত এই ভয়ের অনুভূতি উঁচু কোনো স্থানে গেলেও হতে পারে, এমনকি চিন্তা করলেও হতে পারে।
উচ্চতাভীতি এমনভাবে হয় যে উচ্চতায় গেলে, উচ্চতায় যাওয়ার কথা চিন্তা করলে আক্রান্ত ব্যক্তির ভেতর অত্যন্ত কষ্ট তৈরি হয়। সেটি উদ্বিগ্নতার আকারে হতে পারে, আবার প্যানিকের মতোও হতে পারে। প্যানিকের মতো হলে বুক ধড়ফড় করবে, অস্থিরতা, শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হবে, ঘাম হবে। হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়া, মাথা ঘোরা, চলাফেরা রহিত হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থাও হতে পারে।
উচ্চতায় যাওয়ার কথা চিন্তা করলে বা উঁচু স্থানে গেলে এই সমস্যা, মানসিক চাপ বা কষ্টের অনুভূতি যদি ৬ মাসের বেশি সময় ধরে থাকে, মাত্রাতিরিক্ত ভয় এবং তা সবসময় যদি হতে থাকে তখন তাকে ফোবিক ডিসঅর্ডার বা অ্যাক্রোফোবিক ডিসঅর্ডার বলা হয়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবন ও কাজকর্মকে ব্যাহত করতে পারে অ্যাক্রোফোবিয়া।
ফোবিয়া হচ্ছে নির্দিষ্ট বস্তু বা পরিস্থিতির প্রতি অস্বাভাবিক, অযৌক্তিক ভয় যা এক ধরনের উদ্বেগজনিত ব্যাধি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ফোবিয়ার কতগুলো ধরন আছে। উচ্চাতভীতি বা অ্যাক্রোফোবিয়া স্পেসিফিক ফোবিয়ার অন্তর্গত।
উচ্চতাভীতি কেন হয়
উচ্চতাভীতি হওয়ার কারণকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- বায়োলজিক্যাল বা জৈবিক কারণ, সাইকোলজিক্যাল বা মানসিক কারণ এবং সোশ্যাল বা সামাজিক কারণ।
বায়োলজিক্যাল বা জৈবিক কারণ
১. জেনেটিক কারণে, বংশপরম্পরায় উচ্চতাভীতি হতে পারে। মা-বাবা, ভাই-বোন, নিকটআত্মীয় কারো অ্যাক্রোফোবিয়া থাকলে তাদের ঝুঁকি বেশি।
২. মস্তিষ্কে নরএপিনেফ্রিন ও এপিনেফ্রিন এই দুইটি হরমোন ও ডোপামিনে কোনো ব্যতয় ঘটলে বা বায়োকেমিক্যাল পরিবর্তনের কারণে হতে পারে।
সাইকোলজিক্যাল বা মানসিক কারণ
১. দেখে দেখে শিখে আর সেখান থেকে ফোবিয়া হতে পারে। যেমন- মা যদি তেলাপোকা ভয় পান, উচ্চতায় ভয় পান তবে সেটা দেখে সন্তানের ভেতরেও সেই ভয় কাজ করতে পারে।
২. মানসিক ট্রমার কারণে হতে পারে। মনের ভেতর বিশেষ কষ্ট, মানসিক চাপ, খুব খারাপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার প্রভাবের কারণে হতে পারে।
সোশ্যাল বা সামজিক কারণ
১. উচ্চতা বিপজ্জ্নক, ভয়ের কিছু- এগুলো যদি কারো মধ্যে ঢুকে তাহলে সেখান থেকে অ্যাক্রোফোবিয়া হতে পারে।
২. সামাজিক বিভিন্ন ফ্যাক্টরের প্রভাবে হতে পারে। চাকরি নেই, অন্যদের সঙ্গে মিশতে না পারা এসব সমাজিক ফ্যাক্টর মনের ওপর চাপ ফেলে, ট্রমা তৈরি করে, হতাশা, বিষণ্নতা হয়। সেখান থেকেও ফোবিয়া হতে পারে।
ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অ্যাক্রোফোবিয়া বেশি হয়।
লক্ষণ
১. উচ্চতা নিয়ে চিন্তা, উঁচু ভবন, পাহাড় বা উঁচু কোনো স্থানে ওঠতে পারব না, উচ্চতায় যেতে পারব না এই চিন্তা মাথার ভেতর ঘোরা। সেই চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত থাকা।
২. উচ্চতায় যাওয়ার পর এমনকি উচ্চতায় যেতে হবে তা চিন্তা করলে ভয়ের অনুভূতি হওয়া।
৩. উদ্বিগ্নতা, চিন্তা, মানসিক চাপ প্রকাশ পায়।
৪. প্যানিক অ্যাটাকের মতো হয়। বুক ধড়ফড়, অস্থিরতা, হাত-পা অবশ, ঘাম হয়, মাথা ঝিমঝিম করে। মাথা ঘোরানো, শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে।
৫. দীর্ঘদিন অ্যাক্রোফোবিয়া থাকলে উদ্বিগ্নতার অন্যান্য লক্ষণ দেখা দিতে পারে। ঘুমের সমস্যা হয়, যেকোনো স্থানে গেলেই ভয়ের অনুভূতি, হতাশায় ভুগতে পারেন।
অ্যাক্রোফোবিয়া কাটানোর উপায় বা চিকিৎসা
অধ্যাপক আজিজুল ইসলাম বলেন, বায়োলজিক্যাল ও সাইকোলজিক্যাল এই ২ ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয় অ্যাক্রোফোবিয়ার রোগীকে।
সাইকোলজিক্যাল বা মানসিক চিকিৎসার অংশ হিসেবে বিহেভিয়ার থেরাপি দেওয়া হয়। আচরণ পরিবর্তন করে রোগীকে উচ্চতায় তোলায় ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য শিথিলকরণ বা রিল্যাক্সেশন থেরাপি দিতে হবে। ধ্যান, পেশি শিথিলকরণ, যোগব্যায়াম এগুলো করে রোগীর মন শিথিল করতে হবে।
এরপর অ্যাক্রোফোবিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিকে উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে। সেটি ২ ভাবে করা যেতে পারে। থেরাপিস্ট বা কারো সহায়তায় প্রথমে আস্তে আস্তে স্বল্প উচ্চতার কোনো স্থানে নিয়ে যাওয়া এবং ধীরে ধীরে আরও উঁচু স্থানে উঠার অভ্যাস করানো। প্রথমে কারো সঙ্গে দিতে হবে, এরপর একা উঠার অভ্যাস করাতে হবে।
এর পাশাপাশি বায়োলজিক্যাল চিকিৎসা হিসেবে রোগীর অবস্থা অনুযায়ী ওষুধ দেওয়া হয়। বিহেভিয়ার থেরাপি এবং ওষুধ যদি একসঙ্গে প্রয়োগ করা হয় তাহলে চিকিৎসার ফলাফল ভালো হয়। রোগী যদি একেবারেই ভালো হয়ে যান তবে ক্ষেত্রবিশেষে কারো কারো আবারও অ্যাক্রোফোবিয়া হতে পারে।
দৈনন্দিন জীবনে মানসিক চাপ যত বাড়বে অ্যাক্রোফোবিয়া ফিরে আসার হারও বাড়ে। যদি কেউ রিল্যাক্সড থাকেন, কারো মন ভালো থাকে তাহলে আর ফিরে নাও আসতে পারে।
অধ্যাপক আজিজুল ইসলাম বলেন, অ্যাক্রোফোবিয়ায় যদি কেউ ভোগেন তাহলে সবাইকে বুঝতে হবে এটি একটি রোগ। অবহেলা না করে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। চিকিৎসা না নিলে হতাশা, ব্যর্থতা, উদ্বিগ্নতা বাড়বে এবং পরে অন্যান্য সমস্যা তৈরি হবে।



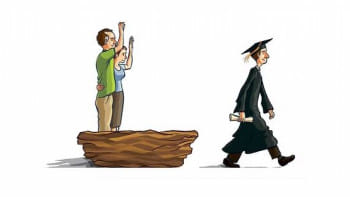
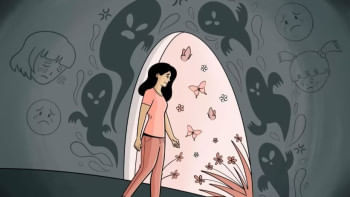




Comments