সাতচল্লিশ কি কেবল ‘দেশভাগে’র রাজনীতি?

বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৪৭ সালকে কীভাবে পাঠ করবো? সাতচল্লিশ বাংলাদেশের ইতিহাসে অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। সাতচল্লিশে যে জনাঞ্চল স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অর্জন করে পাকিস্তান রাষ্ট্রভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে, সেই জনভূমিই ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সার্বভৌম বাংলাদেশ।
এই বিবেচনায় সাতচল্লিশ ও একাত্তর কোনো সাংঘর্ষিক বিষয় নয়, বরং সাতচল্লিশেরই পরম্পরা একাত্তর। এই জনাঞ্চলের জনমানুষ যেমন আত্মপরিচয়ের জন্য চল্লিশের দশকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে, এই জনমানুষই বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে জীবন দিয়েছে, ষাটের দশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে যুক্ত থেকেছে এবং একাত্তরের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে।
ঐতিহাসিক পরম্পরার মধ্য দিয়ে বাংলা অঞ্চলে বসবাসকারী জনমানুষ মুখোমুখি হয় সাতচল্লিশের। এই পরম্পরার মধ্যে বিদ্যমান থাকে রাজনীতির গভীরতর ও বিচিত্র সমীকরণ। সাতচল্লিশের ঘটনা ও রাজনীতি কেবল সাতচল্লিশে সীমায়ত থাকে না; এর পরম্পরা তৈরি হয় আরও আগে—ভৌগোলিক, সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক প্রত্নস্মৃতির ভেতরে।
প্রাক-ঔপনিবেশিক কাল থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কাল পর্যন্ত পাশাপাশি বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনৈতিক ঘটনাপুঞ্জের সৃষ্টি হয়, তা নানা দৈশিক ও বৈশ্বিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭-এ এসে অনিবার্য রূপ ধারণ করে। এর মধ্য দিয়ে বাংলা অঞ্চলে ঘটে যায় আরও একটি বড় ঘটনা, দীর্ঘ সময় ধরে যাকে চিহ্নিত করা হয় 'দেশভাগ' হিসেবে।
'দেশভাগ' শব্দ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে যে প্রশ্নটি প্রথমেই আসে, তা হলো—দেশ বলতে কী বোঝানো হচ্ছে, কোন দেশের কথা বলা হচ্ছে? এর সীমা কী? ভাগ হলো কোন দেশ—অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশ নাকি, সমগ্র ভারত উপমহাদেশ? রাষ্ট্রের ধারণার মধ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব আছে। কিন্তু দেশ বলতে যে ধারণা, তার মধ্যে থাকে একটি জনাঞ্চলের মানুষের মধ্যে বিরাজমান স্বদেশের ধারণা—যা অনেকখানি অনুভূতিসাপেক্ষ। দেশচেতনা আর রাষ্ট্রচেতনা অভিন্ন নয়। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় ২০০ বছর একই ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর আওতায় থাকার ফলে ভারত সম্পর্কে একটি অখণ্ড দেশ-ধারণাও বিরাজমান আছে। সেই বিবেচনায় দেশভাগ বলতে সমগ্র ভারত উপমহাদেশ ভাগের একটি ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু ভারত কখনোই একক দেশ-ধারণায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কংগ্রেস-কথিত একক ভারতীয় জাতীয়তাবাদেও একে যৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায়নি।
ফলে একটি বৃহৎ দেশ ভারত সাতচল্লিশে ভাগ হয়ে তিন ভূখণ্ডের দুই দেশে পরিণত হলো—এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আছে একমাত্রিক ভারতসাপেক্ষতা। দেশভাগকে ভারত-ভাগের প্রতিরূপ হিসেবে বিবেচনার মধ্যে একটি পূর্বতন ঔপনিবেশিক মানসিকতা যেমন উপলব্ধি করা যায়, তেমনি ওই ঘটনার পর সাতাত্তর বছর অতিক্রান্ত হলেও এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াশীলতার উপস্থিতি দাবি করা যায়। বাংলাদেশে প্রচলিত 'দেশভাগ' বলতে বিশেষভাবে বিবেচিত হয় বাংলা-ভাগের বাস্তবতা। যদিও পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এক দেশভুক্ত কিনা এই নিয়ে ভিন্ন বিবেচনার সুযোগ আছে। দেশভাগ সংক্রান্ত প্রায় সকল আলোচনাতে 'দেশত্যাগ', 'দেশবদল', 'দেশচ্যুতি', 'দেশহারানো', 'দেশছাড়া' প্রভৃতি শব্দবন্ধগুলো দিয়ে একটা বিপুল শ্রেণির মানুষের বাস্তুত্যাগের সংকটকে চিহ্নিত করা হয়।
শব্দবন্ধগুলোই চিহ্নিত করে দেয়, বাংলার অন্তর্ভুক্ত দুই অংশ এক দেশভুক্ত নয়। এক দেশভুক্ত হলে ত্যাগ বা বদলের প্রসঙ্গ আসতো না। দুই বাংলা বিভিন্ন সময়ে একই প্রশাসনিক কাঠামোর আওতাভুক্ত থাকলেও, দুই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর একই ভাষা তথা 'অভিন্ন বাংলা'র দাবি জারি থাকলেও দুই অঞ্চলের ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক এমনকি ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে সুচিহ্নিত। প্রাচীন বঙ্গ জনপদ থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়-জাতি-গোষ্ঠী-শ্রেণির সমন্বয়ে যে বাংলা জনাঞ্চল অর্থাৎ বাংলাদেশ, তার ভূ-পরিধিগত স্বাতন্ত্র্যও সুপ্রাচীন।
পদ্মা-মেঘনা-যমুনাবিধৌত পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশ মূলত প্রাচীন বঙ্গ জনপদের উত্তরসূরি। বাংলার সংগ্রামশীল ও অধিকারসচেতন জনমানুষের পরিচয় তার সুদীর্ঘ নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়পর্বে কেন্দ্রীয় শক্তির আধিপত্যও যেমন এই জনাঞ্চলের মানুষ মেনে নেয়নি, তেমনি কাঠামোবদ্ধ মতবাদ বা ধর্মমত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন নতুন মতবাদ ও ধর্মমতকে গ্রহণ করেছে; নিপীড়নমূলক কাঠামোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বিদ্রোহও করেছে। এই জনাঞ্চলের মনোভূমিতে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করা স্বাভাবিক। চল্লিশের দশকে এই মুক্তি-আকুল জনগোষ্ঠী তথা বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত তার আত্মসন্ধানের মহাযাত্রায় একটি বাহন হিসেবে সামনে পেয়ে যায় মুহম্মদ আলি জিন্নাহ পরিকল্পিত 'দ্বিজাতিতত্ত্ব'জাত 'পাকিস্তান-আন্দোলন'কে। 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' তথা ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী ধারণা বাংলার জনসাধারণকে একটি গভীরতর বাস্তবতার মুখোমুখি করে।
উপনিবেশের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পূর্ববঙ্গের জনমানুষ কেন 'পাকিস্তান-আন্দোলন'কে সারথি করল, তার আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত এখন অনেকখানি প্রকাশ্য ও স্পষ্ট, যাকে এক কথায় বলা যায় বৈষম্যমুক্তির স্বপ্ন। এই বৈষম্যমুক্তির পেছনে ধর্মতাত্ত্বিক বিবেচনার চেয়েও প্রাধান্য পায় অর্থনৈতিক মুক্তি, রাজনৈতিক মুক্তি। সাতচল্লিশের পর পূর্ববঙ্গ আকৃতিগতভাবে একটি সুনির্ধারিত রাজনৈতিক রূপ লাভ করে। সময়ের পরিক্রমায় যে বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে পাওয়া যায়—একসময়ের সাতচল্লিশ-পূর্বাপর পূর্ববঙ্গ—সেই বাংলাদেশও বঙ্গ জনপদের প্রাচীন কাঠামোকেই নিজের ভেতর ধারণ করেছে।
কেবল দেশভাগ নয়, পূর্ববঙ্গের জনগণের শোষণমুক্তির আন্দোলন ও উপনিবেশ মুক্তির স্মারক হিসেবেও ১৯৪৭-এর তাৎপর্য অনুসন্ধান করা হয়। এই শোষণমুক্তির সঙ্গে স্বাধীনতার প্রশ্নটি জড়িত। বিশেষত বাংলা জনাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান বাংলাভাষী পাকিস্তান আন্দোলনকে 'স্বাধীনতা'র আন্দোলন হিসেবেই দেখেছিল এবং ১৯৪৭-এ তা অর্জন করেছিল। তাই সাতচল্লিশের রাজনীতি 'স্বাধীনতা'র রাজনীতি নাকি 'দেশভাগে'র রাজনীতি, এ নিয়ে ভাবনাগত ভিন্নতা ও বিতর্ক এখন পর্যন্ত অমীমাংসিত ও চলমান।
'দেশভাগ' শব্দটির রয়েছে একটি পরিভাষাগত ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত। সাতচল্লিশ-পূর্বাপর সময়ে পার্টিশন, স্বাধীনতা, আজাদী, পাকিস্তান কায়েম, মুক্তি, নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, বাটোয়ারা কিংবা বর্ডারিংয়ের বাংলা পরিভাষা হিসেবে বহুল প্রচলিত শব্দ 'দেশভাগ'। কিন্তু সাতচল্লিশকালে পূর্ববাংলা-প্রান্তের জনগণের কাছে তা দেশভাগ হিসেবে গৃহীত হয়নি।
সাতচল্লিশের অব্যবহিত পরের মননশীল ও সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্ম এবং প্রকাশিত পত্রপত্রিকা সাক্ষ্য দেয়, সাতচল্লিশকে প্রথমত স্বাধীনতা বা আজাদী হিসেবেই গ্রহণ করা হয়। মূলত ষাটের দশক থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসক শক্তির বিপরীতে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকশিত হয়, তার বয়ানে সাতচল্লিশের ঘটনাসমষ্টি দেশভাগ হিসেবে গৃহীত হতে থাকে।
যদিও এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ পূর্ব বাংলার আর্থ-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতেই বিকশিত; তথাপি পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণনীতির বিপরীতে এক কল্পিত অখণ্ড সাংস্কৃতিক 'বাংলা দেশ' চেতনা ওইকালের জাতীয়তাবাদী চিন্তায় অবচেতনভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশ পর্বে 'দেশভাগ' শব্দটি সাতচল্লিশের রাজনীতির সমার্থক হিসেবে গৃহীত হয়।
'দেশভাগ' শব্দগত ও রাজনৈতিকভাবে রূপ লাভ করে একটি বাঙালি জাতীয়তাবাদী বয়ানসৃষ্ট ফলাফল হিসেবে। অর্থাৎ একই রাজনৈতিক ঘটনা পরবর্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তার সাপেক্ষে বিবেচিত ও সংজ্ঞায়িত হয়। দেশভাগের ফলে যে স্বভূমি ত্যাগ, দাঙ্গা, হত্যা, উদ্বাস্তু পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তা ঐতিহাসিকভাবে সমর্থিত। এই ভাগের প্রক্রিয়াগত ত্রুটি জন্ম দিয়েছিল এক বিপর্যয়কর পরিস্থিতির। এর দায় একই সঙ্গে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি কিংবা ক্রিয়াশীল স্থানীয় রাজনৈতিক শক্তি—কোনো পক্ষ এড়াতে পারে না।
কিন্তু দেশভাগের সঙ্গে যে অখণ্ড দেশ চেতনাকে আরোপ করা হয়, তার ভৌগোলিক ও চেতনাগত ঐক্যের পরিধি এখন পর্যন্ত অনির্ণীত। রাজনৈতিকভাবে নতুন দুই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে নতুন সীমানা নির্ধারণ তখন ছিল অনিবার্য। ব্রিটিশ আমলা সিরিল জন র্যাডক্লিফ সেই সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন জনশুমারিতে মানুষের সাম্প্রদায়িক অবস্থান তৈরি করা হয়েছিল; ধর্ম-সম্প্রদায় ও বর্ণ পরিচয়ে বিভক্ত করা হয়েছিল, যা ছিল মূলত ঔপনিবেশিক শাসনপ্রণালির অংশ। সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনশুমারি ও পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলোর সম্প্রদায়গত ফলাফল বিবেচনা কার্যকর ছিল বলে দাবি করা হয়; কিন্তু সেই বিবেচনা ঠিকঠাক কাজ করেনি।
এ কারণে দেখা যায়, অনেক হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল যেমন পাকিস্তানভুক্ত হয়েছে, তেমনি অনেক মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলও ভারতভুক্ত হয়েছে। আর সীমান্তবর্তী অঞ্চলের এই জটিলতা ছাড়াও দুই দেশের অভ্যন্তরে হিন্দু ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ পাকিস্তান ও ভারতের রাষ্ট্রসীমায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে এই ভাগের বিষয়টি যতটা না দেশচেতনার সঙ্গে জড়িত, তারচেয়ে বেশি রাষ্ট্রধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। দেশভাগ বা স্বাধীনতা ধারণার সঙ্গে কার্যকারণগত পরিস্থিতির সাপেক্ষে সাতচল্লিশের ঘটনামসষ্টিকে 'রাষ্ট্রের সীমানা চিহ্নিতকরণ' বা 'নতুন রাষ্ট্রসীমা' হিসেবে অভিহিত করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশে সাতচল্লিশের রাজনীতি এককভাবে দীর্ঘদিন চিহ্নিত হয়েছে কেবল দেশভাগের রাজনীতি হিসেবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আছে একমাত্রিকতা।
সাতচল্লিশের ঘটনা প্রধানত রাজনৈতিক ঘটনা। তাই একে পাঠ কারার ক্ষেত্রে 'স্বাধীনতা' বা 'দেশভাগ' দৃষ্টিকোণের ব্যবহারও রাজনৈতিক। তবে কোনো দৃষ্টিভঙ্গিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বহুস্তরিত বাস্তবতার একটি সামূহিক রূপ সাতচল্লিশের রাজনীতি।
দীর্ঘদিন পর্যন্ত সাতচল্লিশের ইতিহাসচর্চা ছিল 'হাই পলিটিক্সে'র বিষয়। সাতচল্লিশ পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় রাজনীতি, অর্থাৎ ক্ষমতার রাজনীতির শুদ্ধ্যশুদ্ধির দিকেই ছিল প্রধান মনোযোগ। জনমানুষের ওপর, বিভিন্ন শ্রেণির ওপর অভিঘাতকে শনাক্তির প্রয়াস ছিল সামান্য। মূলধারার এই ইতিহাসচর্চার বিপরীত দিক হচ্ছে জন-ইতিহাসচর্চা। জন-ইতিহাসচর্চায় সাতচল্লিশ-কেন্দ্রিক অনেক নতুন নতুন ভাষার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে—বিশেষত ওই সময়ের পর্বকে উপজীব্য করে রচিত কবিতা-উপন্যাস ছোটগল্প নতুন নতুন বয়ান হাজির করছে, যেখানে দুঃখের সঙ্গে প্রাপ্তির গল্পও থাকছে। নব্য ইতিহাসবাদী চর্চায় সাহিত্য-উপকরণগুলো ইতিহাস পাঠের জরুরি উপাদান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সাতচল্লিশ-পরবর্তী পূর্ববাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশের ওই সময়ের জনমানুষের কাছে সাতচল্লিশ-প্রসঙ্গটি ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত থাকে।
পাকিস্তান-পর্বে সাতচল্লিশকে দেখা হয় নতুন রাষ্ট্রপ্রাপ্তি হিসেবে। এর অব্যবহিত পরবর্তী সংকটে গুরুত্ব পায় পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ববাংলার ওপর আগ্রাসন-শোষণ ও কর্তৃত্ব প্রদর্শনের বহুমাত্রিক ঘটনা; রাজনীতি পায় নতুন গতি। নতুন প্রতিপক্ষ, নতুন শোষকের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম ও জাতীয়তার অনুসন্ধানে 'দেশভাগে'র অনুষঙ্গ ধীরে ধীরে ক্রিয়াশীল হতে থাকে।
সাতচল্লিশের ঘটনা প্রধানত রাজনৈতিক ঘটনা। তাই একে পাঠ কারার ক্ষেত্রে 'স্বাধীনতা' বা 'দেশভাগ' দৃষ্টিকোণের ব্যবহারও রাজনৈতিক। তবে কোনো দৃষ্টিভঙ্গিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বহুস্তরিত বাস্তবতার একটি সামূহিক রূপ সাতচল্লিশের রাজনীতি। ওই বাস্তবতার কিছু শক্তিশালী বয়ানও দীর্ঘদিন ধরে দুই রাষ্ট্রে জারি আছে। ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতার ফলে তথা অখণ্ড বঙ্গ ভাগ হওয়ার কারণে পূর্ববাংলা থেকে অনেক হিন্দু-ধর্মাবলম্বীকে দেশচ্যুত হতে হয়েছে, উদ্বাস্তু জীবনবরণে বাধ্য হতে হয়েছে, দলে দলে দেশত্যাগ করতে হয়েছে—এটি একটি বয়ান। কিন্তু এটিই একমাত্র বয়ান নয়। কোনো বয়ানই প্রশ্নাতীত নয়।
প্রতিষ্ঠিত বয়ানের সঙ্গে পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের বয়ান যদি তাতে যোগ না হয়, সেই বয়ানের বলয় পূর্ণতা পাবে না। সাতচল্লিশকে দেখার জন্য সাতচল্লিশের মধ্যেই আছে বহুত্ববাদী উপাদান। ফলে বাংলাদেশের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে সাতচল্লিশ স্বাধীনতা বা দেশভাগ বা রাষ্ট্রীয় সীমানা চিহ্নিতকরণ—এমন একক কোনো মীমাংসা নিয়ে উপস্থিত হয় না। তাই একমাত্রিক দৃষ্টিকোণ ব্যবহার না করে সাতচল্লিশের রাজনীতিতে সাতচল্লিশের বহুত্ব অনুসন্ধানের মধ্যেই এর সামূহিকতাকে ধারণ করা সম্ভব।


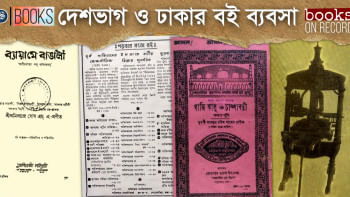








Comments