বঙ্গাব্দ ১৪৩২: ‘আজি পুরানো যা কিছু দাও গো ঘুচিয়ে’

সময়ের চাকা ঘুরে এল আরও এক পাক। চৈত্রের শেষ দিবসের আলো নিভল। রাত পেরিয়ে নতুন আলোর সকাল নিয়ে এল পুরাতন বছরের মলিনতা মুছিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা।
আজ পয়লা বৈশাখ; বঙ্গাব্দ ১৪৩২ এর প্রথম দিবস। জীবনকে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে এক পা এগিয়ে দেওয়া এ নববর্ষ যেন সেই মৃত্যুকেই লঙ্ঘন করে অনন্ত আনন্দের বোধে উদ্বোধিত হওয়ার দিন।
কাজপাগল রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রতিটি দিনই ছিল একেকটি নবজনমের লগ্ন। তথাপি একশ বছরেরও বেশি সময় আগে ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখে তিনি লিখেছিলেন, 'তবু মন একটা বিশেষ দিনের প্রয়োজন অনুভব করে। যেদিন সে প্রথম দিনকে আপনার মধ্যে বন্ধনমুক্তভাবে উপলব্ধি করতে পারে।'
বাঙালির জীবনে উৎসবের রঙ ছড়িয়ে আবার এসেছে সেই পয়লা বৈশাখ। আবহমানকালের বাঙালি ঐতিহ্যের বরণডালা সাজিয়ে বিপুল আয়োজনের ভেতর দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে তৈরি সবাই।
আজ ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সব মানুষ শামিল হবেন এ বৈশাখী উৎসবে। গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী নতুন বাংলাদেশে সব ভেদাভেদ ভুলে নতুন বঙ্গাব্দকে বরণ করে নেওয়ার চেষ্টা থাকবে সবার।
লোকসংস্কৃতি গবেষকদের কাছে বাংলা নববর্ষ এক অনন্য বৈশিষ্ট্যময় উৎসব। কারণ পৃথিবীতে প্রচলিত বেশিরভাগ বর্ষপঞ্জির উৎপত্তি কোনো না কোনো ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু বাংলা নববর্ষের সঙ্গে ধর্মীয় অনুষঙ্গ নেই। মূলত কৃষিকাজ ও খাজনা আদায়ের ব্যবস্থাকে ঘিরে এর প্রচলন হয়। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যবসা-বাণিজ্যের দেনা-পাওনার হিসাব মেটানো।
তবে কৃষি উৎসব বা রাজস্ব আদায়ের বিষয় হিসেবে বৈশাখকে সামনে এনে বাংলা সন প্রবর্তনের পর তা রাজনৈতিক হয়ে ওঠে পাকিস্তান শাসনামলে।
সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের শাসকশ্রেণি যখন তাদের অন্যায়-অন্যায্য শাসনকে ন্যায্যতা দিতে ধর্ম ব্যবহার করতে চেয়েছে, তখন এ ভূখণ্ডের বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করে তোলে এর সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়।
পাকিস্তানের সেনাশাসক আইয়ুব খানের আমলে বাঙালির বাঙালিয়ানা নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে যখন রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ করা হয়, তখন এই বর্ষবরণ উৎসব হয়ে ওঠে বাঙালির আত্মপরিচয় টিকিয়ে রাখার রাজনৈতিক হাতিয়ার।
তখন ছায়ানট সংস্কৃতি কেন্দ্র রমনার বটমূলে প্রতিবাদী উচ্চারণে বর্ষবরণের যে আয়োজন করেছিল, তা হয়ে ওঠে নগরে এই উৎসবের প্রধান অনুষঙ্গ।
সেই ষাটের দশকে রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ উৎসব বাঙালির আত্মপরিচয়ের আন্দোলন-সংগ্রামকে বেগবান করেছিল। সেই একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রেরণা জুগিয়েছিল ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামেও।
বাঙালি সমাজকে নিয়ে মুক্তির পথযাত্রী হতে এবার সেই ছায়ানটের বর্ষবরণের বার্তা হলো—'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়।'
ছায়ানটের ৫৮তম এ আয়োজন যথারীতি শুরু হয়েছে নতুন বছরের প্রথম দিন সোয়া ৬টায় ভোরের আলো ফুটতে ফুটতে ভৈরবীর রাগালাপ দিয়ে। ব্যতিক্রম হলো, এবারই প্রথম ছায়ানটে বর্ষবরণ করল বাঙালি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সদ্যপ্রয়াত সভাপতি সন্জীদা খাতুনকে ছাড়াই।
গত শুক্রবার এ আয়োজনের বিস্তারিত তুলে ধরতে করা সংবাদ সম্মেলনে ছায়ানটের সাধারণ সম্পাদক লাইসা আহমদ লিসা বলেন, 'বিশ্বব্যাপী যেমন ক্ষয়ে চলেছে মানবতা, তেমনি এদেশেও ক্রমান্বয়ে অবক্ষয় ঘটছে মূল্যবোধের। তবুও আমরা আশাহত হই না, দিশা হারাই না, স্বপ্ন দেখি হাতে হাত রেখে সকলে একসাথে মিলবার, চলবার। বাঙালি জাগবেই, সবাই মিলে সুন্দর দিন কাটানোর সময় ফিরবেই। সার্থক হবেই হবে, মানুষ-দেশ, এ পৃথিবীকে ভালোবেসে চলবার মন্ত্র।'
'আনন্দ শোভাযাত্রা'র প্রতিপাদ্য 'নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান'
গত জুলাই অভ্যুত্থানে সরকার বদলের পর এবার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইউনেস্কোর অপরিমেয় বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পাওয়া বর্ষবরণের 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র নাম বদলে রাখা হয়েছে বর্ষবরণের 'আনন্দ শোভাযাত্রা', যা নিয়ে সমালোচনা আছে।
১৪৩২ বঙ্গাব্দের প্রথম সূর্যাদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হওয়া ছায়ানটের বর্ষবরণের আয়োজন শেষ হতে না হতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের সামনে থেকে সকাল ৯টায় শুরু হবে এই শোভাযাত্রা। শাহবাগ মোড় ঘুরে টিএসসি মোড়, শহীদ মিনার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র, দোয়েল চত্বর হয়ে বাংলা একাডেমির সামনের রাস্তা দিয়ে পুনরায় চারুকলা অনুষদে গিয়ে শেষ হবে তা।
গতকাল রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর জানিয়েছে, শোভাযাত্রা চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য প্রবেশ পথ ও সংলগ্ন সড়ক বন্ধ থাকবে। 'শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য রক্ষায়' আশপাশ দিয়ে শোভাযাত্রায় প্রবেশ করা যাবে না। সবার প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে শেষ প্রান্ত দিয়ে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের জন্য।
জনসংযোগ দপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুদিনের ঐতিহ্য ও স্বকীয়তা অব্যাহত রেখে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক করার জন্য লোক-ঐতিহ্য ও ২৪ এর চেতনাকে ধারণ করে আরও বড় পরিসরে এবং বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে এবছর শোভাযাত্রায় সর্বজনীন অংশগ্রহণের আয়োজন করা হয়েছে।
'শোভাযাত্রায় এবছর ২৮টি জাতিগোষ্ঠী, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ বিভিন্ন দেশের অতিথিবৃন্দ অংশ নেবেন। এই বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রায় এবছর থাকবে ৭টি বড় মোটিফ, ৭টি মাঝারি মোটিফ এবং ৭টি ছোট মোটিফ।'
পয়লা বৈশাখের সর্বজনীন এ উৎসবটি শুরুর দিকে ছিল মূলত গ্রামাঞ্চলকেন্দ্রিক। গ্রামীণ মেলা, লোকজ নানা ধরনের খেলাধুলা ও নৃত্য-সংগীত ছিল এর প্রধান আকর্ষণ। দিনে দিনে এই উৎসব শহরাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। এখন পয়লা বৈশাখের উৎসবের আড়ম্বর শহরগুলোতেই বেশি লক্ষ্য করা যায়।
রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রা ছাড়াও ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ছোট-বড় নানা ধরনের অনুষ্ঠান হয়, মেলা বসে। বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতেও বৈশাখী মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, ব্যবসায়ীরা খুলে বসেন হালখাতা।
'দেশ বিচিত্র, নববর্ষ অভিন্ন' শীর্ষক এক নিবন্ধে লোকসংস্কৃতি ও পল্লীসাহিত্য গবেষক শামসুজ্জামান খান যেমন লিখেছেন, 'আমানি নামের কৃত্য, লাঠিখেলা, হাডুডু, গরুর দৌড় ইত্যাদি ছিল বাংলা নববর্ষের গ্রামীণ বাংলার আঞ্চলিক উৎসব। নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ এ উৎসব ইংরেজ আমলে ইংরেজদের নববর্ষের আদলে নতুন আঙ্গিক ও রূপ পরিগ্রহ করে। এ ক্ষেত্রে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের বিশেষ ভূমিকা ছিল। ভারতের স্বাদেশিকতার চেতনাও এভাবে নববর্ষ উদযাপনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।'
শান্তিনিকেতনে শিক্ষাকে আনন্দময় ধারায় প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন ঠাকুর পরিবারের রবীন্দ্রনাথ। তারই সহায়ক হিসেবে তিনি সেখানে বহু উৎসবের সূচনা করেছিলেন। সেসব উৎসবের অন্যতম ছিল পুরাতন বাংলা বর্ষকে বিদায় জানিয়ে নববর্ষকে আবাহন করার অনুষ্ঠান।
দিনটিতে রবীন্দ্রনাথ কিছু না কিছু লিখতেন, ব্যক্তিগত সংকল্প গ্রহণ করতেন, অনুজদের উপদেশ দিতেন। বঙ্গাব্দ ১৩৩৩-এর পয়লা বৈশাখেই তিনি রচনা করেছিলেন সেই অমর গান; যেটি ছাড়া বাংলা নববর্ষ প্রায় অসম্পূর্ণ—'এসো হে বৈশাখ'। মৃত্যুর ছায়াকে অতিক্রম করা এ গান যেন 'নবজনমের অমল আয়ুর' প্রার্থনা সংগীত।
এমন প্রার্থনার মতোই আজকের দিনে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের কথা ধার করে তো বলাই যায়—'আজি পুরানো যা কিছু দাও গো ঘুচিয়ে,/মলিন যা কিছু ফেলো গো মুছিয়ে।/শ্যামলে কোমলে কণকে হীরকে,/ভুবন ভূষিত করিয়ে দাও।।'
স্বাগত বঙ্গাব্দ ১৪৩২।







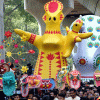


Comments