‘শ্রম সংস্কারে শ্রমিকদের মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করতে হবে’
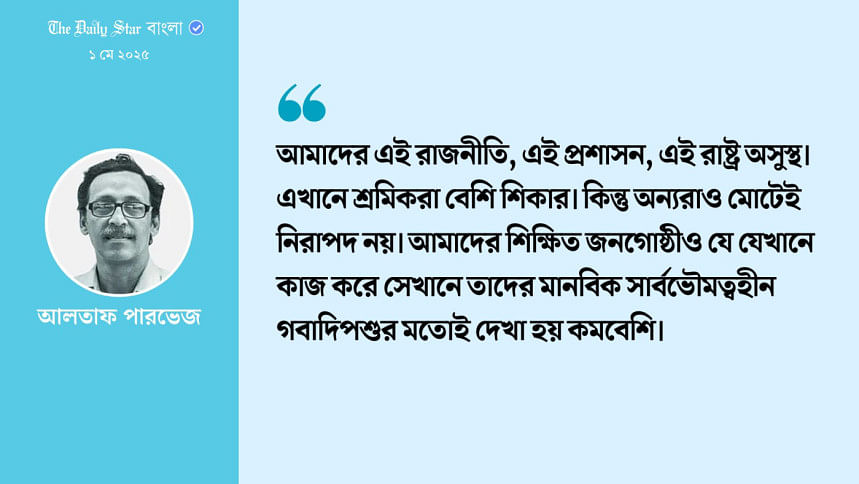
শ্রমিকরা দেশের অন্যতম চালিকা শক্তি। কিন্তু, নানাভাবেই তারা নিগ্রহ ও বৈষম্যের শিকার। যার ফলে, মালিকরা লাভবান হলেও শ্রমিকদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না।
সম্প্রতি দ্য ডেইলি স্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দেশের শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো নিয়ে কথা বলেছেন লেখক-গবেষক আলতাফ পারভেজ।
দ্য ডেইলি স্টার: ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে শ্রমিকদের ত্যাগ বা ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। প্রায় নয় মাস পেরিয়ে গেছে গণঅভ্যুত্থানের। এই সময়কালকে শ্রমিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?
আলতাফ পারভেজ: চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের ভেতর শতাধিক জন ছিলেন সরাসরি শ্রমজীবী। আবার আহতদের মাঝেও শত শত জন শ্রমজীবী পরিবারের।
কোটার মতো শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ইস্যুতে এই আন্দোলন শুরু হলেও শ্রমিকদের দিক থেকে এই গণঅভ্যুত্থানে এত বিপুল অংশগ্রহণের কারণ কী? কারণ দুটি। প্রথমত, আন্দোলনের বৈষম্যবিরোধী শ্লোগান ও অঙ্গীকার। দ্বিতীয়ত, ২০২৪ সালের আগের দুই বছরে শ্রমজীবীদের আয় রোজগারের বিপন্নতা।
শেখ হাসিনার সময়ে শ্রমজীবীরা দুইভাবে খুব বিপন্ন ছিল। প্রথমত, মজুরি বাড়ানোর কথা বললেই তাদের বিরুদ্ধে শিল্পপুলিশকে পাঠানো হতো। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যমূল্য লাগামহীন বৃদ্ধির কারণে শ্রমিকদের 'প্রকৃত আয়' কমে যাচ্ছিলো।
সচরাচর আমাদের দেশে শ্রমিকদের বাৎসরিক মজুরি বাড়ে ৫-৬ শতাংশ হারে। অথচ মূল্যস্ফীতি বাড়ছিল ১০-১২ শতাংশ হারে। এতে শ্রমিকদের জীবন অসহনীয় ছিল। তারা ভেবেছে, এই সরকার গেলে তাদের মজুরি বাড়বে এবং তারা মার্কেট সিন্ডিকেট থেকে রেহাই পাবে।
সমস্যা হলো, গত ৮-৯ মাসে এর কোনোটিই তেমন হয়নি। বাংলাদেশে ৪২টি খাতে মজুরি নির্ধারিত করা হয়েছে বিগত সময়ে। এই সরকারের সেগুলো আপডেট করা দরকার ছিল। কিন্তু সেটা হয়নি। আবার মার্কেট সিন্ডিকেটগুলো এখনও পণ্য বাজার ভালোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করছে।
এর বাইরে শ্রম আইনের সংস্কার বা শ্রমিক জীবনের মানোন্নয়েও সরকার উল্লেখযোগ্য কোনো সংস্কার করতে পারেনি এখনও।
ডেইলি স্টার: আপনার চোখে নতুন বাংলাদেশে শ্রমিকদের অবস্থান কেমন হওয়া উচিত?
আলতাফ পারভেজ: শ্রমিকদের একটা মর্যাদাপূর্ণ জীবনের সুযোগ দিতে হবে। যেখানে সে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শ্রমের উপযুক্ত মূল্য পাবে। যে মূল্য দিয়ে সে পরিবারের বাকি সদস্যদের নিয়ে শোভন জীবনযাপন করতে পারবে। তাতে যেন খাওয়া-পড়ার পাশাপাশি শিক্ষা ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা থাকে। তাকে কর্মস্থলে নিরাপদ পরিবেশ দিতে হবে। সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তাকে পেশাগত সমস্যা বলার জন্য মতামত প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। সংঘ গঠনের অধিকার দিতে হবে। তার কথা বলার জন্য প্রতিনিধি বাছাইয়ের অধিকার থাকতে হবে।
অর্থাৎ তার জীবন আইনগতভাবে সুরক্ষিত এবং সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের আওতায় থাকতে হবে। তাকে যেন গবাদিপশু মনে না করা হয়, তাকে যেন মানুষ মনে করা হয়।
ডেইলি স্টার: সম্প্রতি শ্রম সংস্কার কমিশন বিভিন্ন সুপারিশসহ তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। সেখানে বিভিন্ন খাতের শ্রমিকদের মজুরি তিন বছর পরপর মূল্যায়ন ও পুনর্নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে।
এ ছাড়া, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মজুরি না দিলে শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ, রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের জন্য আপৎকালীন তহবিল, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের শর্ত শিথিলকরণ, নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস নির্ধারণ এবং স্থায়ী শ্রম কমিশন প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছে। এসব প্রস্তাব নিয়ে আপনার মন্তব্য কী?
আলতাফ পারভেজ: শ্রম কমিশন অনেকগুলো সুপারিশ ও প্রস্তাব দিয়েছে। আমি তাদের প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ পড়েছি। এবারের মে দিবস হলো গণঅভ্যুত্থানের সরকার প্রথম মে দিবস। আমি মনে করি, এবারের মে দিবসে শ্রম কমিশনের সুপারিশের ৫-১০টি বাস্তবায়ন হয়ে যাওয়া উচিত।
সরকার প্রায়ই বলছে, সংস্কার করতে রাজনৈতিক ঐকমত্য লাগবে। কিন্তু দেখেন, শ্রমিকদের নিয়ে শ্রম কমিশনের এমন কিছু সুপারিশ আছে, যেগুলো কোনো রাজনৈতিক দল বিরোধিতা করবে বলে মনে হয় না। যেমন: শ্রমিককে নিয়োগপত্র দিতে হবে। এটায় আপত্তি করার কিছু নেই। শ্রম আইনের সংস্কার করে গৃহশ্রমিক, কৃষিশ্রমিকসহ নানান ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মীদের শ্রমিকের আইনগত মর্যাদা দিতে হবে।
শ্রমিকদের হালনাগাদ তথ্যভাণ্ডার নেই দেশে। সেই কাজ এখনি শুরু হতে পারে। যেসব খাতে মজুরি নির্ধারণ হয়েছে অনেক দিন হলো, সেগুলো অবিলম্বে আপডেট করতে বলা যায়। রানাপ্লাজাসহ শ্রমিক মৃত্যুর বড় ঘটনাগুলোর দ্রুত বিচারের নির্দেশ দেওয়া যায়। আসন্ন বাজেটে শ্রম বিষয়ক মন্ত্রণালয় দুটির বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে তাতে নতুন নতুন কিছু কর্মসূচি নেওয়া যায়।
এসব বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো আপত্তি করার কারণ দেখি না।
কিছু কিছু সংস্কার প্রশ্নে জাতীয়ভিত্তিক সম্মতি দরকার হতে পারে। সেই আলোচনাও দ্রুতলয়ে শুরু হওয়া দরকার।
ডেইলি স্টার: এসব প্রস্তাবের মাঝে কোন সংস্কারগুলো জরুরি ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন?
আলতাফ পারভেজ: শ্রম কমিশন বলেছে, যিনি শ্রমিক নিয়োগ দিবেন তিনি 'মালিক' নন, 'নিয়োগকর্তা' হিসেবে বিবেচিত হবেন। আর এরকম সব নিয়োগকর্তার বেলায় শ্রম আইনকে কার্যকর ধরতে হবে।
কিছু কিছু খাতে মজুরি অমানবিকভাবে কম। সেগুলো নিয়ে দ্রুত মজুরি বোর্ডের বসা দরকার।
শ্রমিক অধিকার ও কারখানার পরিবেশ দেখার জন্য যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার জনবল ও দক্ষতা বাড়ানো এবং তার আইনগত ক্ষমতা বাড়ানো দরকার দ্রুত।
শ্রম আদালতের সংখ্যাও অনেক বাড়ানো উচিত এবং আদালতে যারা বিচার কাজ করবেন, তাদের উপস্থিতি ও নির্ধারিত সময়ের ভেতর রায় দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে।
সরকার অবিলম্বে একটা ন্যূনতম জাতীয় মজুরি মানদণ্ড ঘোষণা করতে পারে। এটা বহু দেশে আছে। আমাদের এখানেও জরুরি। তিন বছর পরপর বাজার দরের সঙ্গে এটা সমন্বয় করবে সরকার।
শ্রমিকদের সংঘ গঠনের অধিকার সহজ করতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের শর্তগুলোও নমনীয় করা যায় এখনও।
ডেইলি স্টার: প্রস্তাবিত সংস্কারগুলো বাস্তবায়নের সম্ভাবনা কতটুকু বলে আপনার মনে হয়? আর তাতে কতটুকু পরিবর্তনই বা আসবে, বিশেষ করে যেখানে দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৮৫-৯০ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত?
আলতাফ পারভেজ: শ্রম কমিশন যেসব সুপারিশ করেছে সেগুলোর অধিকাংশ বাস্তবায়নযোগ্য এবং বাস্তবায়ন করা জাতীয় স্বার্থে দরকার। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে চাই। বাংলাদেশে যখন যে সরকারই আসুক, তাদের নিশ্চয়ই একটা প্রধান অগ্রাধিকার হবে দারিদ্র্য বিমোচন। দরিদ্র অবস্থা থেকে উত্তরণের মানে হলো মানুষকে অন্তত দিনে দুই ডলারের বেশি মজুরি পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন এমন শিল্প-অবস্থা নিশ্চয়ই আমরা রাখতে পারি না যেখানে দিনে মজুরি ২০০ টাকার নিচে। এটা সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
তাছাড়া ওই শিল্পগুলো তো লাভজনক। তাহলে এরকম মজুরি কেন থাকবে? আপনি চা শিল্পের অবস্থা দেখুন। সেখানে কিন্তু এভাবে চলছে।
আবার পোশাক শিল্পে দেখুন, বাৎসরিক মজুরি বৃদ্ধি পাচ্ছে সিঙ্গেল ডিজিটে। অথচ দেশে মূল্যস্ফীতি হচ্ছে ডাবল ডিজিটে। পোশাক শিল্পে প্রবৃদ্ধিও হচ্ছে। তাহলে আমরা মূল্যস্ফীতির চেয়ে কম হারে মজুরি বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়ে কী চাইছি? এ খাতের লাখ লাখ শ্রমিক দরিদ্র হয়ে যাক? এটা রাজনৈতিক দল ও সরকারের ঘোষিত নীতিরই বিরুদ্ধে যায়।
অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কথা বললেন। আমাদের শ্রম খাতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতই বড় ও প্রধান। কিন্তু এই খাতের অনেক কর্মীই শ্রমিক। ফলে তাদের শ্রম আইনে যুক্ত করতে হবে। আজকে গৃহশ্রমিকদের পরিচয়পত্র দেন না মালিকরা। এটার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের বিষয়ে কিছু নীতিমালা অবশ্যই থাকতে হবে এবং সবাইকে সেটা মানতে হবে। আমরা লাখ লাখ গৃহশ্রমিককে আদিম জীবনে রেখে দিতে পারি না।
আজ দেশে লাখো মোটরচালিত রিকসা চলছে। এই চালকদের লাইসেন্স দেওয়া, প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ তো এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। এসব বন্ধ করার ধারণা বাস্তব সম্মত নয়।
লাখো খেতমজুর আছে দেশে। কার্তিক-অগ্রহায়ণে তাদের কাজের অভাব হয়। তাদের জন্য ওইসময় 'কাজের বিনিময়ে মজুরি কর্মসূচি' নেওয়া জরুরি।
শ্রম কমিশন দলিতদের বিষয় লিখেছে। দলিতদের বড় অংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী। ঢাকায় কয়েক শত বছর ধরে আছে এরা। অথচ তাদের সবাই ভূমিহীন। ঢাকার আশেপাশে খাসজমিতে তাদের পুনর্বাসন করা দরকার এবং সেটা করা যায়।
কিন্তু, প্রশ্ন হলো সরকার এসব বাস্তবায়ন করবে কি না। আমি মনে করি রাজনৈতিক-সামাজিক চাপ না থাকলে সম্ভবত শ্রম কমিশনের অনেক সুপাারিশই বাস্তবায়ন হবে না।
কে সেই চাপ দিবে? শ্রমিকরা তো অসংগঠিত। রাজনৈতিক দলগুলোতে তাদের উপস্থিতিও দুর্বল। ফলে আপাতত খুব বেশি আশাবাদী হতে পারছি না।
ডেইলি স্টার: শ্রম সংস্কারের পাশাপাশি শ্রমিকদের সঙ্গে হওয়া অন্যায়ের বিচারও একটি মৌলিক দাবি। আমরা দেখেছি রানা প্লাজা, তাজরীন বা হাশেম ফুডসের মতো দুর্ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে বিচারিক দীর্ঘসূত্রিতা।
আলতাফ পারভেজ: এটা একটা জাতীয় লজ্জা ও জাতীয় ব্যর্থতা যে রানাপ্লাজার মতো ঘটনারও বিচার শেষ হলো না আজ পর্যন্ত। রানাপ্লাজার ঘটনা প্রমাণ করে, শ্রমিক জীবন আমাদের রাজনীতির কাছে, আমাদের প্রশাসনের কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। শ্রমিকদের লাশ ও রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে অর্থনৈতিক উল্লাস করতে আমরা মোটেই লজ্জিত নই।
আমি এসবকে বিচারিক দীর্ঘসূত্রিতা না বলে বৈচারিক অবহেলা ও উদাসীনতা বলতে চাই। রানাপ্লাজা অধ্যায় জানিয়ে দিলো, বাংলাদেশের শ্রমজীবীদের নীরবতা গণমৃত্যুতে এই রাষ্ট্র, এই রাজনীতি সামান্যতম দায় বোধ করে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো গণঅভ্যুত্থানের পর আমরা 'দায় ও দরদে'র রাজনীতির কথা শুনেছিলাম। প্রতিশ্রুতি ছিল এটা বৈষম্যহীন 'দ্বিতীয় রিপাবলিক' হবে। কিন্তু সেটা কোথায়?
ডেইলি স্টার: শ্রমিকের অধিকারের পাশাপাশি তার সম্মান ও স্বীকৃতিও গুরুত্বপূর্ণ। শ্রম কমিশন এমন প্রস্তাবও করেছে যে শ্রমিককে 'তুই-তুমি' বলে সম্বোধন করা যাবে না। কিন্তু এ ধরনের সংস্কার শুধু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সম্ভব নয়। তার জন্য চাই সামাজিক রূপান্তরও। সেটা কীভাবে সম্ভব?
আলতাফ পারভেজ: আপনি ঠিকই বলেছেন, শ্রমিকদের প্রতি অবজ্ঞা, তাদের অমর্যাদা এখানে সামাজিক কাঠামোর অংশ। আমাদের অর্থনীতি পুঁজিতান্ত্রিক হলেও এখানে সমাজ জীবনে কুৎসিত সামন্তীয় সংস্কৃতি বিদ্যমান। শ্রম ও শ্রমিককে এখানে মর্যাদার সঙ্গে দেখতে শেখেনি সমাজ। তবে এর কারণ রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক।
আমাদের রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে সংস্কার হয়নি। রাজনীতি এখনও কিছু পরিবার নিয়ন্ত্রণ করছে। শিল্প প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোও পরিচালিত হয় আইনকানুনের তোয়াক্কা না করে সামন্তীয়। এসব বন্ধ করতে রাষ্ট্রের আমূল ও গণতান্ত্রিক সংস্কার দরকার। চব্বিশের অভ্যুত্থান তো চাই চেয়েছিল।
খেয়াল করে দেখুন, এখানকার রাজনীতি ও প্রশাসন খোদ অন্যান্যদেরও খুব একটা মানুষ মনে করে না। সামান্য একটা কোটার আন্দোলন থেকে দেশে দেড় হাজার মতো মানুষ হত্যা করে ফেলা হলো মাত্র দেড় মাসে। বিশ্বে এমন নজির বিরল।
আমাদের এই রাজনীতি, এই প্রশাসন, এই রাষ্ট্র অসুস্থ। এখানে শ্রমিকরা বেশি শিকার। কিন্তু অন্যরাও মোটেই নিরাপদ নয়। আমাদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীও যে যেখানে কাজ করে সেখানে তাদের মানবিক সার্বভৌমত্বহীন গবাদিপশুর মতোই দেখা হয় কমবেশি। এখানে শ্রমিকের, কর্মীর জীবন গবাদিপশুর ইমেজ থেকে মুক্তি চায়।










Comments