শিক্ষা সংস্কারে প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন
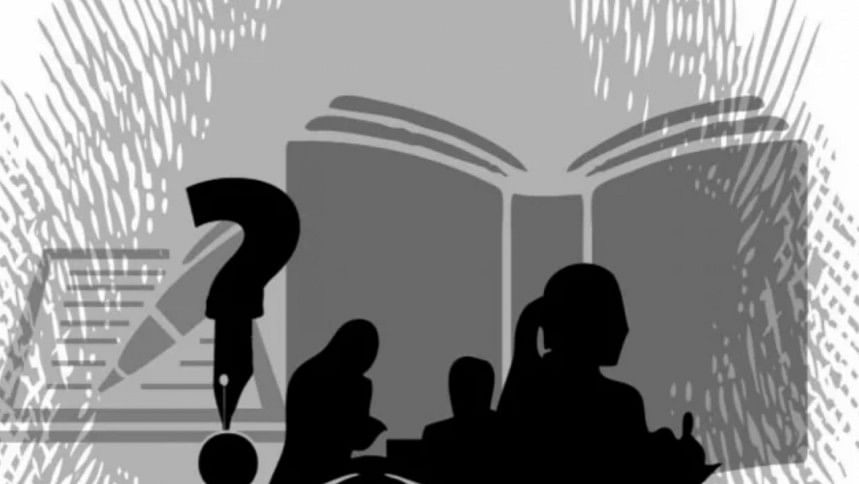
কোনো ব্যবস্থা ও শাস্ত্রসম্মত বিধান কখনো চিরস্থায়ী নয়। কোনো নীতিই চিরকাল একই শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে টিকে থাকে না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন, মনন ও চিন্তার জগতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে—মূলত ধীরলয়ে, কখনো বা আকস্মিক। পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যই মানুষকে নানান পরিকল্পনা, ব্যবস্থা ও উদ্যোগ নিতে হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার জন্য নিতে হয় নানান সাময়িক ও দূরদর্শী কৌশল।
শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। পরিমার্জন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজনের মধ্য দিয়ে চলে শিক্ষার সংস্কার ও প্রসার। রাষ্ট্রও তাই। রাষ্ট্রের উন্নয়নের তথা মানুষের অগ্রযাত্রার অন্যতম মূল হাতিয়ার শিক্ষা। তাই এই হাতিয়ারকে পুঁজি করে দেশকে এগিয়ে নিতে গেলে এর প্রয়োজন বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার। আর এক্ষেত্রে সাহসী ও দৃঢ় চিত্তে এগিয়ে আসতে হবে চিন্তাশীল, বিবেকবান ও নীতিনিষ্ঠ কর্মঠ ব্যক্তিদের।
এটাও সত্য যে সংস্কার ও পরিবর্তন হতে হবে দীর্ঘমেয়াদি, ভালো ফলাফল পাওয়ার নিমিত্তে। পরীক্ষা নেওয়া, পরীক্ষা পাস ও সিলেবাসের গণ্ডির মধ্যে চক্রাকারে ঘোরার নাম শিক্ষা নয়। আবার চাকরির নেশায় অধ্যয়ন করা ও করানো শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও বিদ্যায়তনের কাজ নয়। সৃষ্টিশীল ও প্রগতিশীল মানুষ তৈরি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনই মূলধারার শিক্ষার কাজ। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষায়িত শিক্ষার মাধ্যমে বের হয়ে আসবে দক্ষ নাগরিক, যারা জ্ঞান-দক্ষতাকে বুনিয়াদ করে রাষ্ট্রের ও সমাজের নানান কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে।
১৮৩৫ সালের মেকেলের মিনিটের মতো কেরানি বানানোর কেরামতি দেখানো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজ নয়। আমদানি-নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা ও নীতি দিয়ে আমরা বেশিদূর এগোতে পারব না। নিজেদের ভূমি, মানুষ ও সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি ও দাবিকে সামনে রেখেই সাজাতে হবে শিক্ষার রূপকল্প, যা প্রথমে নিজস্ব দেশজ বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকেও যাতে ধরে ফেলতে পারে ক্রমান্বয়ে। এজন্য নিজস্ব ভাষায় বিদ্যা দান, বই রচনা এবং এর পাঠ ও পঠন জরুরি। নিজস্ব ভাষায় বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের উৎকর্ষ হয় ফল্গুধারার মতো—তা মাথায় না রাখলে জাতি বেশি দূর এগোতে পারবে না।
শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থার আদলে শিক্ষাকে সাজাতে গেলে আমরা তামাশার বস্তুতে রূপান্তরিত হবো; হবো নব্য উপিনিবেশবাদের নয়া পুতুল। দেশীয় ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির যোগসাজশ না থাকলে শুধু পাশ্চাত্যের শিক্ষার আধুনিক মোড়কে নিজেদের সঁপে দিলে আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি কখনো জাগ্রত হবে না। শির উঁচু করে নিজের দেশকে বহির্বিশ্বে তুলে ধরতে ব্যর্থ হবো। চাপানো কিছু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সৃষ্টির আনন্দে জীবন' দান করতে পারে না, ঠিক যেমন পারে না 'মনের মধ্যে ঘা' দিতে।
শিক্ষাকে শুধু বাজারে করা যাবে না; অর্থাৎ শিক্ষার মধ্যে অবশ্যই মানবিক ও মননশীলতার চর্চার রসদ থাকবে। থাকবে প্রকৃতির মতো সৃষ্টিশীলতার আনন্দ। বাজারের চাকরিকে উদ্দেশ্য করে শিক্ষার প্রজেক্ট নিলে সে শিক্ষা সামগ্রিক তেমন কোনো মঙ্গল দেশের জন্য বয়ে আনবে না। বরং, শিক্ষার গতি প্রকৃতি এমন কৌশলে সাজাতে হবে, যা বল্গাহারা ও অতি লোভী বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক কল্যাণে। বাজারের প্রেসক্রিপশন ও বেনিয়াদের চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষা প্রজেক্টকে নাকচ করে দিতে হবে।
দিনকে দিন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে একশর উপরে চলে গেছে। তাহলে কি টাকা থাকলেই শিক্ষা! এসব অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান ভালো, আবার অনেকগুলা যাচ্ছেতাইভাবে শিক্ষাদান করে। বিশেষ করে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান অর্থলোভী। তারা নিম্নমানের শিক্ষক দিয়ে চালায়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তো ভর্তি পরীক্ষাই হয় না এবং কিছু আছে এখনো টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট দেয়। মানে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেয়। আবার ভালো কিছু প্রাইভেট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার খরচতো আকাশচুম্বী। আমাদের মতো ভঙ্গুর অর্থনৈতিক দেশে এটা বিলাসিতার মতো দেখায়। এদিকে সরকারি তথাকথিত ভালো ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আজ সঠিক পাঠদান ও শিক্ষা প্রদানে ব্যর্থ বলেই অনেকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্থান বলে দাবি করেন। সমাধান কোথায়, ভাবতে হবে গভীরে গিয়ে। আর কত মানহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চাই আমরা!
শিক্ষা নিয়ে আমাদের সবচেয়ে বেশি ভাবতে হবে। শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ ঢের বাড়াতে হবে। শিক্ষকদের আলাদা বেতন স্কেল করে নানান ধরনের প্রণোদনা দিতে হবে। শিক্ষকের জীবন মান রুগ্ন হলে, শিক্ষার মানও রুগ্ন হবে। বিদ্যায়তন হবে প্রগতিশীল মন-মানসিকতার নাগরিক তৈরির কেন্দ্র।
যে বয়সে যা দরকার—জীবনের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য একটি বিদ্যায়তনের তার সবটুকুন না থাকলেও অনেকটাই থাকা জরুরি। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল আর ভালো চাকরিই শিক্ষার শেষ কথা না; সামাজিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক বের করে আনাও শিক্ষার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শুধু কথায় নয়, রাষ্ট্রকে কাজে নেমে তার প্রমাণ দেওয়া উচিত।
শিক্ষা একটি বৈষম্যহীন সমাজ গঠন করবে এবং তা সর্বজনীন হবে—এটাই সবার প্রত্যাশা। তবে উচ্চশিক্ষা সর্বজনীন না হওয়াই শ্রেয়। মূলত সংখ্যার আস্ফালন নয়; শিক্ষার গুনগত মান নিশ্চিত হবে। শিক্ষার্থীদের সব অর্জন যেন হয় মেধা ও পরিশ্রমের সমন্বয়ে, যাতে করে ভবিষ্যতে তারা যাই অর্জন করুক না কেন সময় ও পরিশ্রম দিয়ে করতে শিখে এবং এর মূল্য বোঝে।
কেবল ডিগ্রি নিলেই হবে না—তা যত বড় ডিগ্রিই হোক না কেন। শরীর, মন, আত্মা ও মেধার সুষম বিন্যাস ও উন্নয়ন না হলে শিক্ষা ভালো কিছু বয়ে আনে না। এজন্য যদি আরেকবার বলতে হয় দ্বিধাহীনভাবে বলবো—মাতৃভাষায় শিক্ষার বিকল্প নেই। মাতৃভাষাতে যত সহজে ও সাবলীলভাবে বিজ্ঞান ও গণিত বুঝব, তা কি অন্য ভাষায় আদৌ বুঝতে পারব বা পারি? এই একটা প্রশ্ন রেখে গেলাম।
১৮৭৪ সালে জার্মান দার্শনিক কান্ট 'এনলাইটমেন্ট' বা আলোকায়নের কথা বলেন। সেই সূত্র ধরে কিছু বলতে গেলে বলতে হবে, শিক্ষা নিজের আত্মাকে জাগায় পরাধীনতার শিকল ভাঙার গল্প বলে বলে। নিজেদের উন্নত মানুষ, জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্যই সবার কল্যাণে শিক্ষার বিস্তার করতে হবে এবং টেকসই ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। তাহলে কামিয়াব হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে।
রাষ্ট্র মেরামত ও শিক্ষা সংস্কার হাতে হাত রেখে চলুক। সুশিক্ষা আমাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক ও মানবিক সমাজ গড়তে সাহায্য করবে। চাকরিকেন্দ্রিক শিক্ষা আমাদের দাসখত দিতেই শিখাবে। রাখবে পঙ্গু ও মরণাপন্ন করে আজীবন। তাই শিক্ষা সংস্কার ও রাষ্ট্র মেরামত নিয়ে আওয়াজ উঠুক দিকে দিকে। হোক কলরব প্রতিটি বিদ্যায়তনে।
আরিফুল ইসলাম লস্কর: কবি, প্রাবন্ধিক এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক










Comments