ভোট, নয়াভোট ও ‘ভোটচিন্তা’
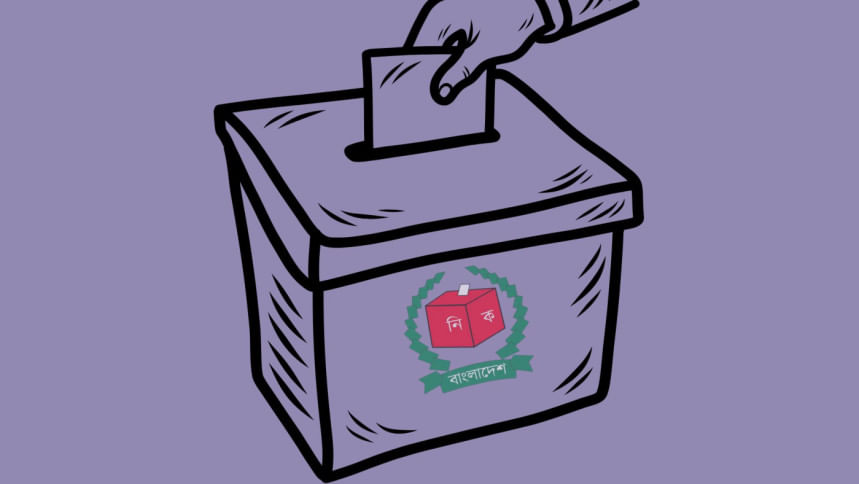
ভোটের মৌসুম যে আসছে, সেটা বোঝা গেল একটা প্রান্তিক জেলা শহরে ঢুকতেই। মাসখানেক পরে ঢুকেছি এই জেলা শহরে। ফলে, নতুন এই পরিবর্তনটা চোখে পড়ল। অনেকগুলো নতুন মোটর সাইকেলের শোরুম দেখলাম গজিয়ে উঠেছে দ্রুতই। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই একমাসে এমন কোনো ইতিবাচক ঘটনা ঘটেনি যে, তাতে এই পরিবর্তন দেখতে হবে।
পরিবর্তন একটাই ঘটেছে—সেটা অর্থনীতিতে নয়, রাজনীতিতে। দেশে ভোটের এবং বলাই বাহুল্য খুবই প্রত্যাশিত ভোটের একটা আগমনী ঘোষণা এসেছে। ধরে নেয়া হচ্ছে, ফ্যাসিবাদের পতনের পর আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতেই ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
নির্বাচনী মৌসুম আসতেই নড়েচড়ে বসেছে ভোটাকাঙ্ক্ষী নির্বাচনী দলগুলো। ফলে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে থাকা নির্বাচন করতে চাওয়া প্রার্থীদের সরবতাও বেড়েছে মাঠে-ময়দানে। তারই ফলস্বরূপ নির্বাচনকে টার্গেট করেই যে মোটরসাইকেলের দোকানের প্রস্তুতি, সেটা বলাই বাহুল্য।
যদি সবকিছু ঠিক থাকলে এবারে উৎসবমুখর ও ভোটারসমৃদ্ধ দিনের ভোট দিনেই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেটা হলে, নির্বাচন সম্পন্ন করতে দরকার হবে যেসব আয়োজনের, তার মধ্যে এই মোটরবাইকও বড় অনুষঙ্গ—সেটা এই নবতর মোটরবাইকের শোরুম খোলার আয়োজন দেখেই পরিষ্কার হলো।
বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীরা লাগসই বিনিয়োগ করতে শুরু করেছেন নির্বাচনকে সামনে রেখেই। দিন গেলে ভোটের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রয়োজনীয় অন্যান্য খাতগুলোও জেগে উঠবে নিশ্চয়। দ্রুতই সেসব খাতেও পরিবর্তন চোখে পড়বে আশা রাখি।
২.
৫ আগস্টের পর পরিবর্তনগুলোর প্রতি নজর রাখছি। এসব পরিবর্তন আমাদের রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজের নানা চালচিত্র হাজির করছে। হাজির করছে সমাজের মধ্যে জেগে ওঠা শক্তিগুলোর আচরণ ও সামর্থ্যকেও।
একটা বড় পরিবর্তন ঘটেছে দেশের পরিবহণ খাতে। বিশেষ করে আন্তঃজেলা পরিবহণের দিকে খেয়াল করলে খুব মজার চিত্র ধরা পড়বে। আমাদের গণপরিবহণের ব্যবস্থাপনা মূলত বেসরকারিখাত নির্ভর। এখানে সরকারিখাতের অংশ খুবই কম। সরকারি প্রতিষ্ঠান বিআরটিসির পরিবহণগুলোও চলে লিজ ভিত্তিতে, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়। ফলে প্রায় পুরো পরিবহণ ব্যবস্থা বেসরকারিখাতেই পরিচালিত হয়।
আওয়ামী ফ্যাসিবাদী আমলে এই খাতের বড় গডফাদাররা পলাতক। এই খাতের মালিকানারও পরিবর্তন ঘটেছে। রাজনৈতিক শক্তিতে যারা আওয়ামী লীগকে রিপ্লেস করেছেন, তারাই এই ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ: ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে একচেটিয়া প্রভুত্ব করা 'এনা পরিবহণে'র ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এসেছে। 'এনা পরিবহণে'র নামও পরিবর্তিত হয়েছে 'ইউনাইটেড পরিবহণ' শিরোনামে। বোঝা যায় এর পেছনে আছে বর্তমানের ক্ষমতায়িত রাজনৈতিক শক্তি।
কান পাতলে এসব নব্য গডফাদারদের নামও শোনা যায় সহসাই। ঢাকা-নেত্রকোনা সড়কে চলাচলকারী 'শাহজালাল পরিবহণ' নতুন চেহারায় আবির্ভূত হয়েছে 'রফরফ পরিবহণ' শিরোনামে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই দুই সড়কেই যাত্রীসেবার মান কমেছে ভীষণভাবেই। ভাড়া কমেনি বটে, তবে নতুন রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকরা কোনোভাবেই যাত্রীসেবার মানের নিম্নমুখীনতা ঠেকাতে পারেননি—এটা খুব সিগনিফিকেন্ট ঘটনা।
আন্তঃজেলা গণপরিবহনে ফ্যাসিবাদের গডফাদারদের ব্যবস্থাপনার মান নতুন গডফাদারদের মানের চাইতে উন্নততর ছিল—এই সত্য যাত্রীরা প্রকাশ্যেই উচ্চারণ করতে দ্বিধা করছেন না। কেন এমন ঘটছে?—জানতে চেয়েছিলাম এইপথে চলাচলকারী বেশ কজন যাত্রীর কাছে।
তাদের উত্তর হচ্ছে, যারা পরিবর্তিত অবস্থায় মালিকানা দখল করেছেন, তারা বহু বছরের বুভুক্ষু-ক্ষুধার্ত, এখন গোগ্রাসে গিলছেন। যাত্রীসেবার বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার সময় নেই। যাত্রীসেবা দিয়েই যে মানুষের মন জয় করতে হবে, এটা তাদের বিবেচনায় নেই। তারা এখন ক্ষুধা মেটাতেই ব্যস্ত, ভীষণ ব্যস্ত।
নব্য দখলদার রাজনৈতিক শক্তির এই 'বুভুক্ষু মডেল' খুব লক্ষণীয়। ভোটাররা এটা খেয়াল করছেন। চোখ-কান খোলা রাখলে বোঝা যাবে, নদী-পাথর-বালু-বৃক্ষ-ফুটপাত-বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে সর্বত্রই এই 'বুভুক্ষু মডেল' সক্রিয়।
ভোটের আগমনী মৌসুমে এই ঘটনা কী প্রভাব ফেলতে পারে, দেখার বিষয় সেটাই। তবে ধারণা করা যায়, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-জ্বালানিসহ সর্বত্রই এই 'বুভুক্ষু মডেল' সামনের নির্বাচনে ভোটারদের অনুগ্রহ কাড়তে বড় চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়লে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।
৩.
এবার ভোটারের সংখ্যা ১২ কোটি ৬০ লাখ বলা হচ্ছে। সেটা বাড়তেও পারে। এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ছিল ৮ কোটি ১০ লাখ। এবারের নির্বাচনে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি ভোটার বেড়েছে, আরও বাড়তে পারে। এই ভোটারদের বড় অংশ নতুন ভোটার—যাদের বড় অংশ কখনই ভোটকেন্দ্রে যায়নি। সুযোগ পেলে এবারই তারা প্রথমবারের মতো ভোটকেন্দ্রে যাবে এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নতুন ভোটারদের 'মনস্তত্ব' আমাদের অজানা। সম্ভবত দলীয় ভোটারদের বাইরে তারাই এবার ভোটের ফলাফল নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখবে। এই নতুন ভোটারদের 'মনস্তত্ব' কেমন হবে? সেটা এখনো জানার কোনো সুযোগ আসেনি। তবে, সামনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ ডাকসু, রাকসু, জাকসু নির্বাচনে এর একটা প্রতিফলন দেখা যেতে পারে। তরুণরা কী ভাবছে, তার একটা ছিটেফোঁটার ইংগিত মিলতে পারে।
আপাতত এর বাইরে আমরা বিবেচনায় নিতে পারি সাম্প্রতিকতম একটি জরিপের ফলাফলকে।
ভয়েস ফর রিফর্মের সহায়তায় জরিপটি পরিচালনা ও গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করেছে ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স স্টাডিজ (বিআইজিডি)। গবেষণা জরিপটির নাম দেওয়া হয়েছে বিআইজিডি পালস সার্ভে-০৩। শিরোনাম: 'জনগণের মতামত, অভিজ্ঞতা ও প্রত্যাশা'। এই জরিপের কিছু পর্যবেক্ষণ রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য বিবেচ্য হতে পারে—
ক. এই জরিপে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের বয়সী অংশীজনের সংখ্যা ৫১ শতাংশ। অর্থাৎ তরুণদের বড় অংশের মতামত এখানে আছে।
খ. এই জরিপে অংশ নেওয়া ৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা বিভিন্ন দলকে ভোট দেবেন বলেছেন। ৭০ শতাংশ উত্তরদাতা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সমর্থক নন। অর্থাৎ বোঝা যায় বড় অংশ ভোটার পার্টিজান নন।
গ. কোন দলকে ভোট দেবেন, এই প্রশ্নে সিদ্ধান্ত না নেওয়া উত্তরদাতাদের অংশ প্রায় ৫০ শতাংশ। এটা খুব গুরুত্ববহ। কেননা এই ভোটাররা দলের চেয়ে প্রার্থীকে গুরুত্ব দিতে পারেন।
ঘ. উত্তরদাতাদের ৫১ শতাংশ চান, ভালোমতো সংস্কার করে তারপর নির্বাচন হোক। এই ইংগিতও গুরুত্ববহ।
৪.
এই জরিপটি শেষ কথা নয়। তবে, এর মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর বিষয়ে কিছু সুস্পষ্ট ইংগিত আছে।
প্রথমত, দেশের ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থানের যে স্পিরিট, যেটা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, সেদিকে একটা গভীরতর মনোযোগ আছে তরুণদের। যারা ভাবছেন, তরুণরা রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার বিষয়ক অগ্রাহ্যতা বা ভুলোমনকে সায় দেবেন, তাদের সেই ভাবনা বুমেরাং হতে পারে ভীষণভাবেই।
দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলগুলো পার্টিজান ভোটের যে পুরনো হিসাব ধরে বসে আছেন, এটা খুব ভুল প্রমাণিত হতে পারে। ২০০১ সালের নির্বাচনের ভিত্তিতে যে ভোটের হিসাবকে রাজনৈতিক দলের ভোটের হিস্যা হিসেবে আমরা গণ্য করছি, সেই হিসাব এবার ভুল প্রমাণিত হতে পারে। কেননা এবার ভোটের জনমিতি, জনঅভিজ্ঞতা কোনোটাই আর পুরনো দরজায় দাঁড়িয়ে নেই। সবটাই অনেকভাবেই পরিবর্তিত হয়েছে।
তৃতীয়ত, নতুন ভোটারদের 'ভোটচিন্তা' নয়া আকারে হাজির হতে পারে। জেনজি-জেনারেশনের সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভরতা, ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থানের ক্ষতস্মৃতি, শক্তিমান রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের পেশিবহুল আচরণ আমাদের শক্তিমান রাজনৈতিক দলগুলোর পুরনো ভাবনাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে দারুণভাবে।
চতুর্থত, যে রক্ত ও আত্মাহুতির ওপর দাঁড়িয়ে এই ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থান, তার রাজনৈতিক ন্যারেটিভে আওয়ামী দুঃশাসন ও প্রতিবেশী ভারতের আধিপত্যবাদী প্রবণতা একটি বড় দিকনির্ণায়ক। এই ভাবনাতে রাজনৈতিক দলগুলোর নমনীয়তা-আপসকামিতা জেনজি-জেনারেশনের ভোট মানসিকতায় প্রভাব ফেলতে পারে দারুণভাবে।
পঞ্চমত, পুরনো বা বয়সী ভোটারদের নন-পার্টিজান, সৎভাবাপন্ন দায়িত্বশীল অংশের মধ্যেও একটা গুণগত পরিবর্তন হতে পারে। ফ্যাসিবাদী দলের বিচারের প্রশ্নে, ইসলামোফোবিয়ার প্রশ্নে, প্রগতিশীলতার প্রশ্নে, ভারতের প্রশ্নে, রাজনৈতিক পক্ষগুলোর 'বুভুক্ষা-মডেলে'র প্রশ্নে তাদের অবস্থানেও নৈর্ব্যক্তিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। সেটা রাজনৈতিক দলের পার্টিজান ভোটের হিসাব ওলটপালট করে দিতে পারে।
পুনশ্চ: দখল-দূষণ এবং সুশাসনের প্রশ্নে শক্তিমান রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক বয়ানে, আচরণে, কর্মদক্ষতার প্রয়াসে বড় কোনো পরিবর্তনের আভাস দেখা দিয়েছে, এই বিশ্বাসে ভর করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আগামী দিনে এই পুরনো রাজনৈতিক চর্চাই যে বহুল পরিমাণে ফিরবে না, জনগণকে পুরনো দিনের দুঃশাসন উপহার দেবে না—সেই বিশ্বাস দেওয়ার পাটাতন সবলভাবে দৃশ্যমান নয়।
রাজনীতির এই সংস্কৃতি এবার ভোটের ব্যালটে বিপুলভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। রাজনৈতিক দলগুলো সতর্ক ও হিসাবি না হলে, পুরোনো হিসাব ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে। গত বছরের ৫ আগস্টের আগে ফ্যাসিবাদী হাসিনার যে হিসাব সম্পূর্ণ উল্টে দিয়েছিল জেনজি, এবার ভোটেও সেরকম পুরোনো ভাবনাকে উল্টে যেতে দেখলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। আমাদের প্রতিষ্ঠিত সব রাজনৈতিক দল, তাদের সম্ভাব্য এমপি-প্রার্থীদের সেই দিকে নজর দেওয়া জরুরি।
শুভ কিবরিয়া: সিনিয়র সাংবাদিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক










Comments