‘নতুন উপসর্গ’ ও ‘পুরোনো রাজনীতি’: নির্বাচন কতদূর
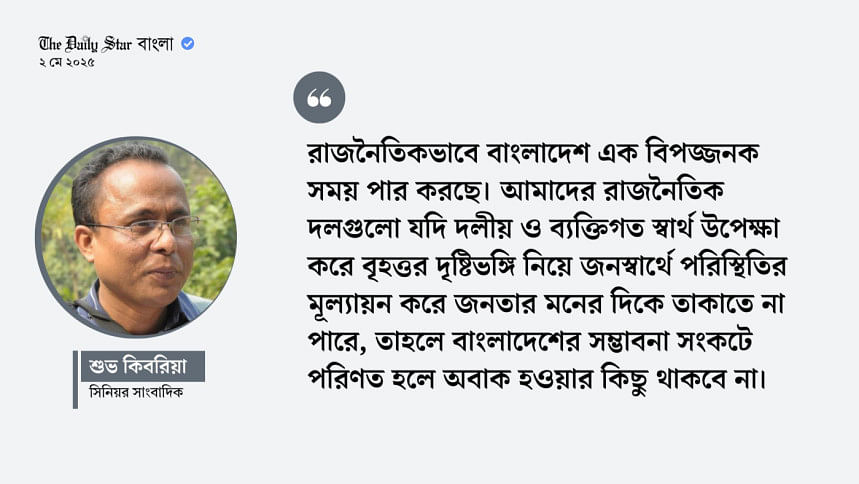
রাজনীতিতে এখন অনেক নতুন নতুন ঘটনা ঘটছে। ধারণা করা যায়, আরও নতুনতর ঘটনা ঘটবে। একেকটি ঘটনা একেক রকম সম্ভাবনা ও সংকট নিয়ে হাজির হবে। আমাদের রাজনীতি ও নির্বাচন তাতে বেশ দোল খাবে, তার ক্ষীণরেখাটি এখন ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে।
সর্বশেষ যে ঘটনাটি রাজনীতিতে আলোড়ন তুলেছে সেটা হচ্ছে রাখাইনে মানবিক করিডোর দেওয়ার প্রস্তাব এবং রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলার উপায় নিয়ে আলোচনা। আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে থাকা মিয়ানমারের রাখাইনে মানবিক করিডোর দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের অবস্থান যখন পরিষ্কার হচ্ছে, তখন বিএনপি এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে মিয়ানমারের রাখাইনে সহায়তা পাঠানোর জন্য 'মানবিক করিডর' স্থাপনে অন্তর্বর্তী সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে মর্মে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, সে বিষয়ে দলের স্থায়ী কমিটির সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিএনপি। তারও আগে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিজ এলাকায় এক জনসভায় এ বিষয়ে মত প্রকাশ করতে যেয়ে বলেই ফেলেছেন—'আমরা আরেকটা গাজায় পরিণত হতে চাই না'।
নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ও উৎকণ্ঠা
অন্যদিকে বহুল আলোচিত ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ এখনো পাওয়া যায় নাই, এমনকি মাসও না। দেশের বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি দাবি করছে নির্বাচনের সুস্পষ্ট তারিখ। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা বলছেন ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের জুনের কথা। ফলে, বিএনপি ঠিক সন্তুষ্ট নয়। তারা ভাবছে, নির্বাচনই সমাধান অথচ সেই নির্বাচনের তারিখ নিয়ে তালবাহানার শেষ নেই। বিএনপির যুক্তি খুব সুস্পষ্ট, নির্বাচনই খুলে দেবে সংস্কারের পথ। বিএনপির ব্যাখ্যা হচ্ছে, নির্বাচিত সরকারের হাতে দেশ শাসনই হচ্ছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মূল চাওয়া।
দেশের আরেক উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর মন বোঝা দায়। পেন্ডুলামের দোলকের মতো দুলছে তার রাজনৈতিক ঘোষণা। কখনো তারা চাইছে আগে সংস্কার, পরে নির্বাচন। কখনো বলছে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি, কখনো বলছে গণ-হত্যাকারীদের বিচার না করে নির্বাচন নয়। লন্ডনে খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করে এসে জামায়াত নেতার কথায় যে নতুন সুর, তার বাজনাও ইঙ্গিতবাহী। ফলে, অতীতের মতো রাজনীতিতে জামায়াত তার বহুরূপী চেহারাটা কেমন করে যেন আজও জাগিয়ে রেখেছে সোৎসাহে, বিড়ম্বনা-নিপীড়ন-অত্যাচার সয়েও।
ছাত্র-জনতার দল ও সংশয়...
নির্বাচন নিয়ে কঠোর অবস্থানে গণ-অভ্যুত্থানের গর্ভে জেগে ওঠা ছাত্রজনতার দল এনসিপি। যদিও এখনো তারা রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন পায় নাই, তবুও তাদের এক পা রাষ্ট্র ক্ষমতায়, আরেক পা রাজনীতির মাঠে। নতুন দলের নেতাদের অনেকের বাহারি ব্যয়বহুল জীবন ও নানাজনের নানারকম দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসছে।
ছাত্র-তরুণদের উদ্যোগে সরকার ও রাজনৈতিক দল গঠন—অনেকের মধ্যেই পরিবর্তনের সম্ভাবনার উৎসাহ তৈরি করেছিল। রাষ্ট্র পরিচালনা ও রাজনীতিতে তারা ইতিবাচক কিছু করবেন—এমন আশাও জোরেশোরে করা হয়েছিল। তবে সরকারি পদ এবং দলের দায়িত্বে থাকা কারও কারও কর্মকাণ্ডে সেই প্রত্যাশা দিনকে দিন কমছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছে এই তরুণদের কারও কারও বিরুদ্ধে।
ফলে গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্র-জনতার যে অংশ বিজয়ীর বেশে সামনে এসেছিল, তাদের অনেকেরই বিতর্কিত কর্মকাণ্ড জনমনে প্রত্যাশার চমকের পারদটাকে আর জাগিয়ে রাখতে পারছে কি না, সে সন্দেহও দেখা দিয়েছে।
নতুন দল গঠনের হিড়িক
এরকম একটা অনিশ্চিত, দোদুল্যমান অবস্থায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন নতুন দল গঠনের হিড়িক পড়ে গেছে। বিবিসি বাংলার খবর বলছে, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত গত আটমাসে অন্তত ২২টি রাজনৈতিক দল ও ও চারটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম আত্মপ্রকাশের খবর এসেছে গণমাধ্যমে। যার মধ্যে ২০২৪ সালে ১১টি আর ২০২৫ সালের প্রথম চার মাসে আরও ১১টি দল গঠিত হয়েছে। সেই হিসাবে প্রতি মাসে গড়ে তিনটি করে রাজনৈতিক দল ও সংগঠন হয়েছে।
আত্মপ্রকাশ করা দলগুলোর মধ্যে আছে—নিউক্লিয়াস পার্টি অব বাংলাদেশ (এনপিবি), জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক পার্টি, ওয়ার্ল্ড মুসলিম কমিউনিটি, সমতা পার্টি, বাংলাদেশ জনপ্রিয় পার্টি (বিপিপি), সার্বভৌমত্ব আন্দোলন, বাংলাদেশ সংস্কারবাদী পার্টি (বিআরপি), বাংলাদেশ মুক্তির ডাক ৭১, বাংলাদেশ জাগ্রত পার্টি, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক পার্টি (বিজিপি), জাতীয় বিপ্লবী পরিষদ, দেশ জনতা পার্টি, আমজনতার দল, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক শক্তি, বাংলাদেশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (বিএসডিপি), বাংলাদেশ জন-অধিকার পার্টি, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), জনতার বাংলাদেশ পার্টি, জনতার দল, গণতান্ত্রিক নাগরিক শক্তি, ভাসানী জনশক্তি পার্টি, আ-আম জনতা পার্টি (বিএজেপি) ও বাংলাদেশ জনতা পার্টি।
এত অল্প সময়ে এত নতুন রাজনৈতিক দল তৈরি হচ্ছে কেন? এটা কি স্বাভাবিক বিষয় না এর গর্ভে আছে কোনো নতুন অঘটনের প্রয়াস? এ বিষয়টি রাজনীতিতে অনেক ধরনের উদ্বেগ ও জটিলতার নিয়ামক হয়ে উঠতে পারে বলে অনেকের অভিমত।
ফিকে হচ্ছে ভরসা!
ছাত্রজনতার গণ-অভ্যুত্থানের পরে রাষ্ট্র নিয়ে মানুষের মনে নতুন আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। মানুষ ভেবেছে সংস্কার যতটুকুই হোক আর যেভাবেই হোক, রাষ্ট্রকে হতে হবে জবাবদিহিমূলক ও যথাসম্ভব দুর্নীতিমুক্ত। এই যাত্রায় নানারকম চিড় ধরছে। কী অন্তর্বর্তী সরকার, কী 'সংস্কারপন্থী' দল কী পুরোনো রাজনৈতিক দল—কেউই আর শক্তিমান ভরসা হয়ে উঠছে না। আর দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলে কোনো সংস্কারই আলোর মুখ দেখবে না, টেকসইও হবে না। ফলে, সংস্কার প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের চেয়ে যেকোনো মূল্যে নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার যে তড়িঘড়ি আকাঙ্ক্ষা সেটা যত উন্মোচন হচ্ছে, ততই সংস্কার সম্ভাবনা জনমনে ম্রিয়মাণ হয়ে উঠছে।
গণ–অভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্র, সরকার ও গণতন্ত্র নিয়ে বিএনপি নেতাদের বক্তব্যে যে নৈতিক জাগরণ দেখা গিয়েছিল, তা জনমনে প্রশংসিত হয়েছিল। আওয়ামী লীগের মাঠে অনুপস্থিতির কারণে বিএনপি দ্রুত সারাদেশের রাজনৈতিক শূন্যস্থান যতই পূর্ণ করতে থাকে, ততই সেই প্রশংসা ফিকে হতে থাকে। অবারিত রাজনৈতিক সুযোগে বিএনপির অনেক কর্মী দখলদারি ও চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে পড়েন। বহিষ্কার করেও এ সমস্যা কমানো যায়নি। স্থানীয় জনগণের মধ্যে এ নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে। এবং তারা এর মধ্যে দিয়ে পুরোনো দিনের রাজনীতি ফিরে আসার ইঙ্গিত পাচ্ছে।
সংবিধান সংস্কার প্রশ্নে অনেক বিতর্ক ও পক্ষ-বিপক্ষ দেখা যাচ্ছে। সেটা এক অর্থে শুভলক্ষণও বটে। কেননা, সংবিধান বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা ও বিতর্ক যত চলবে সেটা আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষাকে ততই সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু সংবিধান যাদের হাতে কার্যকর হবে, সেই রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা নিয়ে আলোচনা তেমন হচ্ছে না। আমাদের সব বড় দলের অভ্যন্তরীণ গঠনতন্ত্রে দলীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে আছে দলপ্রধানের হাতে। ফলে পরিবারতন্ত্র এবং কর্তৃত্ববাদ দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রচর্চায় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো সংবিধান সংস্কার প্রশ্নে যতটা সোচ্চার, দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চার বিষয়ে সংস্কার প্রশ্নে ততটাই নীরব।
আওয়ামী লীগ কীভাবে রাজনীতিতে ফিরবে অথবা শাস্তি পাবে—সে বিষয়ে কোনো রাজনৈতিক ঐকমত্য নাই। এনসিপি চায় দলটি নিষিদ্ধ হোক। এ বিষয়ে বিএনপির যুক্তি, আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে জনগণ বা আদালত, এর ফলাফল যা-ই হোক। অন্যদের অবস্থাও খুব সুস্পষ্ট নয়। আওয়ামী লীগ প্রশ্নে রাজনীতিতে সব পক্ষই সুবিধা নেওয়ার অপেক্ষায় আছে। কেউ নিষিদ্ধ করে, কেউ বিচার করে, কেউ তাকে নির্বাচনের মাঠে ফিরিয়ে এনে রাজনৈতিক ডিভিডেন্ড নিতে চায়। আওয়ামী লীগ প্রশ্নে, গণহত্যার বিচারের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোর এই মতবিরোধ ও সুবিধাবাদ জনপ্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।
ফলে গণ-অভ্যুত্থান যে জনআশা জাগিয়েছিল তাতে চিড় ধরছে।
উপসর্গ ও রাজনীতির পুরোনো মডেল
নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এক ধরনের উৎকণ্ঠা আছে। কেননা তারা জানে, দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই বারবার অনির্বাচিত সরকার আসে। প্রতিবারই অনির্বাচিত সরকার সুশাসনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোকে সংস্কার করে সুশীল দলে পরিণত করার চেষ্টা চালায়। ফলাফল যাই হোক সেটা রাজনৈতিক দলগুলোকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করে। এবং নির্বাচিত সরকারে যাওয়ার সহজ পথকেও কঠিন করে তোলে। এবারও সম্ভবত বড় রাজনৈতিক দলগুলো সেই ভয়কেই বড় করে দেখছে। কেননা:
ক) রাজনীতিতে অনেক এজেন্ডা চলমান আছে। সংস্কার একটি বড় এজেন্ডা। গণহত্যার বিচার একটি বড় দাবি। আওয়ামী লীগকে ডিল করার প্রশ্নও একটি এজেন্ডা। এর মধ্যে হালে যুক্ত হলো রাখাইনে মানবিক করিডোর বিষয়ক আলোচনা। এই বিষয়টি বহুমাত্রিক। এর সঙ্গে জাতিসংঘ ও আমেরিকা যুক্ত। আছে চীন ও ভারতের স্পর্শকাতর স্বার্থও। আছে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের উপায় খোঁজার নতুন পথ। আছে দেশের নিরাপত্তা ও সামরিক ঝুঁকির প্রশ্নও।
খ) উপসর্গ হিসেবে এই নতুন এজেন্ডার আলোচনা ও বিতর্ক আমাদের এমন এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারে যে নির্বাচন বিলম্বিতও হতে পারে বলে রাজনৈতিক দলগুলোর আশঙ্কা। আবার এই প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীন-ভারত-আমেরিকার সঙ্গে তাদের সম্পর্কও বদলে দিতে পারে।
গ) আমাদের প্রধানতম রাজনৈতিক দলগুলোর চিন্তা ও রাজনৈতিক চর্চার মধ্যে নতুন মডেল নাই। বরং তারা চিরাচরিত পুরোনো মডেলেই চলতে চাইছে। অথচ বদলে গেছে বহু কিছু। দেশের রাজনীতিতে গণ-অভ্যুত্থান তো বটেই ঘটে গেছে গণহত্যা। এসব পরিস্থিতি মোকাবিলা করে যে নতুন প্রজন্ম রাজনৈতিক আলোচনায় এসেছে, সেই বিশাল জনগোষ্ঠীর চিন্তার সঙ্গে বয়স্ক রাজনৈতিক গোষ্ঠীর চিন্তার ফারাকই শুধু নয়, চিন্তার সংঘর্ষও বিদ্যমান। ফলে রাজনীতির পুরোনো মডেল আগামী দিনে প্রায় সাড়ে চার কোটি নতুন ভোটারের মনকে জয় করবে, না ভয় পাবে—সেটাও একটা প্রশ্ন।
পুনশ্চ: এখন ভাবনা হচ্ছে রাজনীতিতে যেসব নতুন উপসর্গ যুক্ত হচ্ছে, তা কি ডিল করতে পারবে আমাদের পুরোনো রাজনীতি? ডিল করতে না পারলে যথাসময়ে কি নির্বাচন হবে? অন্তর্বর্তী সরকার কি সংস্কার করেই নির্বাচনে যাবে? নাকি নির্বাচন প্রশ্নে রাজনৈতিক দল ও অন্তর্বর্তী সরকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাবে? পুরোনো রাজনীতি ও নতুন উপসর্গের ডামাডোলে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ কি সুরক্ষিত হবে? এসব 'যদি' ও 'কিন্তু'র মধ্যেই খাবি খাচ্ছে নির্বাচনের প্রশ্নও।
রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ এক বিপজ্জনক সময় পার করছে। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো যদি দলীয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ উপেক্ষা করে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জনস্বার্থে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে জনতার মনের দিকে তাকাতে না পারে, তাহলে বাংলাদেশের সম্ভাবনা সংকটে পরিণত হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।
মনে রাখতে হবে, নগর পুড়লে দেবালয়ও রক্ষা পাবে না…
শুভ কিবরিয়া: সিনিয়র সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক










Comments