আল মাহমুদ যেভাবে এসেছে জুলাই বিপ্লবে

আমাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত।/ আমাদের রক্তে সবুজ হয়ে উঠেছিল মুতার প্রান্তর।/ পৃথিবীর যত গোলাপ ফুল ফোটে তার লাল বর্ণ আমাদের রক্ত।/ তার সুগন্ধ আমাদের নিঃশ্বাস বায়ু।
যখন আবু সাঈদের বুক বির্দীণ করে দেয় ঘাতক পুলিশের বুলেট। তখন রংপুর থেকে ঢাকা পুরো দেশের দেয়ালে-গ্রাফিতিতে প্রতিবাদি স্লোগানে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে কবি আল মাহমুদের এই পংতিগুলো। কবি আল মাহমুদ জীবনকে দেখেছেন কবিতার ভেতর, কবিতাকে করে তুলেছেন জীবনের ভাষ্য। প্রতিদিনের উচ্চারিত শব্দসমবায় থেকে সংগ্রহ করেছেন শব্দ। ফলে তার জটিল চিন্তাও হয়ে উঠেছে সহজবোধ্য। তার লেখনিতে যেমনি এসেছে সময়ের গল্প, তেমনি স্বাদেশিকতা ও আন্তর্জাতিকতা বোধও এনেছেন শব্দের গাথুনিতে। রাজনৈতিক চেতনা তাকে করে তুলেছে জনবান্ধব।
চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে অনেক তরুণকেই বিনা অপরাধে জেলে নেয়া হয়েছে। যদিও তাদের মনে প্রাণে ধ্যানে জ্ঞানে ছিলো বৈষম্যহীন এক বাংলাদেশের স্বপ্ন। কবি- লেখকরা তরুণদের এই আশা আকাঙকাকে পথ দেখান, তারা থাকেন পথ-প্রদর্শকের কাতারে।
আল মাহমুদ মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রশ্নে বারবার চেতনাকে জাগ্রত এবং প্রতিবাদী ভূমিকায় নিজেকে অবতীর্ণ করেন। এক্ষেত্রে নিজ জন্মভূমি ও ভিন্ন দেশের মানুষের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য বিবেচনায় আনেননি। ফলে পৃথিবীর যে প্রান্তেই মানবাধিকার লংঘন এবং স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে সেখানেই কবি কবিতা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। কেননা তিনি রুশোর মতো বিশ্বাস করেন, মানুষের প্রজন্ম জন্মগতভাবে স্বাধীন। তাদের স্বাধীনতা, তাদের নিজেদের অবিচ্ছেদ্য সত্তা। সে-সত্তাকে প্রদান করার অধিকার তাদের নিজেদের ব্যতীত অপর কারোরই হতে পারে না। অপর কারোর স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করার অধিকার প্রাকৃতিক বিধানেরই বিরোধী। চব্বিশের জুলাই আন্দোলনে ছাত্র-জনতার প্রতিবাদি মিছিলে অনেকটাই প্রাসঙ্গিক ছিলেন আল মাহমুদ। এমনকী দেয়ালে দেয়ালে প্রতিবাদি স্লোগান ও গ্রাফিতিতে আল মাহমুদের কবিতা শোভা পেয়েছে। মঞ্চে-মিছিলেও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন।
শত শত তরুণের আত্মত্যাগের এই অভ্যুত্থানের মাঠে প্রতিবাদি স্মারক হিসেবে এসেছে আল মাহমুদের কবিতা। কবি লেখেন- আমাদের এ মিছিল নিকট অতীত থেকে অনন্ত কালের দিকে।/ আমরা বদর থেকে ওহুদ হয়ে এখানে /শত সংঘাতের মধ্যে এ কাফেলায় এসে দাঁড়িয়েছি।/ আমরা আজন্ম মিছিলেই আছি।/ এর আদি বা অন্ত নেই। / পনেরশত বছর ধরে সভ্যতার উত্থান-পতনে আমাদের পদশব্দ একটুও থামেনি।/
চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে অনেক তরুণকেই বিনা অপরাধে জেলে নেয়া হয়েছে। যদিও তাদের মনে প্রাণে ধ্যানে জ্ঞানে ছিলো বৈষম্যহীন এক বাংলাদেশের স্বপ্ন। কবি- লেখকরা তরুণদের এই আশা আকাঙকাকে পথ দেখান, তারা থাকেন পথ-প্রদর্শকের কাতারে। কবি চার্লস সিমিকের কথায়, 'প্রত্যেকটা ধর্ম, আদর্শ এবং চিন্তার প্রথা ও পন্থা ব্যক্তি মানুষটাকে পুনঃশিক্ষা দিতে চায়, তাকে ভিন্ন একটা মানুষে রূপান্তর করতে চায়। একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক নিজের জন্য ভাবেন না, তারা তোমাকে এ কথাই বলবে।' 'জেলগেটে দেখা' কবিতায় উপস্থিত সেই দেশপ্রেমিক আল মাহমুদ; যিনি চিন্তারে সক্রিয়তা দিয়ে স্বদেশকে দেখেছেন। যখন নাহিদ-আসিফদের আয়নাঘরে নিয়ে নিপীড়ণ করা হয়, সেসময়ের কষ্ট যেন অনুরণিত হয়েছে একজন আল মাহমুদের কবিতায়। সেই কথার সত্যকে জীবনের সত্যে সমীকৃত করে দিয়েছেন কবি।
আমি কতদিন আমার কারাকক্ষের লোহার জালি চেপে ধরেছি। / হায় স্বাধীনতা, /অভুক্তদের রাজত্ব কায়েম করতেই কি আমরা সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলাম।/ আর আমাকে ওরা রেখেছে বন্দুক আর বিচারালয়ের মাঝামাঝি/ যেখানে মানুষের আত্মা শুকিয়ে যায়।/ যাতে আমি আমরা উৎস খুঁজে না পাই।/ কিন্তু তুমি তো জানো কবিদের উৎস কি? / আমি পাষাণ কারার চৌহদ্দিতে আমার ফোয়ারাকে ফিরিয়ে আনি।' /
সিমিক মনে করেন- ভাষায় কবিতা হলো কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সক্রিয় অন্য সব ক্ষমতা মোকাবেলার শক্তি। কবির কবিতায়ও ছিল সরব শক্তির মোকাবেলা। এই আত্মবিশ্বাসই আল মাহমুদকে ভিন্ন মানুষে রূপান্তরিত করেছে। তিনি জানতেন প্রার্থনার শক্তির সমান্তরালে থাকে দ্রোহের শক্তি।
'কানা মামুদ, কানা মামুদ/ কোথায় পেলে ওড়ার বারুদ'। এই দ্রোহেরই সংগ্রাম করেছিলেন আল মাহমুদ জীবনভর। মাঝখানে এক প্রবল ঝড় এসে তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল ভিন্ন লোকে। তার নিজের ভাষায় এর উপযুক্ত জবাবও হয়তো মিলবে অন্বেষণে-অন্বেষণে।
দেড় দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকারের অন্যায়, অবিচার আর দুঃশাসনের বিপরীতে ছাত্রজনতার যে অভ্যুত্থান হলো, সেখানেও আল মাহমুদ হয়ে ওঠেন প্রতিবাদী উৎস। ফ্যাসিবাদ বিরোধী এই আন্দোলনে ধর্ম-বর্ণ, মত-পথ ও ব্যবসা-পেশা ব্যতিরেকে সকল প্রতিবাদী মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে আল মাহমুদের কবিতা। ভার্চুয়াল মাধ্যমে, পোস্টারে, প্লা কার্ডে, দেয়াল লিখনে ও গ্রাফিতিতে আল মাহমুদের প্রতিবাদী ও প্রতিরোধী বাণীগুলো যেন ইট-পাথরকেও জাগিয়ে তোলে। আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে সর্বস্তরের মানুষ।
কবি তা অনেক আগেই বলেছেন- আমরা তো শাহাদাতের জন্যই মায়ের উদর থেকে পৃথিবীতে পা রেখেছি।/ আমাদের মিছিল ভয় ও ধ্বংসের মধ্যে বিশ্রাম নেয়নি, নেবে না।/ শুধু কী তাই স্বৈরশাসকের পালিয়ে যাওয়ার সঙ্গেও যেন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে আল মাহমুদের কবিতা- তিনি বলেছিলেন/ আমরা জানি। /আমাদের ভয় দেখিয়ে শয়তান নিজেই অন্ধকারে পালিয়ে যায়। / আমাদের মুখাবয়বে/ আগামী ঊষার উদয় কালের নরম আলোর ঝলকানি।

আল মাহমুদ আজীবন লোক ঐতিহ্যের সঙ্গে আত্মীয়তা করেছেন; কখনো এই পথ থেকে সরে আসেননি। তাঁর কবিতায় নিছক শিল্পসৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়নি; গভীর জীবনবোধ, গণচেতনা, জাতির আত্মপরিচয়, প্রাণ ও স্রোত প্রতিবেশকে নগর সভ্যতার বিপরীতে স্থাপন এবং বর্তমান জীবন ও সময় বাস্তবতার সঙ্গে শেকড়ের সম্বন্ধসূত্র সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো তা নির্মাণ থেকে পুনর্নিমাণে শিল্পরূপ হয়ে উঠেছে।
আল মাহমুদ কোনো প্রথাবিরোধী, দ্রোহী বা উদ্ধত ধাঁচের কবি- লেখক বা চিন্তক ছিলেন না। তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষের কাছ থেকে পাওয়া সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং এর ঘাত-প্রতিঘাত সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। কবি বলতেন তিনি তার ঐতিহ্য ধর্মকে পরিত্যাগ করে এসেছেন, এটা তারা কখনোই প্রমাণ করতে পারেনি। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে তারা গালিগালাজ করে। এলিয়টের মতে, বাইবেলের 'সাম' কিংবা 'ইসাইয়াহ্' অংশ জীবন-অভিজ্ঞতার সমান্তরালেই জন্ম নেয়। এলিয়ট অবশ্য এমনও বলেন যে, বাইবেলকে সাহিত্য হিসেবে বিবেচনা না করে বরং সেটিকে শব্দের অভিজ্ঞতা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।
আল মাহমুদ আরও বলেন, 'অনেকে অপব্যাখ্যা করেন আমি নাকি সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছি! এসব কুৎসা রটনায় আমার কিছু যায় আসে না! আমার কেন, কোন কবির কিছু যায় আসে না! রাজনীতি ও ধর্মকে, ধর্ম মানে ধর্মীয় উপমাকে আমি কবিতার দৃষ্টান্ত করে তুলেছি! যেমন উপকথা বা প্রবচনকেও আমি কবিতায় নিয়ে এসেছি!'
জুলাই অভ্যুত্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার অনেক দেয়ায়ে যে কবিতার দেয়াল লিখন দেখা গেছে তা হলো - আজ আবার হৃদয়ে কেবল যুদ্ধের দামামা/ মনে হয় রক্তেই ফয়সালা।/ বারুদই বিচারক।/ আর স্বপ্নের ভেতর জেহাদ জেহাদ বলে জেগে ওঠা। (বখতিয়ারের ঘোড়া)
গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী নতুন বাংলাদেশের জন আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশের প্রধানতম কবি নাম আল মাহমুদ। আল মাহমুদ বিগত স্বৈরাচারী শাসনামলে ক্ষমতাসীনদের নিপীড়ন ও সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হন।
গত চার দশক ধরে আল মাহমুদ সাংস্কৃতিক স্বৈরাচার ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চেতনা বিরোধী তৎপরতার বিপক্ষে যে আমৃত্যু লড়াই অব্যাহত রেখেছিলেন, ২৪ এর সফল গণঅভ্যুত্থান তারই ধারাবাহিকতা। তাই নতুন বাংলাদেশে আল মাহমুদ অবশ্য পাঠ্য কবিসত্তা। তিনি বামপন্থি রাজনীতিকে চেতনার নিজস্ব মননে সাম্যবাদের মন্ত্রে জারিত ও দীক্ষিত হয়েই তার লেখালেখিতেও এ প্রভাব ছায়া পাত করে সুস্পষ্টভাবেই।
আল মাহমুদ স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে ঝুলন্ত জীবনের ঝুঁকিময় ক্ষণ গণনা করেছেন। যৌবনে সাম্যবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় লালিত যৌবন কাটিয়েছেন। মধ্যবয়স পর্যন্ত তার চিন্তাচেতনা সুস্পষ্ট কমিউনিস্ট ধারায় সাম্যবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত ছিল। সাহিত্যের সে চেতনার স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। আল মাহমুদ কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক এবং সাংবাদিক। সবকিছুকে অতিক্রম করে চির জাগ্রত থাকে তার কবি সত্তা। আজকে আমরা যখন সমাজ বাস্তবতার সর্বত্র নষ্ট রাজনীতির কালো আঁচড় দেখতে পাচ্ছি, এমনকি আমাদের শিল্প-সাহিত্যেও তার করাল প্রভাব দেখা যাচ্ছে, তখন আল মাহমুদ সময়ের কঠিন বাস্তবতার গড্ডলিকা অতিক্রম করে নিজেকে চিরায়ত সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে সমকালীন সতীর্থ লেখক-সাহিত্যিকদের নির্ভীক- সাহসি উচ্চারণের পথ দেখিয়ে গেছেন।
আল মাহমুদ প্রগতিশীলতার নামে বাম বুদ্ধিজীবীদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতার প্রধান সমালোচক ছিলেন। বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে আল মাহমুদকে আজীবন আবিষ্কার করা গেছে প্রতিবাদীদের প্রথম কাতারে। এ জন্য কবিকে সইতে হয়েছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক লাঞ্ছনা। বঞ্চিত করা হয়েছে নাগরিক মর্যাদা ও মুক্তিযোদ্ধার সম্মান থেকে। কিন্তু ঈমানের ঐশ্বর্যে প্রাণবন্ত কবি এতে অবদমিত ছিলেন না। তার অবস্থান ছিল ঈমান ও ইসলামের পক্ষে। তিনি ছিলেন বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পুরোধা।
আল মাহমুদের কবিতা একান্ত নিবিড়ভাবে মিশে থাকে বাংলাদেশের নদ-নদী, প্রকৃতি-প্রান্তর, মানুষ ও মৃত্তিকায় তার গল্প-উপন্যাসে ঘনিষ্ঠভাবে উঠে এসেছে বাংলাদেশের দৃশ্যচিত্র, ইতিহাসের আবছায়া অধ্যায়, বৃহত্তর গণমানুষের প্রত্যাশার প্রতিফলন। সমুদয় রচনার মধ্যে আল মাহমুদের প্রবন্ধাবলি তার আদর্শিক সংগ্রাম ও প্রতিশ্রুত গন্তব্যের প্রতি অকুণ্ঠ অগ্রসরতার উচ্চস্বর আত্মপ্রকাশ। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর প্রতি তার দায় ও দরদ প্রতিফলিত হয়েছে তার প্রবন্ধাবলিতে। তাই এই নতুন বাংলাদেশের জন্মলগ্নে গভীর অভিনিবেশে তার প্রবন্ধসমূহ পাঠ করা অবশ্যই গণআকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ নির্মাণপ্রকল্পের অন্যতম বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মসূচি।
বাংলাদেশের কবিতার পঞ্চাশের দশকে এসেছিল পাকিস্তানবাদ ও বামপন্থি কমিউনিস্ট ধারার বিপরীতে দেশত্ববোধক রোমান্টিতা। বাংলাদেশের পঞ্চাশের কবিরাই সমাজ সচেতনার সঙ্গে নান্দনিকতার একটি মিশেল ঘটাতে পেরেছিলেন। এরা কবিতাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন রোমান্টিকতার কাছে। এ দশকে, বিশেষ করে আল মাহমুদ, হাসান হাফিজুর রহমান ও ওমর আলীর কবিতা দেশ-মাটি প্রত্যয়ে অভিন্ন প্রতীক হয়ে উপমা-উৎপ্রেক্ষার সমন্বিত শিল্পভাষ্য হয়ে ওঠে। সনেট দশ-এ কবির উচ্চারণ:
'শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতের উঠিয়াছে হাত/
হিয়েনসাঙের দেশে শান্তি নামে দেখো প্রিয়তমা,/
এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত/
তাদের পোশাকে এসো এঁটে দিই বীরের তকমা/
আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুসম বন্টন,/
পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ,/
এমন প্রেমের বাক্য সাহসিনী করো উচ্চারণ/
যেন না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ।'
সমাজতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাত। ফসলের সুসম বন্টনের ইচ্ছে। লোকধর্মে ভেদাভেদ না থাকার প্রত্যাশা। সব একসূত্রে গথিত হয়ে হাজির করেছে বৃহৎ এক স্বপ্নকে, যা ব্যক্তির এবং সমষ্টির সর্বজনীন এক চাওয়া। একটা কল্যাণ রাষ্ট্রে, জনগণ বান্ধব দেশে, দেশজ সংস্কৃতির চর্চায় এগুলো যে অপরিহার্য ও অনিবার্য তা স্পষ্ট করেছে এই কবিতা। 'প্রকৃতি' কবিতায় দেখা যায় কৃষকের প্রত কবির হার্দিক টান ও অনুভব।
'কতদূর এগোলো মানুষ!/কিন্তু আমি ঘোরলাগা বর্ষণের মাঝে/
আজও উবু হয়ে আছি। ক্ষীরের মতন গাঢ় মাটির নরমে/
কোমল ধানের চারা রয়ে দিতে গিয়ে/ভাবলাম, এ-মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার...।'
কবিকে কোনো ক্ষীণ রাজনীতির বিভাজনে বিভাজিত ও গন্ডিবদ্ধ করে রাখা অসম্ভব। কতদূর এগুলো মানুষ? এই প্রশ্ন আজ গোটা মানব সভ্যতার। আমরা আসলে এগিয়ে যাওয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা করে করে কেবল পিছিয়ে পড়ছি। যখন অলীক-বিভাজনের দেয়াল তুলে মুক্তি সংগ্রামীদের কোনঠাসা করে রাখা হয়, যখন মনুষত্বের পরিচয় অগ্রাহ্য করে একজন সৃষ্টিশীল মানুষকে রাজনৈতিক ভিলেনে পরিনত করা হয়, তখন জাতি এগুতে পারে না। মানবতা ও প্রগতিশীলতা মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য হয়।
আমাদের চলমান সমাজবাস্তবতা যেন সেই মুখ থুবড়ে পড়া সমাজেরই প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। কবি জীবনান্দ দাস লিখেছিলেন, 'যারা অন্ধ, সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দ্যাখে তারা'। আর ভাষা সংগ্রামী-মুক্তিযোদ্ধা কবি আল মাহমুদকে তাদের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রগতিশীলতা ছবক ও গঞ্জনা শুনতে হয়েছে, যারা নাকি সুযোগ থাকা সত্বেও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেননি। তাদের অনেকে মুক্তিযুদ্ধের পর কবিতা লিখে, প্রগতিশীল রাজনৈতিক ভাবধারা ও ইসলাম বিদ্বেষী ভূমিকা নিয়ে আল মাহমুদের মত কবিকে মৌলবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেছেন। ঠুনকো রাজনৈতিক বিভেদ ও ধর্মীয় ভাবাদর্শ পুঁজি করে স্বাধীনতার পর দেশের প্রগতিশীল লেখক-সাহিত্যিকদের বিভাজিত অবস্থান ও পারস্পরিক রেশারেশি জাতিকে কিছুই দিতে পারেনি। অথচ তাদের ঐক্য জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি নিমার্ন করতে পারত। দেশে একশ্রেনীর রাজনৈতিক নেতা বলেন, সেক্যুলারিজম মানে ইসলাম বিদ্বেষ নয়, সব ধর্মের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা। অথচ ইসলামের প্রতি আস্থা ও প্রাক্টিসিং মুসলমান হওয়ার কারণে আল মাহমুদকে গালাগাল, নাজেহাল করা হয়েছে। 'কতদূর এগুলো মানুষ' কবিতায় এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়ার অর্ধশত বছর পর কবি আল মাহমুদ লোকান্তরিত হলেন।
এই অর্ধ শতাব্দীতে দেশ, সমাজ ও সভ্যতা এগিয়েছে নাকি পিছিয়েছে এই বিতর্ক যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছে। পশ্চিমা পুঁজিবাদি অর্থনীতি দ্বারা নতুন বিশ্বব্যবস্থা চলছে মাৎস্যন্যায় পন্থায়। বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে গিলে খায়, তেমনি ছোট অর্থনীতি ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে বড় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শক্তিগুলো গিলে খেতে চাইছে। এভাবেই গত শতাব্দীতে বহু ভাষা ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির বিলুপ্তি ঘটেছে। বায়ান্ন সালে তরুন প্রজন্ম মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষায় এবং একাত্তুরে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের উদাহরণ সৃষ্টি করেও আমরা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষা করতে পারছি না। এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের লক্ষ্য হচ্ছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজকে অধীনস্থ করা।
তিরিশের দশকে ইতালীয় কবি ও মার্কসবাদী দার্শনিক অ্যান্তোনিও গ্রামসি পুঁজিবাদী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আগ্রাসনের এই প্রবণতাকে কালচারাল হেজিমনি বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার কথা বলতে গিয়ে মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদী সরকারের বাহিনীর হাতে বন্দি গ্রামসি জেলখানায় বসেই তার শ্রেষ্ঠ লেখাগুলো লিখেছিলেন। সব ধর্ম-বর্ণ ও রাজনৈতিক মতাদর্শের সম্মিলন ও সহাবস্থানই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সৌন্দর্য।
আমাদের মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও চেতনায় এই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির আকাঙ্খা ছিল সবচেয়ে অগ্রগণ্য। সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে পরস্পর বৈরী ও বিভাজিত মানুষ নিয়ে কোনো জাতিরাষ্ট্র মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। অথচ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে কবি আল মাহমুদ সকলের কাছে পৌঁছতে চেয়েছেন। শেঁকড়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা ও শক্তি সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানোর প্রেরণা মানুষ বড় কবি-লেখকদের কাছ থেকেই পেয়ে থাকে। জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক গতিপথ নির্মাণে আল মাহমুদ অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক, তিনি আমাদের বাংলাদেশপন্থারও দিকপাল।









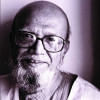

Comments