পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশন বাতিলই কি সমাধান?
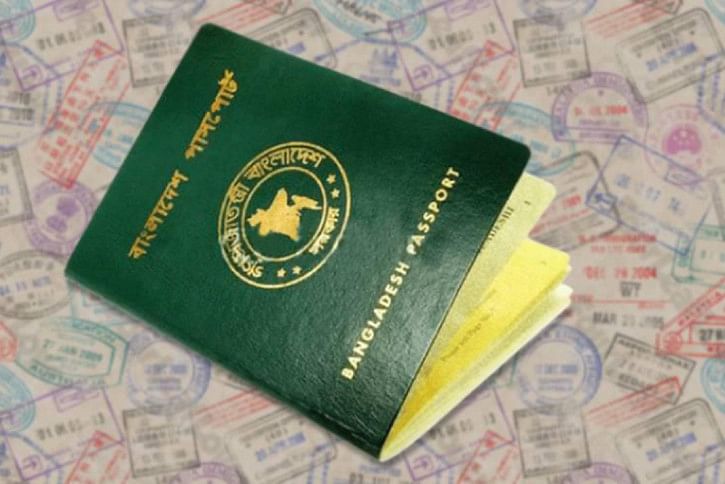
এই লেখাটি যিনি পড়ছেন, তার যদি পাসপোর্ট থাকে এবং পাসপোর্ট করতে গিয়ে ভেরিফিকেশনের সময় পুলিশকে টাকা (ঘুষ) না দিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি সৌভাগ্যবান। কেননা এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন, যার পাসপোর্ট করার সময় পুলিশকে ঘুষ দিতে হয়নি—তা তিনি যে পেশারই হোন না কেন।
পাসপোর্ট করার জন্য বছরের পর বছর নাগরিকদের নানাবিধ তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। যে কারণে অনেক বছর ধরেই এই আলোচনা ছিল, জাতীয় পরিচয়পত্র থাকার পরেও কেন পাসপোর্ট করতে পুলিশ ভেরিফিকেশন লাগবে?
এমন বাস্তবতায় সম্প্রতি পাসপোর্ট করার ক্ষেত্রে পুলিশ ভেরিফিকেশনের পদ্ধতি বাতিল করে দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। মঙ্গলবার এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরও কিছু শঙ্কা রয়ে গেছে বলে অনেকে মনে করেন।
দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংগঠন-টিআইবি পাসপোর্টে পুলিশ ভেরিফিকেশন বাতিলের প্রস্তাব দিয়েছিল আরও ৮ বছর আগে—২০১৭ সালে। ওই বছরের ২১ আগস্ট 'পাসপোর্ট সেবায় সুশাসন: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে টিআইবির পক্ষ থেকে বলা হয়, নতুন পাসপোর্ট করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান পুলিশ ভেরিফিকেশন পদ্ধতির কারণে সেবাগ্রহীতাদের হয়রানি ও দুর্নীতি হয়। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা ওই ব্যবস্থা বাতিলের সুপারিশ করে এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি।
টিআইবির গবেষণায় বলা হয়, নতুন পাসপোর্টের আবেদনকারীদের তিন চতুর্থাংশকেই পুলিশ ভেরিফিকেশনের সময় অনিয়ম ও হয়রানির শিকার হয়ে 'ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত টাকা' দিতে হয়। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, পুলিশ ভেরিফিকেশনে হয়রানি হচ্ছে। ফলে এটার কোনো দরকারই নেই। এর বদলে সকল নাগরিকের জন্য 'বায়োমেট্রিক ডাটা ব্যাংক' এবং 'অপরাধী তথ্য ভাণ্ডার' তৈরি করে তার সঙ্গে পাসপোর্ট অফিস ও ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের সংযোগ স্থাপন করার সুপারিশ করেন তিনি।
এরপর বিভিন্ন সময়ে পাসপোর্ট করতে গিয়ে পুলিশি প্রতিবেদনের নামে নাগরিকদের নানাবিধ হয়রানির খবর গণমাধ্যমে এসেছে। অনেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন।
গত ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরে রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য গঠিত জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের পক্ষে থেকেও পুলিশ ভেরিফিকেশন বাতিলের সুপারিশ করা হয়। গত গত ১৭ ডিসেম্বর সচিবালয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়ে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী বলেন, তিনি মনে করেন, পাসপোর্ট করার ক্ষেত্রে পুলিশ ভেরিফিকেশনের প্রয়োজন নেই।
অবশ্য গত ৬ জানুয়ারি রাজধানীর আগারগাঁওয়ের পাসপোর্ট অধিদপ্তর পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছিলেন, রোহিঙ্গাদের পাসপোর্ট নেওয়া ঠেকাতে পুলিশ ভেরিফিকেশন পদ্ধতি এখনই তুলে দেওয়া যাচ্ছে না।
যদিও পাসপোর্টে পুলিশ ভেরিফিকেশন বাতিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের পরে গত সোমবার তিনিই আবার বলেছেন, পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশন তুলে দেওয়ায় রোহিঙ্গারা যেন সুযোগ নিতে না পারে সে ব্যাপারে সরকার ব্যবস্থা নেবে। তিনি বলেন, জনগণকে ভোগান্তি থেকে রক্ষা করতে পাসপোর্টের ভেরিফিকেশন তুলে দেওয়া হয়েছে। অনেক দিনের চিন্তাভাবনা থেকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
রোহিঙ্গাদের ঠেকানো যাবে?
বাংলাদেশে এ মুহূর্তে ১২ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বসবাস করছে—যারা মিয়ানমার সরকারের জাতিগত নিধনের শিকার হয়ে প্রাণ নিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে। মানবিক কারণে বাংলাদেশ তাদেরকে আশ্রয় দিলেও বাংলাদেশ এখন যে রোহিঙ্গা সংকটের সবচেয়ে বড় ভিকটিম—তা নিয়ে দ্বিমতের সুযোগ কম।
রোহিঙ্গাদের নিয়ে সংকট ও ঝুঁকি বহুমাত্রিক। তার একটি হচ্ছে বাংলাদেশের মূল জনগোষ্ঠীর স্রোতধারায় তাদের মিশে যাওয়া। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি যেহেতু চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অঞ্চলের সঙ্গে অনেকখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ—ফলে চট করে কে রোহিঙ্গা আর কে রোহিঙ্গা না, সেটি যাচাই করা কঠিন। আর এই সুযোগ নিয়ে রোহিঙ্গাদের অনেকেই যে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্র পেয়েছে, তা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। শুধু কক্সবাজার নয়, অনেক দূরবর্তী জেলায় গিয়েও যে তারা নানা উপায়ে জাতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করছে, সেটিও নতুন কোনো খবর নয়। ফলে এখন তারা ওই জাতীয় পরিচয়পত্রের সুবাদে সহজেই পাসপোর্ট পেয়ে যাবে এবং বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে বিদেশ ভ্রমণ করতে পারবে।
অনেকে মনে করেন, রোহিঙ্গারা দলে দলে যদি বাংলাদেশি পাসপোর্ট সংগ্রহ করে এই দেশ থেকে চলে যায়, সেটা বরং বাংলাদেশের জন্যই ভালো। কিন্তু মুশকিল হলো, জাতিগত নিধন ও নানাবিধ বঞ্চনার ভেতরে বেড়ে ওঠা রোহিঙ্গাদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতার হার বেশি। ফলে তারা বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে অন্য কোনো দেশে গিয়ে যখন অপরাধে জড়াবে, তাতে দুর্নাম হবে বাংলাদেশের। সুতরাং এরইমধ্যে যেসব রোহিঙ্গা নানা উপায়ে বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করেছে, তারা এখন যদি পাসপোর্ট করতে চায়, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বা পাসপোর্ট অধিদপ্তর সেটি কী করে ঠেকাবে?
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা যদিও বলছেন যে তারা সতর্ক থাকবেন—কিন্তু সেই কৌশল কী হবে তা তিনি বলেননি। মুশকিল হলো, সরষের ভেতরে ভূত থাকলে কোনো কৌশলই কাজে আসবে না। যদি আসতো, তাহলে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে পারত না।
২০২০ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের একটি খবরে বলা হয়, নির্বাচন কমিশনের কঠোর নিরাপত্তা ও নির্দেশনার পরও রোহিঙ্গাদের হাতে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) পৌঁছে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম অঞ্চল ছাড়াও পিরোজপুরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিদ্যমান ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, এখন নিবন্ধিত রোহিঙ্গারাও ভোটার হয়ে যাচ্ছেন। সারাদেশে নির্বাচন কমিশনের সতর্কতাও কাজে আসেনি। কীভাবে এটা হচ্ছে—সেটা নিয়ে উদ্বিগ্ন খোদ কমিশন।
গত পাঁচ বছরে এই পরিস্থিতির কি খুব একটা উন্নতি হয়েছে? যদি না হয় তাহলে পুলিশ ভেরিফিকেশন বাদ দিয়ে রোহিঙ্গাদের পাসপোর্ট পাওয়ার পথ আরও সহজ করা হলো কি না? শুধু রোহিঙ্গা নয়, রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর বা যাকে পাসপোর্ট দিলে তিনি এর অপব্যবহার করবেন বলে শঙ্কা রয়েছে, এমন কেউ যদি জাতীয় পরিচয়পত্রের সূত্র ধরে পাসপোর্ট সংগ্রহ করেন, সেটি দেশের জন্য কতটা কল্যাণকর হবে?
পাসপোর্টও নাগরিক অধিকার
বলা হয়, জন্মনিবন্ধন ও পাসপোর্ট সব নাগরিকের জন্মগত অধিকার। অর্থাৎ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই একজন মানুষ যেমন কোনো ধরনের হয়রানি, জটিলতা ও সময়ক্ষেপণ ছাড়া ওই দেশের নাগরিক হিসেবে জন্মনিবন্ধন পাওয়ার অধিকারী, তেমনি জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট। এর জন্য আলাদা করে পুলিশ ভেরিফিকেশনের প্রয়োজন নেই।
গত রোববার 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০২৫' এর উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসও বলেছেন, 'জন্মসনদ ও এনআইডির মতো পাসপোর্টও এই দেশের নাগরিকদের একটি পরিচয়পত্র। জন্মসনদ ও এনআইডির জন্য আমাদের যেমন পুলিশ ভেরিফিকেশন লাগেনি, তেমনি পাসপোর্টের জন্যও লাগবে না। এই দেশের নাগরিক হিসেবেই আমরা তা পাবো।'
বাস্তবতা হলো, খুব ব্যতিক্রম ছাড়া পুলিশের ভেরিফিকেশন মূলত তাদের টাকা কামানোর একটি বড় উৎস। সব তথ্য সঠিক থাকার পরেও তারা যেমন ঘুষ না পেলে রিপোর্ট দিতে বিলম্ব করে বা অনেক সময় সঠিক রিপোর্ট দেয় না বলে অভিযোগ আছে, তেমনি টাকা নিয়ে অনেকের ভুল তথ্যও সঠিক উল্লেখ করে প্রতিবেদন দিয়ে দেয়, এই অভিযোগও বেশ পুরনো। অর্থাৎ সব তথ্য সঠিক থাকলেই যে পুলিশ দ্রুততম সময়ের মধ্যে রিপোর্ট দিয়ে দেবে—এমনটিও নাও হতে পারে। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে সেই ভেরিফিকেশন বাতিল করে দেওয়াই উচিত এবং সরকার এই সিস্টেম বাতিল করে দিয়ে একটি জনবান্ধব ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলাই যুক্তিযুক্ত।
ভেরিফিকেশন বাতিলই কি সমাধান?
পুলিশ ভেরিফিকেশন ছাড়া পাসপোর্ট করার সুযোগ তৈরির মধ্য দিয়ে কয়েকটি ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন:
১. ভুয়া নাম-ঠিকানায় পাসপোর্ট তৈরি করে অপরাধীরা সহজে দেশ ছাড়ার সুযোগ পেতে পারে।
২. ভুয়া তথ্য দিয়ে এক ব্যক্তি একাধিক পাসপোর্ট নিতে পারে, যা মানবপাচার, অবৈধ অভিবাসন বা আন্তর্জাতিক অপরাধের জন্য ব্যবহার হতে পারে।
৩. জঙ্গি, মানবপাচারকারী বা অন্যান্য অপরাধী গোষ্ঠী সহজে আন্তর্জাতিকভাবে চলাফেরা করতে পারবে।
৪. নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর পাসপোর্টধারীদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়তে পারে।
৫. জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যভাণ্ডার বা অন্যান্য ডিজিটাল ব্যবস্থা এখনো পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। ফলে যদি ভুল বা জাল তথ্য থেকে যায়, তাহলে তা ধরার সুযোগ কমে যাবে।
তাহলে সমাধান কী?
১. ভেরিফিকেশন পুরোপুরি তুলে না দিয়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সন্দেহজনক মনে হলে সেইসব ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভেরিফিকেশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে অবশ্যই সেটি হতে হবে পেশাদার, নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত।
২. ভেরিফিকেশনের নামে সংশ্লিষ্টরা যাতে কোনোভাবেই ঘুষ নিতে না পারে, সেজন্য পুরো সিস্টেম ডিজিটালাইজড করতে হবে। তারপরও কারো বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
৩. রাষ্ট্রের সব বাহিনীকে অনেক বেশি সতর্ক ও তৎপর থাকতে হবে।
৪. সব নাগরিকের জন্য 'বায়োমেট্রিক ডাটা ব্যাংক' এবং 'অপরাধী তথ্য ভাণ্ডার' তৈরি করতে হবে সেটিকে নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।
৫. ভেরিফিকেশনের পদ্ধতি বাতিল করে দিলে কিছু অসাধু কর্মকর্তার ঘুষ-বাণিজ্য বন্ধ হলেও আখেরে এর দ্বারা পুলিশ বাহিনীও উপকৃত হবে। কেননা তাদের ওপর একটি বিরাট চাপ কমবে। ফলে তারা অপরাধ তদন্তের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে বেশি মনোযোগ দিতে পারবে।
আমীন আল রশীদ: সাংবাদিক ও লেখক










Comments